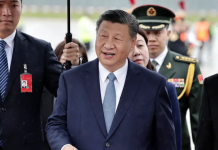ড. মো. মোরশেদুল আলম »
মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্র ধীরে বহে মেঘনা ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দের ৯ ফেব্রুয়ারি মুক্তি পায়। এটি স্বকীয় চলচ্চিত্র নির্মাণশৈলী, আধুনিক জীবনবোধ, সমকাল, স্বদেশ আর বাস্তব জীবনের নবতর উপস্থাপনায় ঋদ্ধ প্রখ্যাত চলচ্চিত্র নির্মাতা আলমগীর কবির পরিচালিত মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক পূর্ণদৈর্ঘ্য কাহিনীচিত্র। চলচ্চিত্রটি নির্মিত হয়েছে বাংলাদেশ ও ভারতের যৌথ প্রযোজনায়। ‘British Film Institute’ প্রণীত এ যাবতকালে বাংলাদেশে নির্মিত শীর্ষ ১০টি ছবির একটি তালিকা (Top 10 Films of Bangladesh) এক সময় তাদের ওয়েব সাইটে পাওয়া যেত। মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণির টানাপোড়নের চিত্র এতে প্রতিফলিত হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের বিশাল পটভৌমিক পরিম-ল থাকা সত্ত্বেও আলমগীর কবিরের চলচ্চিত্রে নিবিড়ভাবে ওঠে এসেছে সদ্যস্বাধীন দেশে মধ্যবিত্ত নাগরিকদের যুদ্ধবিধ্বস্ত জীবনযাপন ও আত্মত্যাগের করুণতম চিত্র। নির্মাতা মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে চলচ্চিত্রে উপস্থাপনের জরুরি প্রয়োজন বলে অনুভব করেছিলেন। কারণ, মুক্তিযুদ্ধকে কেন্দ্র করে ভারত ও বাংলাদেশের মানুষের মধ্যে যে সংযোগ ও মননের সমন্বয় ক্ষণকালের জন্য হলেও ঘটেছিল সে সংবাদটি পরবর্তীকালের উভয় দেশের নবপ্রজন্মের নিকট আলোকিত করা।
বাংলাদেশের রাজনীতি বিশেষ করে পররাষ্ট্রনীতি সম্পর্কিত বিষয়ও এতে স্থান পেয়েছে এই চলচ্চিত্রে। মুক্তিযুদ্ধে ভারতের অংশগ্রহণ এবং তাদের অবদানের চিত্র এতে উপস্থাপন করা হয়েছে। ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক ছিল এ চলচ্চিত্রের প্রধান দিক। চলচ্চিত্রটি নির্মাণ ছিল একটি নিরীক্ষাধর্মী ও মেধাদীপ্ত প্রয়াস। তবে প্রত্যক্ষভাবে যুদ্ধদৃশ্যের চিত্রায়ণ এতে তেমন গুরুত্ব পায়নি। আলমগীর কবির-এর মতে, উদ্ভট কাল্পনিক ঘটনার আশ্রয়ে নির্মাণ না করে ধীরে বহে মেঘনা চলচ্চিত্রটি সম্পূর্ণ নতুন আঙ্গিকে নির্মাণের চেষ্টা করা হয়েছে। সমগ্র মুক্তিযুদ্ধের ঘটনা কিন্তু গল্পের গাঁথুনিতে উল্লিখিত হয়নি। শুধু যুদ্ধবিধ্বস্ত বাস্তব মানুষের রূপায়ণকে চলচ্চিত্রটিতে আলাদা করে গুরুত্ব দেয়ার প্রয়াস রয়েছে। ধীরে বহে মেঘনা চলচ্চিত্রটি বাংলাদেশের চলচ্চিত্রশিল্পের ইতিহাসে এক নবতর আধুনিক প্রয়াস। দেশের বা সমাজের নানা সঙ্গতি-অসঙ্গতি, দুঃখ-দুর্দশা ও জীবন সংগ্রামের যে সকল চিত্র তাঁর চলচ্চিত্রে প্রতিফলিত হতে দেখা যায়; তা তিনি সবসময় বাস্তবতার নিরিখে উপস্থাপন করতে চেয়েছেন।
আলমগীর কবিরের ধীরে বহে মেঘনা চলচ্চিত্রে আশাবাদী আকাক্সক্ষার ঢেউ দোলায়িত হয়েছে মেঘনার প্রবহমানতায়। যুদ্ধের ক্ষত চিহ্ন আছে এখানে মানুষের স্মৃতিতে তবু তারা বেঁচে আছে এই বর্তমানে, যুদ্ধোত্তর নতুন দেশেÑ নতুন গন্তব্যে পৌঁছুবার আকাক্সক্ষায়। কারো বা প্রিয়জন, প্রিয়তমা আর স্বজন হারানোর বেদনায় বর্তমান অস্তিত্বের অঙ্গহানী বা অসম্পূর্ণতা আছে এই ছবির প্রায় সকল চরিত্রেরই। ভারতের অনিতা হারিয়েছে প্রদীপকে, আর বাংলাদেশের সুমিত বয়ে বেড়ায় প্রিয়তমা হাসুর পাকিস্তানি সৈন্য কর্তৃক ধর্ষিত হবার নির্মম স্মৃতি। বোন নাজমারও রয়েছে সদ্য বিবাহিত জীবনে হানাদারদের হাতে স্বামী রফিকের হত্যা দৃশ্য অবলোকনের একক নির্মম অতীত। অনিতা, হাসু, নাজমা, সুমিত, মানবেন্দ্র সকলেই যেন যুদ্ধ শেষে যুদ্ধের রেখে যাওয়া এক একটি জীবন্ত ফসিল। ছবিটির ঘটনাকাল দেখানো হয়েছে ১৯৭২ সাল, মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তী স্বাধীন বাংলাদেশ। যুদ্ধ শেষ, তবু যুদ্ধ স্মৃতি তাড়িত চরিত্রগুলো বার বারই ফিরে গেছে যুদ্ধের উত্তাল দিনগুলোতে কখনও ভয়েস ওভার, কখনও যুদ্ধকালীন সময়ে ধারণ করা প্রামাণ্যচিত্রের রাশফুটেজ দর্শনের মধ্য দিয়ে, আবার কখনও ফ্ল্যাশব্যাকের মুহুর্মুহু প্রয়োগে।
ফ্ল্যাশব্যাকে মূর্ত হয়েছে রক্তাক্ত যুদ্ধ, ত্যাগ ও গণহত্যার লাশের ছবি। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতীয়দের সহায়তা এবং যুদ্ধোত্তর পরিবেশে বিক্ষুব্ধ তারুণ্যের চিত্র ফ্ল্যাশ ফরোয়ার্ড কৌশলে চিত্রায়িত হয়েছে। পরিচালক চলচ্চিত্রটির বাস্তবসম্মত আবহ ও পরিবেশে চরিত্রগুলোকে অন্তর্লীন করে স্থাপন করেছেন যা ধীরে বহে মেঘনা’র চলচ্চৈত্রিক নির্মিতির উল্লেখযোগ্য বিষয়সমূহের মধ্যে অন্যতম। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের বাংলাদেশকে উপস্থাপনায় বিশেষ করে অসহযোগ আন্দোলন, যুদ্ধের প্রস্তুতি, গণহত্যা, মুক্তিবাহিনীর বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম এবং বিজয় প্রভৃতি নানাবিধ মৌল বা প্রধান আখ্যান থেকে পরিচালক স্বচ্ছন্দে প্রামাণ্যচিত্রে চলে গেছেন। এ চলচ্চিত্রের প্রশংসায় তানভীর মোকাম্মেল বলেন, ‘যুদ্ধকালীন জনগণের জীবনের আতঙ্কবোধ, সাম্প্রদায়িক সমস্যা ও ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক বা যুদ্ধ কিভাবে মানবিক সম্পর্কগুলোকে বিপর্যস্ত করে, তার কিছু নিপুণ চিত্রায়ণ আছে ছবিটিতে। জীবনের প্রথম ছবি হিসেবে ধীরে বহে মেঘনা নিঃসন্দেহে আলমগীর কবিরের প্রশংসনীয় সৃষ্টি এবং আমাদের চলচ্চিত্রের একটি মাইলস্টোন।’ আলমগীর কবির তাঁর প্রথম চলচ্চিত্র ধীরে বহে মেঘনা’য় (১৯৭৩) যুদ্ধ পরবর্তী বাংলাদেশের বর্তমান আর বর্তমানের প্রবহমানতা ভেঙ্গে অসংখ্য flashback প্রয়োগ করেন মুক্তিযুদ্ধকে নিয়ে বিভিন্ন চরিত্রের নানামুখী অতীত অঙ্কনের প্রয়াসে। বর্তমান আর অতীতের এই মুহুর্মুহু আন্তঃযোগাযোগ যেন ইতিহাসের এক কালপর্ব নির্মাণের তাগিদ থেকে উৎসারিত। এভাবে নির্মাতা এই চলচ্চিত্রে ‘সময়’-এর বর্তমান থেকে অতীতে, আবার অতীত থেকে বর্তমানে ভ্রমণের মাধ্যমে সময়ের ধারাবাহিকতা বা Continuit’ ভেঙ্গেছেন। একই সাথে, মুক্তিযুদ্ধকালীন ও মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তী সময়ের একটি সামগ্রিক চিত্রের ‘Organic Unity’ ও তৈরি হয় এই চলচ্চিত্রে।
ধীরে বহে মেঘনা চলচ্চিত্রটি মুক্তিযুদ্ধের একদম প্রান্তিক বিষয়, প্রতিবেশী দেশের সাধারণ মানুষ, সেনাবাহিনী বা বিমানবাহিনীর লোক, যাঁরা আমাদের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন; তাঁদের ক্ষয়ক্ষতি, অবদান, আত্মত্যাগের গল্প। তাঁদের ‘দৃষ্টিকোণ থেকে মুক্তিযুদ্ধকে দেখা’ এ ছবিতে এসেছে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতের ভূমিকা ছিল অনস্বীকার্য। ভারতের অনেক তরুণ এ দেশের মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিল। এরই প্রাসঙ্গিকতায় মুক্তিযুদ্ধের সময় মিত্রবাহিনীর হয়ে যুদ্ধে অংশ নিয়ে ভারতীয় ছাত্রী অনিতার প্রেমিক ভারতীয় বিমান বাহিনীর পাইলট প্রদীপ নিহত হন। প্রদীপের মৃত্যুর পর সদ্য স্বাধীন হওয়া বাংলাদেশে অনিতা ছুটে আসে স্মৃতি তাড়িত হয়ে। সে বুঝতে চায়Ñ এ দেশের জন্য কিসের এত দায় ছিল প্রদীপের? কিন্তু পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী কর্তৃক এদেশে পরিচালিত ধ্বংসযজ্ঞ স্বচক্ষে পর্যবেক্ষণের পর তার ভুল ভাঙে। চলচ্চিত্রের একটি দৃশ্যে এ প্রসঙ্গে অনিতা বলে, ‘সারা ভারত, বাংলাদেশ যখন জয়ের আনন্দে মত্ত তখন আমি নিজেকে ঘৃণা করেছি, বাংলাদেশকে ঘৃণা করেছি। আমার চোখেও ঘুম ছিল না। থাকতে না পেরে চলে এসেছি এখানে। দেখতে বুঝতে বাংলাদেশ কী এমন জিনিস যার জন্যে চিরদিন দগ্ধে দগ্ধে মরতে হবে। আজ মেঘনার বুকে ভাসতে ভাসতে যেন আমার প্রশ্নের উত্তর পেলাম। হঠাৎ যেন বুঝতে পারলাম এমন দেশের মুক্তির জন্য যে কোনো মূল্য দেয়া যায়।’
এখানে এসে অনিতা তার মায়ের বান্ধবী এবং তার মেয়ে নাজমা ও পুত্র সুমিতের সাথে পরিচিত হয়। সুমিত পেশায় একজন সাংবাদিক। পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী এবং তাদের দোসরদের অত্যাচার ও নির্যাতনের বিভিন্ন দৃশ্য দেখে এবং কাহিনী শুনে অনিতা ভীষণ আবেগ তাড়িত হয়। তার হৃদয় গভীর মানবিকতা বোধে আচ্ছন্ন হয়। যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশ থেকে নতুন অভিজ্ঞতা নিয়ে সে তার দেশ ভারতে ফিরে যায়। ধীরে বহে মেঘনা চলচ্চিত্র প্রসঙ্গে সমালোচক আপন চৌধুরী বলেন, ধীরে বহে মেঘনা’র শেষ দৃশ্যের শটগুলোতে দেখানো হয় লং শটে ইন্ডিয়ান ইয়ার লাইন্সের বোয়িং বিমান অনিতাকে নিয়ে আকাশে উড়লো। ঢাকার বুকে সন্ধ্যা নেমে আসার প্রস্তুতি চলছে। বুড়িগঙ্গার ওপারে সূর্যাস্তের আভা। ঘিঞ্জি পুরানো ঢাকার একফালি আকাশ ধীরে ধীরে মøান হয়ে আসছে। রাস্তার ধারে হাপরের আগুন জ¦লছে দাউ দাউ করে। আর বুড়িগঙ্গার জলে অস্তমিত সূর্যের প্রতিবিম্ব জ¦লছে ঝিকমিক। চমৎকার কয়েকটি ইমেজ নতুন আশাবাদের জন্ম দেয়। এটি ঢাকায় নির্মিত অন্যান্য ছবির চাইতে উন্নতমানের। অন্যান্য ছবির নির্মাণ পদ্ধতি যাত্রাধর্মী হওয়ায় চলচ্চৈত্রিক উপাদান নির্ভর ছবিটি অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে।
আলমগীর কবির পেশায় একজন সাংবাদিক ছিলেন এবং তিনি নিজে মুক্তিযুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেন। তাই তাঁর নির্মিত ধীরে বহে মেঘনা যেন সে সাংবাদিক এবং মুক্তিযোদ্ধারই চিত্র। মুক্তিযুদ্ধের ধ্বংসলীলা ও মানসিক বিপর্যয়কে তিনি প্রামাণ্য ও কল্পনার মাধ্যমে এ চলচ্চিত্রে উপস্থাপন করেছেন। ছবিটি প্রামাণ্য বা তথ্যচিত্রের আঙ্গিকে উপস্থাপিত। চলচ্চিত্রটির নির্মাণশৈলীতে একজন আধুনিক নির্মাতার ছাপ লক্ষণীয়। বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের ইতিহাসে ধীরে বহে মেঘনা চলচ্চিত্রটি এক ভিন্নধর্মী প্রকরণ বা সেলুলয়েডিক স্টাইল। এই প্রামাণ্যের শরীরে টুকরো টুকরো ইমেজ-এর যোজনে গড়ে ওঠে ফিকশানের একটি পূর্ণাঙ্গ অর্গানিক কাঠামো। সামগ্রিক অর্থেই, ধীরে বহে মেঘনা Creative fiction of actuality প্রামাণ্য আর কাহিনিচিত্রের এক অদ্বৈত অথচ নবতর চলচ্চৈত্রিক ভাষা।
ধীরে বহে মেঘনা চলচ্চিত্রের পটভূমিতে দেখি মুক্তিযুদ্ধ-উত্তর বাংলাদেশ, যে বাংলাদেশ সদ্য সমাপ্ত হওয়া যুদ্ধের ক্ষতচিহ্ন কাটিয়ে উঠেনি তখনও। এই চলচ্চিত্রের চরিত্রগুলো বার বারই ফিরে গেছে যুদ্ধের উত্তাল দিনগুলোতে কখনও আত্মকথনে, কখনও যুদ্ধকালীন প্রামাণ্যচিত্রের রাশফুটেজ অবলোকনের মধ্য দিয়ে, আবার কখনও স্মৃতিচারণের মধ্য দিয়ে ফ্ল্যাশব্যাকের পাখায় বর করে। ধীরে বহে মেঘনা চলচ্চিত্রটি এক ধরনের ডকুমেন্টারি। এর প্রত্যেকটি ঘটনা সত্যি, যদিও কিছু কিছু সংলাপ পরিচালকের স্বলিখিত। অনিতাকে মুক্তিযুদ্ধের সময়কার কিছু প্রামাণ্যচিত্রের রাশ দেখানোর সিচুয়েশন তৈরি এবং সে রাশ দেখানোর মাঝে সুমিতের ন্যারেশনে ’৭১-এর ভয়াবহ কিছু ছবি যেমন: চোখবাঁধা অবস্থায় নিহত বুদ্ধিজীবী, পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ধ্বংসযজ্ঞ, সম্পূর্ণ সিকোয়েন্সটি নিঃসন্দেহে সিনেমা ভেরিতের বুদ্ধিদীপ্ত এক ব্যবহার।
চলচ্চিত্রের একটি দৃশ্যে রহিমুল্লাহর এক প্রশ্নের জবাবে সুমিতকে আমরা বলতে দেখি, ‘দেখুন, দেশপ্রেম শব্দটা বড় গোলমেলে। এরই নামে ইয়াহিয়া খান এদেশের ত্রিশ লক্ষ পুরুষ, মহিলা আর শিশুকে হত্যা করেছে। এরই নামে দালালরা বিহারিদের উত্তেজিত করেছে বাঙালিদের হত্যা করতে। আবার এরই জন্যে লক্ষ লক্ষ বীর বাঙালি অস্ত্র তুলে নিয়েছে এবং জীবন দিয়ে দেশকে মুক্ত করেছে।’ রহিমুল্লাহর আরেকটি প্রশ্নের জবাবে সুমিত বলেন, …বাঙালির মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাস কেবলমাত্র দু’এক বছর বা দু’এক দশকের ইতিহাস নয়। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বাংলার নিরীহ, শান্তিপ্রিয় মানুষ বিদেশি এবং দেশি শোষকদের অকথ্য অত্যাচার সহ্য করে সংগ্রাম চালিয়ে এসেছে শোষণের বিরুদ্ধে, কুসংস্কারের বিরুদ্ধে, ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে, সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে। সত্যি কথা বলতে কি আজকের স্বাধীন বাংলাদেশ সত্যিকারের জয়ের পথে প্রথম পদক্ষেপ মাত্র। এর পরের লক্ষ্য একটি শোষণহীন সমাজ ব্যবস্থা। এরই মধ্য দিয়ে বাঙালিকে অনুপ্রেরণা যোগাতে হবে বিশে^র লক্ষকোটি নিপীড়িত মানুষের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী, বর্ণ-বৈষম্যবিরোধী এবং শোষণ বিরোধী সংগ্রামে।
সুমিতের বর্ণনার প্রেক্ষিতে পরিচালক প্রামাণ্যচিত্রে দেখিয়ে যান: মুক্তিবাহিনীর ক্যাম্পে গেরিলা যুদ্ধের ট্রেনিং, গণহত্যা, পরাজিত পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পণ, যৌথ কনভয়ের অগ্রগতি, বিধ্বস্ত জনপদ, ব্রিজ, রেলগাড়ি, দালানকোঠা; মুক্ত যশোরে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদ ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দের বক্তৃতা, মুজিবনগর সরকারের ঢাকা প্রত্যাবর্তন, মিত্রবাহিনীর সৈন্যদের সাথে স্থানীয় মানুষের করমর্দন; যা আমাদের অনেক দুঃখে গড়া ইতিহাস, নয় মাসের সে প্রামাণ্য দৃশ্যাবলিকে সিনেমা-ভেরিতে স্টাইল পূণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রের শরীরে আলমগীর কবির গেঁথে দিয়েছেন, যে কাজটি করতে তিনি অত্যন্ত দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। চলচ্চিত্রটি পরিচালক আলমগীর কবিরকে ব্যতিক্রমধর্মী পরিচালক হিসেবে ১৯৭২ ও ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে বাচসাস পুরস্কার এনে দিয়েছিল।
লেখক : শিক্ষক, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়