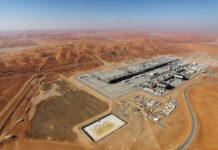সৈয়দ আসাদুজ্জামান সুহান :
স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শক্তিমান কবি ও প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ। মার্কিন বর্ণবাদবিরোধী অবিসংবাদিত নেতা মার্টিন লুথার কিংকে বলা হতো মুকুটবিহীন সম্রাট। ঠিক তেমনি বাংলা সাহিত্যে সত্তরের দশকের মুকুটহীন সম্রাট ছিলেন বিপ্লবী কবি রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ। কবি আল মাহমুদের পর তিনিই দুই বাংলায় সমানভাবে জনপ্রিয় এবং শক্তিমান কবি হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন। তবে তাঁর নামের পাশে নেই বড় কোনো তকমা বা পদক। এতে করে কবি কোনোভাবেই খাটো হননি; বরং যেসব প্রতিষ্ঠান কবিকে সম্মান জানাতে পারেনি, তাদের নিয়েই প্রশ্নটা উঠেছে।
রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহর সমকালীন অনেক কবির নামের পাশে অনেক বড় বড় পদক শোভা পেলেও জনপ্রিয়তায় তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই। জীবিত থাকতে তিনি যতটা জনপ্রিয় ছিলেন, মৃত্যুর পর তিনি তার চেয়েও বেশি জনপ্রিয় হন। ঘুণে ধরা জীর্ণ সমাজকে বদলে দিতেই এই স্বল্পপ্রাণ কবির জন্ম হয়েছিল। ১৯৭৫ থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত দেশে এমন কোনো আন্দোলন নেই, যেখানে কবির অংশগ্রহণ ছিল না। অপশক্তির বিরুদ্ধে তিনি প্রতিবাদী কবিতা লিখেছেন। মুক্ত মঞ্চে সেই প্রতিবাদী কবিতা আবৃত্তি করে সাধারণ মানুষের ভেতরে প্রতিবাদী সত্তা জাগ্রত করার নিরন্তর চেষ্টা করেছেন। তাঁর মননে ছিল কবিতা, আবৃত্তিতে অনলবার্তা আর রক্তে প্রবাহিত বিদ্রোহের লাভা। মৃত্যুতে তাঁর সংগ্রামী জীবনের অবসান হলেও তাঁর প্রতিবাদী কবিতাগুলো আজও পাঠক হৃদয় আন্দোলিত করে। কবিতা, গল্প, কাব্যনাট্য, প্রবন্ধ, গান-যেখানেই শিল্প-সাহিত্য; সেখানেই রুদ্র। তিনি ভক্তদের হৃদয় সিংহাসনে কবিতার রাজপুত্র হয়ে বসে আছেন। তাঁকে আখ্যায়িত করা হয় বাংলা কাব্য সাহিত্যের ‘প্রতিবাদী রোমান্টিক কবি’ হিসেবে।
১৯৫৬ সালের ১৬ অক্টোবর বরিশাল রেডক্রস হাসপাতালে রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবার নাম শেখ ওয়ালীউল্লাহ; মায়ের নাম শিরিয়া বেগম। তাঁদের স্থায়ী নিবাস ছিল বাগেরহাট জেলার মংলা থানার সাহেবের মেঠ গ্রামে। রুদ্রর নিজ বাড়ি সাহেবের মেঠ থেকে তার নানা বাড়ি মিঠেখালি খুব বেশি দূরে ছিল না। রুদ্রর লেখাপড়ায় হাতেখড়ি ও লেখালেখিতে আগ্রহ দুটোই তৈরি হয় এই নানাবাড়িতে। সে সময় ঢাকার বিখ্যাত ‘বেগম’ ও কলকাতার ‘শিশুভারতী’ পত্রিকা রাখা হতো তাঁর নানাবাড়িতে। সেই সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ, নজরুলের পাশাপাশি বিভিন্ন বিখ্যাত লেখকদের বইপত্র তো ছিলই। রুদ্র এসব বইয়ের রাজ্যে মজে যান। নানাবাড়ির পাঠশালায় তৃতীয় শ্রেণি অবধি পড়েন রুদ্র। এরপর ১৯৬৬ সালে চতুর্থ শ্রেণিতে ভর্তি হন মোংলা থানা সদরের সেন্ট পলস স্কুলে।
১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ায় তাঁর আর নবম শ্রেণিতে পড়া হয়নি। যুদ্ধ শেষে নবম শ্রেণি টপকে কবি ১০ম শ্রেণিতে ভর্তি হন ঢাকার ওয়েস্ট অ্যান্ড হাই স্কুলে। এখান থেকেই ১৯৭৩ সালে চারটি বিষয়ে লেটার মার্কসহ বিজ্ঞান শাখা থেকে প্রথম বিভাগে এসএসসি পাস করেন রুদ্র। এরপর ভর্তি হন ঢাকা কলেজে। মা-বাবার ইচ্ছা ছিল, রুদ্র ডাক্তার হোক। কিন্তু রুদ্র বিজ্ঞানের পথে আর না গিয়ে তাঁর পছন্দের মানবিক শাখায় চলে এলেন।
ঢাকা কলেজে এসে রুদ্র পুরোপুরি সাহিত্যচর্চায় মনোনিবেশ করলেন। সহপাঠী হিসেবে পেলেন কামাল চৌধুরী, আলী রিয়াজ, জাফর ওয়াজেদ, ইসহাক খানসহ একঝাঁক তরুণ সাহিত্যকর্মীকে। ১৯৭৫ সালে রুদ্র উচ্চমাধ্যমিক পাস করেন দ্বিতীয় বিভাগ নিয়ে। এরপর তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্সে ভর্তি হন বাংলা বিভাগে। ১৯৭৮ সালে রুদ্র ডাকসু নির্বাচনে অংশ নেন, বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের মনোনয়নে সাহিত্য সম্পাদক পদে। রুদ্র সরাসরি কখনো রাজনীতিতে না এলেও ডাকসু নির্বাচনে অংশ নিয়ে প্রকাশ করেন তার রাজনৈতিক বিশ্বাস। সেই বিশ্বাস টিকে ছিল জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত। ১৯৭৯ সালে রুদ্রর অনার্স পরীক্ষা দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু ক্লাসে উপস্থিতির হার কম থাকায় বাংলা বিভাগের তৎকালীন চেয়ারম্যান ডক্টর আহমদ শরীফ তাঁকে পরীক্ষা দেওয়ার অনুমতি দেননি। পরের বছর, ১৯৮০ সালে তিনি অনার্স পাস করেন। এরপর নানা রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যিক আন্দোলনে জড়িয়ে পড়ার কারণে প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশোনায় আবারও পিছিয়ে পড়েন রুদ্র। পরিশেষে ১৯৮৩ সালে রুদ্র এমএ ডিগ্রি নেন।
রুদ্রর পিতৃপ্রদত্ত নাম মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ। ছোটবেলায় এই নামেই তিনি পরিচিত ছিলেন। লেখালেখির জগতে এসে নামটি তিনি নিজেই বদলে দেন। নামের আগে যোগ করেন ‘রুদ্র’, ‘মোহাম্মদ’-কে করেন ‘মুহম্মদ’ ও ‘শহীদুল্লাহ’-কে ‘শহিদুল্লাহ’। নিজ-প্রদত্ত এই নাম শুধু লেখক হিসেবেই নয়, পরীক্ষার সনদেও তিনি ব্যবহার করেছেন। কবির ভীষণ এক খামখেয়ালির জীবন ছিল। মুক্ত স্বাধীন পাখির মতোই ডানা মেলে এখানে-ওখানে ঘুরতেন। তিনি ছিলেন নিখাদ ভবঘুরে। পারিবারিক সচ্ছলতা ছিল; কিন্তু তিনি সে পথে যাননি। চাকরির প্রাতিষ্ঠানিকতায় নিজেকে বাঁধেননি। কয়েকটা রিকশা ছিল, তা থেকে যা আয় হতো, তাতেই চলতেন। ঠিকাদারি করেছেন, চিংড়ির খামার করেছেন। কিন্তু শৃঙ্খলহীন জীবনের কারণে সফলতা পাননি। পাঞ্জাবি আর জিন্স প্যান্টের যুগলবন্দি তখন বোধ হয় তিনি একাই ছিলেন। তাঁর ছিল অতি মাত্রায় মদ্য প্রীতি। প্রতি সন্ধ্যায় হাটখোলার নন্দের দোকানে হাজিরা দিতেই হতো তাঁর। হুইস্কির বাংলাকরণ করেছিলেন ‘সোনালী শিশির’। এই নামে একটা গল্পও লিখেছিলেন।
জীবন নিয়ে রুদ্র যত হেলাফেলাই করুন না কেন কবিতা নিয়ে কখনো করেননি। কবিতায় তিনি সুস্থ ছিলেন, নিষ্ঠ ছিলেন, স্বপ্নময় ছিলেন। ১৯৭৯ সালে বের হয় রুদ্রর প্রথম কাব্যগ্রন্থ ‘উপদ্রুত উপকূলে’। প্রথম কাব্যগ্রন্থে প্রকাশিত হয় তাঁর বিখ্যাত কবিতা ‘বাতাসে লাশের গন্ধ’। প্রথম বইটির প্রকাশক ছিলেন আহমদ ছফা। ১৯৮১ সালে প্রকাশিত হয় দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ ‘ফিরে চাই স্বর্ণগ্রাম’। তারপর একে একে ‘মানুষের মানচিত্র’ (১৯৮৪), ‘ছোবল’ (১৯৮৬), ‘গল্প’ (১৯৮৭), ‘দিয়েছিলে সকল আকাশ’ (১৯৮৮), ‘মৌলিক মুখোশ’ (১৯৯০)। কবির জীবদ্দশায় মোট সাতটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়; মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয় নাট্যকাব্য ‘বিষ বিরিক্ষের বীজ’।
রুদ্র যেমন খ্যাতিমান কবি ছিলেন, তেমনিভাবে খ্যাতিমান আবৃত্তিকার, গীতিকার ও সুরকারও ছিলেন। তিনি প্রায় অর্ধশতাধিক গান রচনা ও সুরারোপ করেছেন। কবির কালজয়ী কবিতা, পরে সর্বাধিক জনপ্রিয় বাংলা গান ‘আমার ভিতরে বাহিরে অন্তরে অন্তরে’ কবিকে অমরত্ব এনে দেয়। বাংলায় এমন কাউকে খুঁজে পাওয়া মুশকিল হবে, যিনি এই গানটি শোনেননি। দুই বাংলায় এই গানটি যেমন জনপ্রিয়, তেমনি বেশ আলোচিতও। তিনি ‘অন্তর বাজাও’ নামে একটি গানের দল গড়েছিলেন। এই গানের দল নিয়ে দেশের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়িয়েছেন। শেষ জীবনে ফিল্ম বানাতে চেয়েছিলেন কিন্তু অকালমৃত্যু পথ আটকে দিল। রুদ্র ছিলেন জাতীয় কবিতা পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা-যুগ্ম সম্পাদক, সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের প্রথম আহ্বায়ক কমিটির সদস্য এবং বাংলাদেশ সংগীত পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ও প্রকাশনা সচিব।
১৯৮১ সালের ২৯ জানুয়ারি, সামাজিক প্রথা ভেঙে অভিভাবকের অমতে তসলিমা নাসরিনকে বিয়ে করেছিলেন। তসলিমা মূলত ছিলেন একজন চিকিৎসক। ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ থেকে এমবিবিএস ডিগ্রি নিয়ে তিনি মিটফোর্ড হাসপাতালের মেডিকেল অফিসার হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন। রুদ্র ও তসলিমার পরিচয় লেখালেখির সূত্র ধরে। পরিচয় ক্রমে রূপ নেয় প্রণয়ে। রুদ্র-তসলিমার দাম্পত্য জীবন ভালোই কাটছিল। রুদ্রের উৎসাহ ও প্রেরণায় তসলিমাও পুরোপুরি জড়িয়ে যান লেখার জগতের সঙ্গে। তসলিমা চেয়েছিলেন রুদ্রের মতো বন্য পাখিকে সংসারের খাঁচায় বন্দি করে রাখতে। রুদ্রের শৃঙ্খলহীন জীবনে সংসারের খাঁচায় বন্দি হওয়াটা ছিল অসম্ভব। ছয় বছরের দাম্পত্য জীবন শেষে তাঁরা আলাদা হয়ে যান। ১৯৮৬ সালে উভয়ের সম্মতিতে তাঁদের বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে।
তারপর রুদ্র ভীষণ একাকিত্ব অনুভব করেন। তিনি আগের চেয়ে আরও বেশি বেপরোয়া হয়ে ওঠেন। শরীরের ওপর যথেচ্ছ অত্যাচার শুরু করেন। প্রচুর ধূমপান ও মদ্যপান, খাবারে অনিয়ম সব মিলিয়ে বাধিয়েছিলেন পাকস্থলীর আলসার। পায়ের আঙুলে হয়েছিল বার্জার্স ডিজিজ। শারীরিক অসুস্থতাকে তিনি গুরুত্ব দিতেন না। অসুস্থতা নিয়েও তিনি ঢাকায় ও ঢাকার বাইরে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে কবিতা পড়তে যেতেন। জীবনের শেষ পর্যায়ে তিনি নিয়মিত আসতেন নীলক্ষেত-বাবুপুরায় কবি অসীম সাহার ‘ইত্যাদি’ প্রকাশনীতে। কবির অগণিত বন্ধুবান্ধব থাকা সত্ত্বেও এই সময়টায় তিনি অনেক বেশি নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েন। একদিন গুরুতর অসুস্থ হলে কবির স্থান হয় হলি ফ্যামিলির ২৩১ নম্বর কেবিনে। হাসপাতালে সপ্তাহখানেক থেকে পুরোপুরি সুস্থ হয়ে ২০ জুন রুদ্র বাসায় ফেরেন। পরের দিন ২১ জুন ভোরে দাঁত ব্রাশ করতে করতে অজ্ঞান হয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন কবি রুদ্র মোহাম্মদ শহিদুল্লাহ।
অকালপ্রয়াত এই কবি তাঁর কাব্যযাত্রায় যুগপৎ ধারণ করেছেন দ্রোহ ও প্রেম, স্বপ্ন ও সংগ্রামের শিল্পভাষ্য। ‘জাতির পতাকা আজ খামচে ধরেছে সেই পুরোনো শকুন’ এই নির্মম সত্য অবলোকনের পাশাপাশি ততোধিক স্পর্ধায় তিনি উচ্চারণ করেছেন, ‘ভুল মানুষের কাছে নতজানু নই’। যাবতীয় অসাম্য, শোষণ ও ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে অনমনীয় অবস্থান তাঁকে পরিণত করেছে ‘তারুণ্যের দীপ্ত প্রতীকে’। একই সঙ্গে তাঁর কাব্যের আরেক প্রান্তরজুড়ে রয়েছে স্বপ্ন, প্রেম ও সুন্দরের মগ্নতা। সাহিত্য সমালোচকদের মতে, তিনি ছিলেন সত্তর দশকের অন্যতম কবি। তবে পাঠকের বিবেচনায় তিনি বিংশ শতাব্দীর অন্যতম কবি। ওপারে কবি ভালো থাকুক, তাঁর প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা।