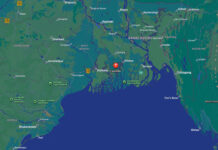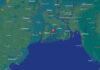ড. শ্যামল কান্তি দত্ত »
পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমানের এক অখ্যাত গ্রামে জন্ম নজরুলের। অল্প বয়সে পিতৃহারা। পারিবারিক স্নেহবঞ্চিত, নিয়মিত অভিভাবকহীন অনাদরে বেড়ে ওঠা। টুকটাক পড়াশোনা; পাশাপাশি বাবুর্চিগিরি, হাটে-বাজারে ফাই-ফরমাশ খাটা; রুটির দোকানে চাকরি, কখনো বর্ধমানে, কখনোবা ময়মনসিংহ-ত্রিশাল-দরিরামপুরে; আবার রানিগঞ্জে ফিরে আসা, স্কুলে ক্লাস এইটে ভর্তি হওয়া; রুশ বিপ্লবের বছরে (১৯১৭) আঠারো বছর বয়সে ম্যাট্রিক পরীক্ষা না দিয়েই প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তড়িঘড়ি গজিয়ে ওঠা বাঙালি পল্টনে যোগ দিয়ে নওশেরায় ছোটখাটো শিক্ষানবিশী শেষে দুবছরের মতো একটানা করাচির সেনাছাউনিতে যুদ্ধে প্রস্তুতি নিতে থাকা। একদা লেটোর দলভুক্ত কিশোরের মানস-পটভূমি যেন ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিক ভূমিকা পালনের জন্যেই তৈরি হয়েছিল। ভাগ্য তাঁকে টেনে নিয়ে গেল পল্টনে। বড় শহরের নাগরিক বেষ্টনীতে তাঁর ভেতরেও গড়ে ওঠে বিশেষ এক পাঁচমিশেলি জীবনযাত্রা। সেখান থেকেই দু-চারটে নাগরিক-কবিতা রচনায় হাতেখড়ি। লোককবি হওয়ার সম্ভাবনারও সেখানেই ইতি। নজরুল পেশাদার সৈনিক ছিলেন না। সরাসরি রণাঙ্গনেও যাননি। কিন্তু তাঁরই মতো অপেশাদার লেখাপড়া জানা সৈনিকদের ছাউনিতে কাটিয়ে এসেছেন প্রায় তিন বছর। করাচিতে থাকায় অনেকটা আরবি-ফারসি ভাষা ও সংস্কৃতির পরিমণ্ডলে ছিল তাঁর বসবাস। লেগে থেকে ফারসি শেখেন তিনি করাচিতেই। এদিকে বিশ্বযুদ্ধের অবসান ঘটে ১৯১৮-তে। অস্থায়ীভাবে গড়ে ওঠা সেনাছাউনি গোটাতে কেটে যায় একটা বছর। জানুয়ারি ১৯২০-এ তিনি ফিরে আসেন কলকাতায়। কবির নিরাশ্রয়ী জীবনে তখন অন্যতম সহায় সমাজতন্ত্রী ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ মুজফফর আহমদ (১৮৮৯-১৯৭৩)। তাঁরই হাত ধরে সংযুক্ত ও নিবিষ্ট হন সাংবাদিকতায়। এই সুবাদে আবার পেয়েছেন সাধারণ মানুষের সান্নিধ্য, লোকভাষার স্পর্শ।
উনিশ শতকে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে যুগসন্ধিকালের কবি ঈশ^রচন্দ্র গুপ্ত (১৮১২-১৮৫৯) যেমন কলকাতার জীবন প্রত্যক্ষ করেনÑ লেখেন, ‘রেতে মশা দিনে মাছি,/ এই নিয়ে কলকেতা আছি ॥’ নজরুলও প্রায় একই অভিজ্ঞতা অর্জন করলেন আধুনিক যুগে অবস্থান করে। তবে আধুনিক যুগে অবস্থান আর নাগরিক বিশ্বরাজনীতির অভিজ্ঞতা তাঁর কাব্যভাষাকে গ্রাম্যতা থেকে মুক্ত করে লোকভাষার মিশল সমকালীন নাগরিক ভাষায় এক শৈলীময় স্বকীয়তায় সমৃদ্ধ করে তোলে। আমরা জানি, কবির একান্ত লৌকিক অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়েই জন্ম নেয় কবিতার ভাষা। ভাষাই কবির আত্মা, আবার ভাষাই কাল-কালান্তরের স্মারক। বুদ্ধিজীবীমহলে বদ্ধমূল বিশ্বাস যে, কবিতার ভাষা হবে চলতি বুলি থেকে স্বতন্ত্র এবং কাব্যের জগতে থাকবে একটি স্বপ্নময়তা। নজরুল চলতি সমস্যাকে চলতি বুলিতেই উচ্চারণ করেন, সাথে সাথে তাঁর পাঠককে স্বপ্নময়তায় নিমগ্ন করেন নিমিষেই। অবশ্য এই স্বপ্নময়তার কারণ যে রোম্যান্টিক যুগের প্রেরণা তা বলার অপেক্ষা রাখে না।
রবীন্দ্র-নজরুল জন্মানোর আগেই উনিশ শতকের প্রথমভাগে ইউরোপে রোম্যান্টিক আন্দোলন পূর্ণতা পায়। রোম্যান্টিকতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য অমিত সম্ভাবনা নিয়ে ব্যক্তির আত্মঘোষণা। তার পেছনে ছিল যুগান্তকারী ঘটনা হিসেবে ফরাসি বিপ্লব ও ইংল্যান্ডের শিল্পবিপ্লব। ফরাসি বিপ্লবের পর মানবাধিকার সনদের ঘোষণা এক রকম ধর্মীয় ও সামন্ততান্ত্রিক বাধা থেকে ব্যক্তির মুক্তির স্বীকৃতি আনল। ব্যক্তির মুক্তির সঙ্গে মানবমুক্তির আকাক্সক্ষা এই ভূখণ্ডেও অনেক অনুভূতিপ্রবণ ব্যক্তির চৈতন্যে জোয়ার জাগায়। নজরুলের শিল্পীসত্তার মৌল প্রবণতা হিসেবে রোমান্টিকতার দুই প্রধান প্রান্তও ‘বিদ্রোহী’-তে উচ্চকিত হয়ে আছে। তাঁর প্রতিনিধিত্বশীল একটি পঙ্ক্তি: ‘মম এক হাতে বাঁকা বাঁশের বাঁশরী, আর হাতে রণ-তূর্য!’ পৌরাণিক কৃষ্ণের দুই রূপ হলেও তা ধারণ করে আছে রোমান্টিসিজমেরও দুই বৈশিষ্ট্য; প্রণয় আর মুক্তিকামী সংগ্রাম। এখানেই উগ্র জঙ্গিবাদী যোদ্ধা থেকে মুক্তিকামী শিল্পীর প্রভূত পার্থক্য। তিনি রণে নামেন মানুষকে ভালোবেসে, মানবতার মুক্তির আকাক্সক্ষায়। এতে চিত্রিত ও আবিষ্কৃত হয়েছে ইউরোপের রেনেসাঁ-উদ্ভূত প্রবল পরাক্রমশালী মানুষেরই শক্তিমান রূপ, তার বীরত্বব্যঞ্জকতা: ‘আমি সহসা আমারে চিনেছি আমার খুলিয়া গিয়াছে সব বাঁধ!’ সক্রেটিস বলেন, ‘নো দাইসেল্ফ’। উপনিষদ বলে, ‘আত্মানাং বিদ্ধি’। অর্থাৎ নিজেকে জানো। নজরুল নিজের পরিচয় জেনেছেন, পাঠককে জানিয়েছেন; সর্বোপরি পাঠকের অহমবোধ জাগ্রত করতে ১৪১ পংক্তির কবিতায় ১৪৫ বার ‘আমি’ শব্দ ব্যবহারের পাশাপাশি আরও ষোলো বার ‘আপনার’, ‘আমার’ ও ‘মম’ সর্বনাম পদ ব্যবহার করেছেন।
গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আত্মার অবিনাশিতা বিষয়ে শিষ্য অর্জুনকে পরামর্শ দিতে গিয়ে তাঁর নিজের স্বরূপ-পরিচয় বর্ণনা প্রসঙ্গে বারে বারে ‘আমি’, ‘আমাকে’ ও ‘আমায়’ ইত্যাদি ব্যবহার করেছেন। বলা বাহুল্য গীতা সংস্কৃত ভাষায় রচিত। সংস্কৃত অহম্ প্রাকৃত ভাষায় হয় অম্হি, এর অপভ্রংশ-রূপ আহ্মি থেকে বাংলায় আমি। নজরুল কাব্যিক ‘মম’ আটবার ব্যবহার করলেও, বাংলা ভাষার বহুল ব্যবহৃত আমি রূপটাই বেশি ব্যবহার করেছেন।
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও একুশ বছর বয়সে তাঁর আমি-কে প্রকাশ করেছেন প্রভাতসংগীত (১৮৮২) কাব্যগ্রন্থের ‘নির্ঝরের সপ্নভঙ্গ’ কবিতায়। প্রকৃতির আভাসে-ইঙ্গিতে তাঁর মধ্যে যে কবিপ্রতিভা রয়েছে তা চিনতে পারছেন, অনুভব করতে পারছেন, তাঁর প্রতিভা বিকশিত-প্রকাশিত হতে ব্যাকুল হয়ে ওঠে বলে : ‘আমি ঢালিব করুণাধারা/ আমি ভাঙিব পাষাণকারা/ আমি জগৎ প্লাবিয়া বেড়াব গাহিয়া/ আকুল পাগল-পারা।’ রবীন্দ্রনাথের প্রতিনিধিত্বশীল এ-কবিতায় কবির অন্তরে বিশ্বের সমস্ত আনন্দ ও সৌন্দর্য যেনো সমুজ্জ্বল হয়ে উঠলো। তবে বিশ শতকের প্রথম দশকেই পূজা পর্যায়ের গানে রবীন্দ্রনাথ গাইলেন : ‘ওগো মরুক না এই আমি’ (রবীন্দ্র, ১৯১০); আরও পরে নিজেকে উজাড় করে দিয়ে গাইলেন : ‘আমার কাছে আমি ছিল সবার চেয়ে দামি’ (রবীন্দ্র, ১৯১৯)। নজরুলের আমি সঙ্গতভাবেই রবির আমি থেকে অনেক আলাদা। ভাষা ও বক্তব্যে তিনি স্বাভাবিকভাবেই রবীন্দ্রবলয় থেকে বহুদূরে। নজরুলের বিদ্রোহ হচ্ছে চেতনাগত বিদ্রোহ। হিন্দু-মুসলিম মিলনের মধ্য দিয়ে তিনি জাতীয় ঐক্য ও সংহতির ডাক দিয়েছেন। কাল পরম্পরায় জাতীয় ঐক্যের এই অনুভবই কবির চেতনাগত বিদ্রোহ। বিদ্রোহে তাঁর চাই আপনশক্তিতে আস্থা। এই শক্তিকে তিনি খুঁজেছেন পৌরাণিক আবহে; শুধু ভারতীয় পুরাণের মধ্যে নয়, তাঁর আরাধ্য হয়েছে আরবীয় এবং গ্রিক পুরাণও। আরবীয় পুরাণ প্রয়োগের কবিতাপাঠে বাঙালি মুসলিমের মধ্যেও বাংলা ভাষার প্রতি দরদ গড়ে ওঠে। বাংলার সাধারণ মুসলমানের বাঙালি পরিচয়ের ক্ষেত্রে ভাষাও একটি বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের আনুকূল্যে উনিশ শতকজুড়ে বাংলা ভাষার লেখ্যরূপে যে সংস্কৃতায়ন ঘটে, তা বাঙালি মুসলমানকে সাহিত্যের মূলস্রোত থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। নজরুল তাঁর তারুণ্যের উদ্দামতা দিয়ে, চিন্তার বৈশ্বিক ঔদার্য দিয়ে, অসাম্প্রদায়িকতার আন্তরিকতা দিয়ে, মানবিকতার বিশ্বপ্রসারিত দৃষ্টিকোণ দিয়েÑ সর্বোপরি, স্বকীয় ভাষাভঙ্গি দিয়ে নিঃসংকোচে বাংলা সাহিত্যের মূল আসরে নিজ শক্তি বলেই আসন করে নেন। ‘বিদ্রোহী’ কবিতার ভূমিকা এ ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে তাৎপর্যপূর্ণ। ভারতীয়, আরবীয় ও ইউরোপীয় এই ত্রিমাত্রিক ঐতিহ্যকে ধারণ করেই তাঁর প্রতিভা পূর্ণতা পেয়েছে। বাংলা কবিতার আসরে এ-কণ্ঠস্বর অভিনব; কালের স্পন্দনকে ধারণ করেও কালোত্তীর্ণ। ফলে বাংলা কাব্যভাষার পালাবদলেও ‘বিদ্রোহী’ কবিতা পালন করে এক অমোঘ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা।
এই পালাবদলকে সে সময় অনেকে বিদ্রুপ করলেও স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁকে স্বাগত জানিয়েছেন। নজরুলের কবিতা প্রসঙ্গে তিনি লেখেন, ‘… কৃত্রিমতার ছোঁয়াচ তাকে কোথাও ম্লান করেনি, জীবন ও যৌবনের সকল ধর্মকে কোথাও তা অস্বীকার করেনি। মানুষের স্বভাব ও সহজাত প্রকৃতির অকুণ্ঠ প্রকাশের ভিতর নজরুল ইসলামের কবিতা সকল দ্বিধা-দ্বন্দ্বের ঊর্ধ্বে তার আসন গ্রহণ করেছে। বিদগ্ধ বাগবিন্যাসের যেমন মূল্য আছে, সহজ সরল তীব্র ও ঋজু বাক্যের মূল্যও কিছু কম নয়। … তীব্রতাও রসাত্মক হলেই কাব্য হয়ে ওঠে, যেমন উঠেছে নজরুলের বেলায়।’ বিদ্রোহের প্রচণ্ড তীব্রতা নিয়ে নজরুলের বিপ্লবী বীর ঘোষণা করে : ‘আমি বিদ্রোহী ভৃগু, ভগবান বুকে এঁকে দিই পদ-চিহ্ন,’ আবার একই কবিতায় সে বলে, ‘ চিত চুম্বন-চোর কম্পন আমি থর-থর-থর প্রথম পরশ কুমারীর!/ আমি গোপন-প্রিয়ার চকিত চাহনি, ছল-ক’রে দেখা অনুখন,’। এভাবে নজরুল এক গণ্ডুষে পান করেন বৈপরীত্যের সমগ্রতা। এমনকি একই পঙক্তিতে তিনি বৈপরীত্যকে ঠাঁই দেন : ‘আমি সৃষ্টি, আমি ধ্বংস, আমি লোকালয়, আমি শ্মশান, আমি অবসান, নিশাবসান।’ বৈপরীত্যের মধ্যে মহাবিশ্বকে তিনি ধারণ করে তাঁর কাব্যশৈলীকে পৌঁছে দেনÑ অননুকরণীয় সাফল্যের চূড়ায়। এ যুগের কবি ও কাব্যসমালোচকে তাই বলতে শুনি : নজরুল সেসব বিরল কবির একজন, যাঁরা তাঁদের কাব্যভাষার স্বাতন্ত্র্যকে নিজেরাই চূড়ায় তুলে দিয়েছেন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এমন সিদ্ধি অর্জন করেছেন, যা নজরুলের পক্ষেও পরে আর অতিক্রম করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। যেমন ‘বিদ্রোহী’ কবিতার ভাষিক নির্মিতি। সমগ্র বাংলা ভাষায় ‘বিদ্রোহী’র মতো শিখরস্পর্শী কাব্যভাষা তার আগে বা পরে আর পাওয়া যায় না। শুধু ভাষায় নয়, ভাবনাতেও এ নতুন। নজরুল কেবল ভাবনার নতুনত্বে থেমে থাকেননি, তিনি কর্মের আহ্বান জানিয়েছেন। কর্মের কথাও তিনি বলেছেন, বীররসে উজ্জীবিত কর্মী-কবি বাঙালিকে কর্মে কামিয়াব করতেÑব্যবহার করেছেন বিচিত্র ক্রিয়াপদ।
বিদ্রোহী কবিতায় একাত্তরটি ক্রিয়াপদ আছে। এর মধ্যে চলিত ভাষার পাশাপাশি কিছু সাধুভাষার ক্রিয়াপদও আছে যেমন : ‘উঠিয়াছি’, ‘ছেদিয়া’, ‘ভেদিয়া’, ‘চাহে’, ‘করতালি দিয়া’ ইত্যাদি। এসব সাধুভাষার ক্রিয়াপদ দিয়ে তিনি যেমন সাহিত্যে স্বকীয় শৈলী সৃষ্টি করেছেন, তেমনি বাংলার লোকবুলিকেও তাঁর কাব্যভাষায় ধারণ করেছেন। আবার কাব্যের প্রয়োজনে একই পঙক্তিতে অবলীলায় সাধু ও চলিত ভাষার ক্রিয়াপদকে ঠাঁই দিয়ে ঘোষণা করেছেন : ‘আমি সহসা আমারে চিনেছি, আমার খুলিয়া গিয়াছে সব বাঁধ!’ এ যেনো কলকাতা আর ঢাকার কথ্য বুলিরে একই পঙ্ক্তিতে বসানোর আয়োজন। কবিতার প্রয়োজনে মুখের বুলিকে নিয়েছেন বটে কাব্যিক ক্রিয়াপদ-প্রয়োগের পারঙ্গমতার প্রমাণও রেখেছেন। যেমন : ‘যাই চূর্ণি’, ‘মানি না কো’ ইত্যাদি। আবার ‘নেহারি’ ‘পাশরি’ ইত্যাদি প্রাচীন বাংলার ক্রিয়াপদও প্রয়োগ করেছেন দক্ষতার সাথে। প্রাচীন এই ভাষার আপেক্ষিক সুবিধা অনেক। কথ্য বা গদ্যের ভাষার তুলনায় এর শব্দভাণ্ডার অনেক বড়, অর্থাৎ ‘দেখি’ এই ক্রিয়াপদটির পাশাপাশি ‘হেরি’, ‘নিরখি’, ‘নেহারি’, ‘লখি’ ইত্যাদি ক্রিয়াপদও আছে। এমনি আরেকটি প্রাচীন ক্রিয়াপদ ‘পাশরি’। এটি আবার বৈষ্ণব পদাবলী যুগের ক্রিয়াপদ। ক্রিয়াপদ ছাড়াও বিদ্রোহী কবিতায় বেশ কয়েকটি বৈষ্ণব পদাবলী যুগের পদের প্রয়োগও পাওয়া যায়। যেমন : ‘আমি অর্ফিয়াসের বাঁশরী,/ … মম বাঁশরীর তানে পাশরি’/ আমি শ্যামের হাতের বাঁশরী’। এখানে বাঁশরী, শ্যাম ইত্যাদি বৈষ্ণব পদাবলীর প্রেমের ঐতিহ্য, আবার আর্ফিয়াস গ্রিক বিদ্রোহী চেতনার ঐতিহ্য। ভারতীয় শ্যামের মতো পাশ্চাত্য আর্ফিয়াসের হাতে বাঁশরী দিয়ে কবি চমৎকার সমন্বয় সাজিয়েছেন। পুনশ্চ কাব্যের ‘বাঁশি’ কবিতায় রবীন্দ্রনাথ বলেন : ‘আকবর বাদশার সঙ্গে/ হরিপদ কেরানির কোনো ভেদ নেই/ বাঁশির করুণ ডাক বেয়ে/ ছেঁড়া ছাতা রাজছত্র মিলে চলে গেছে এক বৈকুণ্ঠের দিকে।’ মৃত্যুর সঙ্গে বাঁশির এই যোগ আমাদেরকে অর্ফিয়াসের বাঁশির কথাও মনে করিয়ে দেয়। প্রিয়তমা স্ত্রীর মৃত্যু হলে অর্ফিয়াস পাতালের দেবতাকে খুশি করেছিলেন বাঁশি বাজিয়ে। বাঁশির সুরে মুগ্ধ দেবতা অর্ফিয়াসের স্ত্রীকে মর্ত্যে ফিরিয়ে দেয়ার আবেদন মঞ্জুর করেন। শর্ত ছিল পাতালের দরজা পার হওয়ার আগে পর্যন্ত অর্ফিয়াস পেছন ফিরে তাকাতে পারবে না। কিন্তু পাতালের দরজা পার হওয়ার আগে নিজেকে সামলাতে পারেনি অর্ফিয়াস। ভাবে, পিছে পিছে আসছে তো ইউরিডাইস? মুহূর্তে ঘুরে তাকালে শর্তভঙ্গের অপরাধে অদৃশ্য হয়ে যায় ইউরিডাইস। বুকভাঙা আর্তনাদ নিয়ে ফিরে আসে অর্ফিয়াস। বেদনার এক অদৃশ্য বাঁশির সুর ঘিরে থাকে অর্ফিয়াসকে। এভাবে বাঁশরি ব্যবহার করে নজরুল প্রাচ্যের ঐতিহ্য পদাবলী সাহিত্যের প্রেম আর পাশ্চাত্য বিদ্রোহকে এক সুরে বাঁধেন। তবে তাঁর বাঁশি অতীতের ঐতিহ্যকে ধারণ করে বর্তমানের কথা বলে। এ বাঁশি বাংলার, এ বাঁশি বাঙালির। বাঁশরির সুর শুনিয়ে কবি বাঙালিকে বিদ্রোহী করে তুলতে প্রয়াসী হন। তাই আমাদের অস্বীকার কবার উপায় নেই যে, ‘বিদ্রোহী’ নজরুল, সেই কবি যিনি ছিলেন একই সঙ্গে সামন্তবাদ বিরোধী ও সাম্্রাজ্যবাদ-বিরোধী। সাম্্রাজ্যবাদী শক্তির সুবিধাভোগী বুদ্ধিজীবীগণ তাই নজরুলের স্বরূপ সন্ধানে নানান প্রতিবন্ধকতা তৈরি করতে তৎপর। এ তৎপরতা থেকে মুক্ত থেকে দেশপ্রেমের চেতনায় প্রাণিত হয়ে ‘বিদ্রোহী’ পাঠের মধ্য দিয়ে ‘খেয়ালি বিধির’ বিরুদ্ধে দ্রোহের ‘অগ্নি-পাথার’ পেরোনোর শক্তি সঞ্চয় করতে হবে।
ঔপনিবেশিক শাসনামলের সুবিধাভোগীরা আজও দেশে তৎপর। আজও ধর্মনিরপেক্ষতাকে তাঁরা ধর্মহীনতা বলে অপব্যাখ্যা করে। তুর্কি ‘বাবা’ শব্দ বদলে আরবি ‘আবু’ থেকে জাত উর্দু ‘আব্বা’ আমদানিতে আগ্রহী। আরেক দল প্রগতিশীলতার নামে নাস্তিকতার বীজ বোনে বটে, বিজ্ঞানমনস্কতায় তাদের আগ্রহ নেই তেমন। ফলে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ বেড়েই চলছে। অথচ নজরুল সকল ধর্মের সহাবস্থান চেয়েছেন, বিরোধিতা করেছেন অত্যাচারীর। সমূলে উৎপাটন করতে চেয়েছেন সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতাকে। যে-কারণে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তর্কচ্ছলে ‘বড়র পীরিতি বালির বাঁধ’ শীর্ষক প্রবন্ধের এক জায়গায় লিখলেন, ‘বাঙলা কাব্য-লক্ষ্মীকে দুটো ইরানি ‘জেওর’ পরালে তার জাত যায় না, বরং তাঁকে আরও খুবসুরতই দেখায়।’ সেটি হলো বাংলা ভাষাকে যদি বিদেশি শব্দ দিয়ে ঋদ্ধ করা যায়, তাহলে বিদেশি ভাষায় বাঙালি মুসলমানেরা যে ধর্মপালন করে সেটা যদি মাতৃভাষায় ভাষান্তর করা যায়; তখন সহজেই বাঙালি মুসলমান ধর্মের মূল আলোয় পৌঁছাতে পারবে। নজরুলের এ প্রচেষ্টাটি সমকালীন পণ্ডিতের কাছেও খুব আশাব্যঞ্জক তত্ত্ব বলে মনে হয়। নজরুলের এই তত্ত্বটি বাংলাদেশের সকল ধর্মের মানুষ যদি মেনে চলে, অর্থাৎ দেশে প্রচলিত সকল ধর্ম যদি মাতৃভাষায় চর্চা হয় তাহলে ধর্মীয় উগ্রতা নিমিষেই বিলীন হতো একথা নিশ্চিত বলা যায়। আবার ‘উৎপীড়িতের ক্রন্দনÑরোল’ থামাতে হলেও দেশের আপামর জনতার মুখের ভাষাকে বুঝতে হবে। এই ভাষাকে ভিত্তি করে ভাষানীতি প্রণয়ন করতে হবে। তবেই ‘বাঙালির বাংলা’ বেঁচে থাকবে। চিরজীবী হবে বাংলাদেশ। নজরুলের প্রথম প্রকাশিত কবিতার নাম ‘মুক্তি’, আর প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ অগ্নি-বীণা (১৯২২) গ্রন্থের প্রথম কবিতা ‘প্রলয়োল্লাস’ (১৯২২)Ñএর প্রথম পঙ্ক্তি : ‘তোরা সব জয়ধ্বনি কর!’। ‘জয় বাংলা’ স্লোগান দিয়ে বাঙালি দেশ স্বাধীন করেছে ‘জাতের নামে বজ্জাতি’ করা মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধ করে। নজরুলকে বাংলাদেশের জাতীয় কবি ঘোষণা করা হয়েছে। তাঁর নামে ইনস্টিটিউট-বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে নজরুল চেয়ার স্থাপিত হয়েছে। সদ্য-স্বাধীন দেশে নির্বাক-উন্মাদ নজরুলকে নিয়ে আসা হয়েছে তবে আশানুরূপ চিকিৎসা করে তাঁকে সুস্থ-সবাক করা যায়নি। আবার মৃত্যুর পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদের পাশে তাঁর কবর দেওয়া হলেও তাঁর সকল বংশধর-উত্তরাধিকারীগণকে এদেশে ঠাঁই দেওয়া সম্ভব হয়নি। তাই আমাদের অক্ষমতাকে অস্বীকার না করে বিদ্রোহীর ভাষার আলোকে নজরুলকে চিনতে হবে। বিদ্রোহীর ভাষাকে বাঁচিয়ে রাখতে পারলে এই ভাষার চর্চাকে অব্যাহত গতি দিতে পারলে অবশ্যই আগামীতে বলতে পারবো, নজরুলের কবরের নীরবতা নয়; বিদ্রোহীর ভাষার অসাম্প্রদায়িকতা, উদ্দামতা, উচ্ছলতা আর অফুরন্ত প্রাণবন্ততা নিয়ে প্রদীপ্ত হবে আমাদের মুক্ত-স্বাধীন বাংলাদেশ। (শেষাংশ)