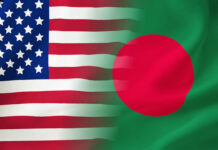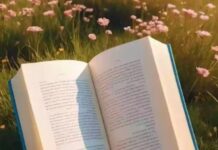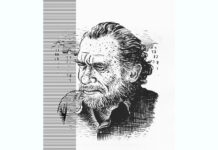দ্বীপ সরকার »
সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম অধুনা সাহিত্যে এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। অন্যতম শিক্ষাবিদ এবং সাহিত্যে আধুনিক ধারার প্রজ্জ্বলিত নায়ক। তাঁর সাহিত্য জীবন যেমন সৃজনশীলতার এক অনন্য দৃষ্টান্ত, তেমনি তাঁর শিক্ষাজীবন ও কর্মজীবনও বাংলাদেশের বুদ্ধিবৃত্তিক জগতে এক উজ্জ্বল অধ্যায়। তাঁর মেধা মনন মিশ্রণে বাস্তবতা ও জাদুবাস্তবতার যে মিলমিশ তৈরি করেছেন তা বাংলা সাহিত্যে দীর্ঘদিন বেঁচে থাকবে। সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম জন্মগ্রহণ করেন ১৯৫১ সালের ১৮ জানুয়ারি, বাংলাদেশের সুনামগঞ্জ জেলায়। তাঁর শৈশব কেটেছে সিলেট অঞ্চলের প্রকৃতি ও সংস্কৃতির আবহে। ছোটবেলা থেকেই তিনি সাহিত্য, ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি গভীর আকর্ষণ অনুভব করতেন এবং চিন্তার ভেতর দিয়ে চষে বেড়াতেন—যেটা তাঁকে পরবর্তীতে সুখ্যাতির দিকে নিয়ে যেতে সহায়ক হয়েছে।
তাঁর লেখার ভঙ্গি, চিন্তাশক্তি ও ভাষা—নির্মাণ তাঁকে সমকালীন লেখকদের থেকে আলাদা করেছে। সাহিত্য, শিক্ষা ও সমাজ নিয়ে তিনি যে ভাবণা প্রকাশ করেন, তা একাধারে গভীর ও মানবিক। তিনি গতানুগতিক ধারাকে ভেঙে নিজস্বতা তৈরি করেছেন। সে কারনে প্রথার বিরুদ্ধে তার কলম চলেছে বেশি। সৈয়দ মনজুরুল ইসলামের শিক্ষাজীবন ছিল অত্যন্ত সমৃদ্ধ ও আন্তর্জাতিক মানের। তিনি সিলেট সরকারি পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ১৯৬৬ খ্রিষ্টাব্দে মাধ্যমিক পাশ করেন। উচ্চ মাধ্যমিক পাস করেন সিলেট এমসি কলেজ থেকে ১৯৬৮ খ্রিষ্টাব্দে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর করেন ১৯৭১ ও ১৯৭২ সালে। ১৯৮১ খ্রিষ্টাব্দে কানাডার কুইন্স বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইয়েটস—এর কবিতায় ইমানুয়েল সুইডেনবার্গের দর্শনের প্রভাব বিষয়ে পিএইচডি করেন।
প্রকৃত শিল্পীরা ছোটবেলা থেকেই প্রকাশিত হোন। তার বিভিন্ন কাজ, বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চা—যা সমাজে এবং সমগোত্রে ছড়িয়ে পড়ে। সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম সেরকম ছোটবেলা থেকেই সাহিত্য ও দর্শনের প্রতি গভীর অনুরাগী ছিলেন। ইংরেজি ও বাংলা, উভয় ভাষায় দখল ছিল। তাঁর লেখায় দেখা যায় পশ্চিমা সাহিত্যরীতি ও বাঙালি সাহিত্য ও সংস্কৃতির এক চমৎকার সমন্বয়। তিনি বিভিন্নভাবে তুলনামুলক সাহিত্যের মেলবন্ধন ও সাদৃশ্য বৈসাদৃশ্য নিয়ে লিখেছেন। বিদেশে পড়াশোনা শেষ করে তিনি ফিরে আসেন বাংলাদেশে এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগে অধ্যাপক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। সেখানে তিনি দীর্ঘদিন ধরে অধ্যাপনা করেছেন এবং পরবর্তীতে বিভাগীয় প্রধান হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। শিক্ষকতা জীবনে তিনি শুধু ক্লাসরুমের শিক্ষক ছিলেন না; বরং তিনি ছিলেন একজন চিন্তাশিক্ষক, একাডেমিক লেখক ও প্রজন্ম—নির্মাতা এবং সর্বোপরি শিক্ষার্থীদের অভিভাবকতূল্য। বিদেশে তাঁর বক্তৃতা, সেমিনার ও রচনাগুলো বিশ্বসাহিত্যেও নানা প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশকে পরিচিত করেছেন। শিক্ষাবিদ হিসেবে তিনি বিশ্বাস করতেন—‘শিক্ষা কেবল তথ্য অর্জন নয়, বরং চিন্তার স্বাধীনতা ও মানবিক মূল্যবোধের বিকাশ’। সৈয়দ মনজুরুল ইসলামের সাহিত্যজীবন শুরু হয় আশির দশকের দিকে। তিনি প্রথমে ছোটগল্পের মাধ্যমে পাঠকসমাজে পরিচিতি লাভ করেন। পরে উপন্যাস, প্রবন্ধ ও অনুবাদ সাহিত্যে নিজের শক্ত অবস্থান তৈরি করেন। কথাসাহিত্যে সব সময় যে সমস্ত রসবোধ পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন তা হলো, জাদুবাস্তবতার ছোঁয়া, সামাজিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতা এবং মানুষের মানসিক জটিলতা। লেখকের উল্লেখযোগ্য গল্পগ্রন্থঃ স্বনির্বাচিত শ্রেষ্ঠ গল্প (১৯৯৪), থাকা না থাকার গল্প (১৯৯৫), কাচ ভাঙ্গা রাতের গল্প (১৯৯৮), অন্ধকার ও আলো দেখার গল্প (২০০১), প্রেম ও প্রার্থনার গল্প (২০০৫)। সুখদুঃখের গল্প, বেলা অবেলার গল্প।
তাঁর গল্পে চরিত্রগুলো প্রায়ই বাস্তবতা ও স্বপ্নের সীমারেখায় অবস্থান করে। এই মিশ্রণই তাঁর গল্পের ভাষা ও বিন্যাসকে করে তুলেছে অনন্য। সৈয়দ মনজুরুল ইসলামের উপন্যাসগুলো সময়, ইতিহাস ও রাজনীতির সঙ্গে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার গভীর সংলাপ তৈরি করে। তার উল্লেখযোগ্য উপন্যাস হলোঃ আধখানা মানুষ্য (২০০৬), দিনরাত্রিগুলি, আজগুবি রাত, তিন পর্বের জীবন, যোগাযোগের গভীর সমস্যা নিয়ে কয়েককজন একা একা লোক, ব্রাত্য রাইসু সহযোগে, কানাগলির মানুষেরা। তাঁর উপন্যাসের ভাষা কাব্যময়, ভাবগম্ভীর ও প্রতীকসমৃদ্ধ। তিনি এক ধরনের ‘ম্যাজিকাল রিয়ালিজম’ প্রয়োগ করেন, যা লাতিন আমেরিকান সাহিত্যরীতি থেকে প্রভাবিত হলেও এর বিষয়বস্তু সম্পূর্ণ দেশজ ও মানবিক।
প্রবন্ধ ও অনুবাদ সাহিত্যে লেখক চমকপ্রদ কাজ করেছে। তিনি বাংলা ও ইংরেজি উভয় ভাষাতেই প্রবন্ধ লিখেছেন। প্রবন্ধগ্রন্থসমূহঃ নন্দনতত্ত্ব (১৯৮৬), কতিপয় প্রবন্ধ (১৯৯২), অলস দিনের হাওয়া,মোহাম্মদ কিবরিয়া, সুবীর চৌধুরীর সহযোগে, রবীন্দ্রানাথের জ্যামিতি ও অন্যান্য শিল্পপ্রসঙ্গ। তাঁর প্রবন্ধে সাহিত্য, রাজনীতি, সমাজ ও সংস্কৃতির নানা দিক উঠে আসে। এছাড়া তিনি বিশ্বসাহিত্যের গুরুত্বপূর্ণ রচনাগুলোর অনুবাদ করে বাংলা পাঠকদের আন্তর্জাতিক সাহিত্যের সঙ্গে সংযোগ ঘটিয়েছেন। সাহিত্যভাবনা ও শৈলীতে সৈয়দ মনজুরুল ইসলামের সাহিত্যচিন্তা ছিলো অনন্য। তার চিন্তার মূল ভিত্তি হলো মানুষ ও তার অভিজ্ঞতার গভীর বিশ্লেষণ। সমাজ ও পারিপার্শ্বিকতার ঘনিষ্ট সম্পর্ক বিশ্লেষন। তিনি বিশ্বাস করেন, সাহিত্য সমাজের প্রতিচ্ছবি হলেও তা কেবল ঘটনাবহুল নয়—এটি মানুষের মনের অজানা জগতের অনুসন্ধান। প্রবন্ধ সাহিত্যের প্রধান বৈশিষ্ট ছিল ভাষার কাব্যময়তা ও ভাবসম্পন্নতা। বাস্তবতার সঙ্গে স্বপ্ন বা কল্পনার সংমিশ্রণ। ইতিহাস ও রাজনীতির প্রেক্ষাপটে ব্যক্তিগত মানসিকতার বিশ্লেষণ এবং সময়, স্মৃতি ও নৈতিকতার প্রশ্নে গভীর মনন। সমাজচিন্তা তার সাহিত্যের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ হয়ে উঠেছিল। তাঁর সাহিত্য শুধু কাহিনি নয়, বরং মানবিকতার পাঠশালা।
সৈয়দ মনজুরুল ইসলামের লেখার মূল বিষয়বস্তু বা কেন্দ্রীয় ধারা কয়েকটি প্রধান দিককে ঘিরে গড়ে উঠেছে।
১.পরিচয় ও অস্তিত্বের অনুসন্ধানঃ তিনি মানুষের অস্তিত্ব সংকট, নিজেকে খুঁজে পাওয়া, এবং পরিচয়ের বিভ্রান্তিকে কেন্দ্র করে বহু গল্প ও উপন্যাস লিখেছেন। উদাহরণ—ভাষা গল্পে লিখেছেন ‘বুড়ি আপা আমার থেকে চার বছরের বড় ছিল’।
২.উত্তর ঔপনিবেশিক বাস্তবতা ও সমাজচিত্রঃ তিনি ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক হিসেবে postcolonial theory–i প্রভাব গভীরভাবে অনুভব করেছেন। তাঁর লেখায় দেখা যায় ঔপনিবেশিক শাসনের উত্তরাধিকার, ভাষার রাজনীতি, ও সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্বের বিশ্লেষণ। তিনি বাংলাদেশি সমাজে আধুনিকতার আগমন ও পশ্চিমা প্রভাবের প্রেক্ষিতে মানুষ ও সংস্কৃতির পরিবর্তন তুলে ধরেছেন।
৩.শহর ও মধ্যবিত্ত জীবনের সংকটঃ তিনি ঢাকাকে তাঁর গল্পের প্রধান প্রেক্ষাপট করেছেন—এ শহরের মধ্যবিত্ত মানুষের স্বপ্ন, হতাশা, নৈতিক দ্বিধা ও বিচ্ছিন্নতা তাঁর লেখার প্রাণ।
৪.স্বপ্ন, কল্পনা ও বাস্তবতার মিশ্রণঃ তার গল্পগুলো প্রায়ইই বাস্তবতা ও ম্যাজিক রিয়ালিজম এর সংমিশ্রণে নির্মিত। তিনি বাস্তব জীবনের কঠিন সত্যের সঙ্গে স্বপ্ন ও প্রতীকের ব্যবহার করে গভীর দার্শনিক অর্থ তৈরি করেছেন। এই ধারা লাতিন আমেরিকান লেখক গার্সিয়া মার্কেস বা বোরহেস এর মতো প্রভাবেরও ইঙ্গিত দেয়।
৫. ইতিহাস, রাজনীতি ও ব্যক্তি জীবনের সংযোগঃ তাঁর অনেক গল্পে মুক্তিযুদ্ধ, রাজনৈতিক দমন—পীড়ন, এবং সামাজিক রূপান্তরের ছাপ আছে। তবে তিনি সরাসরি রাজনৈতিক বক্তব্যের বদলে ব্যক্তিগত জীবনের মধ্য দিয়ে ইতিহাসকে অনুধাবন করেন।
৬. মানবতাবোধ ও নৈতিক দ্বন্ধঃ তিনি বিশ্বাস করতেন, সাহিত্য মানে মানুষের অন্তর্লোকের অনুসন্ধান। তাই তাঁর লেখায় ভালো—মন্দ, পাপ—পুণ্য, দয়া—ক্রোধ,—এসব নৈতিক টানাপোড়েনকে মানবিক দৃষ্টিতে দেখা যায়।
তিনি সমাজে ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা, মুক্তচিন্তা, ধর্মীয় সহনশীলতা ও সংস্কৃতির বৈচিত্র্যের পক্ষে অবস্থান নেন। তাঁর একটি বিখ্যাত বক্তব্য ছিল এমন-‘যে সমাজে কল্পনা নেই, সে সমাজে ন্যায়ও টেকে না’। এই দৃষ্টিভঙ্গিই তাঁর সাহিত্যকে শুধু শিল্প নয়, বরং চিন্তা ও প্রতিবাদের মাধ্যম হিসেবে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে।সাহিত্য ও শিক্ষাক্ষেত্রে অবদানের জন্য তিনি পেয়েছেন বহু সম্মাননা। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য—বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার (১৯৯৬),একুশে পদক (২০২০)। এছাড়াও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সাহিত্য সংস্থা ও একাডেমিক প্রতিষ্ঠান থেকে পেয়েছেন একাধিক সম্মাননা। ব্যক্তিজীবন ও সমাজসেবামূলক ভূমিকাতে তিনি চমৎকার কাজ করেছেন। তিনি বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত। লেখালেখির পাশাপাশি তরুণ প্রজন্মকে সৃজনশীল চিন্তা ও পাঠাভ্যাসে উদ্বুদ্ধ করেন। নতাঁর জীবনের মূলে রয়েছে সততা, নৈতিকতা ও মানবিক বোধ। তিনি বিশ্বাস করেন—‘সাহিত্য মানে কেবল সৌন্দর্য নয়, সাহসও’।
লেখক চলতি বছরের ১০ অক্টোবর,২০২৫ইং চিকিৎসাধিন অবস্থায় মৃত্যুবরন করেন।