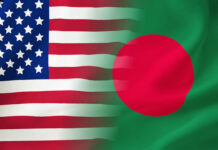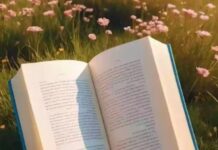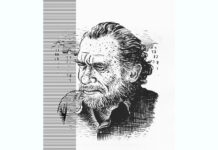বিচিত্র কুমার »
বাংলা আধুনিক কবিতার ইতিহাসে শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের নাম উচ্চারিত হয় এক অন্তর্দগ্ধ সময়ের প্রতিনিধি হিসেবে। তিনি শুধু কবি নন, এক গভীর সময়-সচেতন সত্তা যিনি নিজের জীবন, সমাজ, প্রেম, নিঃসঙ্গতা ও ভাঙনের অভিজ্ঞতাকে কবিতার ভাষায় অনন্য সংবেদনশীলতার সঙ্গে রূপ দিয়েছেন। তাঁর কবিতা যেন এক অন্তর্দেশের রক্তক্ষরণ, যেখানে সময়ের মর্মবেদনা একদিকে ব্যক্তিগত, অন্যদিকে সমষ্টিগত। শক্তি যে সময়ের সন্তান, তা ছিল সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের যুগ। ষাটের দশক থেকে শুরু করে আশির দশক পর্যন্ত তিনি যে সময় অতিক্রম করেছেন, তা বাংলা সমাজে অস্থিরতার, স্বপ্নভঙ্গের, ও মানসিক অনিশ্চয়তার সময়। সেই সময়ের কষ্ট, প্রেম, ক্লান্তি, অস্তিত্বের ভয় এবং জীবনের তীব্র অনিশ্চয়তাকে তিনি কবিতায় পরিণত করেছেন এক অন্তঃসলিলা বেদনায়।
শক্তির কবিতায় সময় কেবল একটি পটভূমি নয়; এটি জীবনের কেন্দ্রে অবস্থান করে। তিনি সময়কে উপলব্ধি করেছেন এক জীবন্ত সত্তা হিসেবে যে সময় মানুষকে ক্ষয় করে, মানুষকে শেখায়, আবার মানুষকে ভেঙে দেয়। তাঁর কবিতায় সময় যেন এক ছায়া, যা অবিরত মানুষের পিছু নেয়। “এই আমি যে রোজ রাতে ঘুমোতে পারি না”- এই স্বীকারোক্তি কেবল একজন নিঃসঙ্গ কবির নয়, বরং এক দগ্ধ সময়ের সন্তান, যার ঘুম হারিয়েছে রাজনৈতিক বিভ্রান্তি, জীবনের অনিশ্চয়তা এবং আত্মবিভাজনের কারণে।
ষাটের দশকের বাংলা সাহিত্য ছিল বিপর্যস্ত সমাজের প্রতিফলন। সেই সময়ে রাষ্ট্রীয় অব্যবস্থা, বেকারত্ব, শহুরে নিঃসঙ্গতা, এবং জীবনের ক্লান্ত বোধ কবিদের মর্মে প্রবেশ করেছিল। শক্তির কবিতায় এই সময়ের বিষন্নতা এক গভীর ব্যক্তিগত বেদনায় রূপ নেয়। তিনি বলেন, “আমি সময়ের কাছে পরাজিত নই, আমি সময়েরই সন্তান।” তাঁর এই স্বীকারোক্তি যেন ঘোষণা করে, সময়ের প্রতিটি আঘাত তাঁর কবিতার খাদ্য হয়ে উঠেছে।
তাঁর বিখ্যাত কবিতা ‘অবশেষে সব ক্ষয় হয়’ এ সময়ের মর্মবেদনা এক ধ্বংসের দর্শনে রূপ নিয়েছে। সেখানে দেখা যায়, জীবনের সমস্ত চেষ্টার পরেও মানুষ সময়ের কাছে নতি স্বীকার করতে বাধ্য। প্রেম, সৌন্দর্য, বিশ্বাস, সবকিছুই একে একে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। কিন্তু সেই ক্ষয়ের মধ্য দিয়েই কবি দেখতে পান পুনর্জন্মের সম্ভাবনা। সময়ের এই দ্বৈত রূপ ধ্বংস ও পুনর্গঠন তাঁর কবিতার মূলে নিহিত।
শক্তির কবিতায় সময় শুধু বহির্বিশ্বের নয়, অন্তর্জগতেরও একটি মানচিত্র। তাঁর কবিতা পাঠ করলে বোঝা যায়, তিনি সময়কে মাপেন না ঘড়ির কাঁটায়, বরং মাপেন হৃদয়ের ধ্বনিতে। তিনি লিখেছেন,
“সময় আমার ভেতরে বসে থাকে,
রোজ একটু একটু করে আমাকে মাপে।”
এই লাইনগুলিতে সময় যেন এক জীবন্ত অস্তিত্ব, যার সঙ্গে কবির প্রতিদিনের সম্পর্ক। এই সময় কখনো নির্মম, কখনো সহানুভূতিশীল, আবার কখনো এক নিঃশব্দ সঙ্গী।
তাঁর কবিতায় সময়ের মর্মবেদনা অনেকাংশে জড়িয়ে আছে জীবনের অস্থায়িত্ববোধের সঙ্গে। তিনি বুঝেছিলেন মানুষের জীবন, প্রেম, সম্পর্ক, সবই ক্ষণস্থায়ী। তবুও এই ক্ষণস্থায়িত্বের মধ্যেই তিনি খুঁজে পেয়েছেন এক চিরন্তন সৌন্দর্য। শক্তির ভাষায়, “সব শেষ হয়ে যায়, তবুও বেঁচে থাকার একটা অনিবার্যতা আছে।” এই বোধ সময়ের প্রতি এক গভীর দর্শন। কারণ, সময় যা নিয়ে যায়, সে-ই আবার নতুন করে জন্ম দেয় জীবনের প্রেরণা।
বাস্তব জীবনের চিত্রে এই সময়ের মর্মবেদনা আরও গভীরভাবে প্রতিফলিত। শক্তি নিজে ছিলেন মধ্যবিত্ত জীবনের সন্তান। তাঁর জীবনে দারিদ্র্য, অনিশ্চয়তা, বেকারত্ব ছিল নিত্যসঙ্গী। যে সময় তিনি কবিতা লিখেছেন, তখন সমাজে যুবকদের মধ্যে এক প্রচণ্ড বিভ্রান্তি কাজ করছিল রাজনীতি ও স্বপ্নের সংঘাতে তারা ভেঙে পড়ছিল। সেই সমাজের প্রতিটি ক্ষত তিনি নিজের কবিতায় অনুভব করেছেন। তাঁর “চুম্বন” কিংবা “চেয়ে আছি” কবিতাগুলোয় দেখা যায় প্রেমের মধ্যেও সময়ের নিষ্ঠুরতার ছায়া। প্রেমিক-প্রেমিকা মিলিত হয়, তবুও তাদের মধ্যে থাকে সময়ের দূরত্ব যা কোনো শক্তিই পেরিয়ে যেতে পারে না।
শক্তির কবিতায় সময়ের সঙ্গে লড়াইটি যেন মানুষ ও নিয়তির লড়াই। সময়কে তিনি এক অদৃশ্য শক্তি হিসেবে দেখেছেন, যা মানুষকে নত করে দেয়। তাঁর এক কবিতায় তিনি লিখেছেন, “সময়কে আমি পেরিয়ে যেতে চেয়েছিলাম, কিন্তু সময় আমাকেই পেরিয়ে গেল।” এই এক বাক্যেই তাঁর কবিতাজীবনের সারসংক্ষেপ নিহিত। এখানে আছে পরাজয়ের বেদনা, আবার আছে এক দার্শনিক গ্রহণও।
তাঁর সময়-চেতনা শুধু ব্যক্তিগত নয়, জাতিগতও। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, ভারতের রাজনৈতিক বিপর্যয়, সমাজে নৈতিক অবক্ষয় সবকিছুই তাঁর কবিতায় প্রতিফলিত হয়েছে সময়ের মর্মবেদনাময় রূপে। তিনি দেখেছেন, মানুষ তার নিজস্ব মানবিকতা হারাচ্ছে, সময় তাকে যন্ত্রে পরিণত করছে। এই অমানবিক সময়ের বিরুদ্ধে তিনি লিখেছেন প্রতিবাদের কবিতা, তবু তাঁর প্রতিবাদ কখনো কোলাহলপূর্ণ নয়, বরং গভীর আত্মদহনময়।
শক্তির কবিতার ভাষা, ছন্দ, ও চিত্রকল্প সবই সময়ের এই বেদনার সঙ্গে সম্পর্কিত। তাঁর শব্দচয়ন কখনো রুক্ষ, কখনো কোমল। তিনি জানতেন, সময়ের মর্মবেদনা প্রকাশ করতে হলে ভাষাকেও সেই যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে যেতে হবে। তাঁর কবিতায় সময় যেন এক শিরায় প্রবাহিত রক্ত—যা থেমে নেই, চলমান, এবং ধীরে ধীরে কবিকে নিঃশেষ করে দিচ্ছে।
বাস্তব জীবনের সঙ্গে তাঁর কবিতার সম্পর্ক এখানেই গভীর। যে সমাজে তিনি বেঁচে ছিলেন, সেখানে সময় মানে ছিল অস্থিরতা মানুষের জীবনে স্থিরতা বা নিশ্চয়তা ছিল না। একদিকে অর্থনৈতিক সংগ্রাম, অন্যদিকে প্রেমে অবিশ্বাস, জীবনের প্রতি অনিশ্চয়তা এইসব মিলিয়ে তাঁর সময় ছিল ক্লান্তির সময়। সেই ক্লান্তি তাঁর কবিতায় রূপ পেয়েছে এক অন্তর্লোকের বিষণ্ণতায়।
কবিতায় শক্তি বারবার ফিরে গেছেন ‘সময়’ ও ‘অপেক্ষা’—এই দুই মূল প্রতীকে। তাঁর কবিতায় অপেক্ষা মানে সময়ের সঙ্গে মানুষের এক নিরব সংলাপ। যেমন তিনি লিখেছেন,
“অপেক্ষা করেছি, কেউ আসেনি,
তবুও জানালা খুলে রেখেছি।”
এই অপেক্ষার ভেতরেই লুকিয়ে আছে সময়ের গভীর মর্মবেদনা। এখানে সময় থেমে নেই, কিন্তু মানুষ এক অনন্ত অপেক্ষায় স্থবির। এই স্থবিরতা আসলে জীবনের অগ্রগতি রোধ করে না, বরং মানবমনের এক শূন্যতাকে উন্মোচন করে।
শক্তির কবিতায় সময়ের মর্মবেদনা আরও এক দিক থেকে প্রকাশ পায় তা হলো স্মৃতির ভেতর দিয়ে। সময় অতীতকে দূরে সরিয়ে দেয়, কিন্তু কবি অতীতকে ছাড়তে পারেন না। তাঁর কবিতায় বারবার ফিরে আসে হারিয়ে যাওয়া প্রেম, মৃত বন্ধুর স্মৃতি, কিংবা এক নিঃসঙ্গ শৈশব। সময় সবকিছু নিয়ে গেছে, কিন্তু সেই হারানো সময়ই তাঁর কবিতার প্রাণ। এইভাবে সময়ের মর্মবেদনা হয়ে ওঠে স্মৃতির কবিতা।
এক অর্থে শক্তির সমস্ত কবিতা একটিই দীর্ঘ সময়চিত্র যেখানে মানুষ ধীরে ধীরে এক ভাঙা সমাজের মধ্য দিয়ে নিজের অস্তিত্ব খুঁজে বেড়াচ্ছে। তিনি সেই অস্তিত্ব খোঁজার যন্ত্রণা লিখেছেন শব্দে, যা আজও পাঠকের মনে অনুরণন তোলে। তাঁর কবিতা আমাদের শেখায়, সময়ের মর্মবেদনা মানে কেবল হারানো নয়; এটি বেঁচে থাকার এক অনিবার্য শিক্ষা।
আজকের বাস্তব সমাজেও তাঁর কবিতার এই সময়চেতনা প্রাসঙ্গিক। মানুষ এখনো সময়ের হাতে বন্দি প্রযুক্তি, অর্থ, রাজনীতি সবই তাকে ঘিরে ফেলেছে। এই আধুনিক সময়েও শক্তির কবিতা আমাদের মনে করিয়ে দেয়, মানুষ তার সময়েরই প্রতিচ্ছবি, এবং সময়ের মর্মবেদনা থেকেই জন্ম নেয় প্রকৃত শিল্প।
সবশেষে বলা যায় শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা সময়ের ব্যথার ভাষা। তাঁর কলমে সময় কাঁদে, সময় হাসে, সময় ভালোবাসে, আবার সময় ধ্বংসও করে। তিনি দেখিয়েছেন, সময় আমাদের চারপাশের বস্তু নয়, বরং আমাদের ভেতরের অনুভব। আর সেই অনুভবের মর্মবেদনাই শক্তির কবিতার মূল সুর। তাঁর কবিতা তাই কখনো নিছক সাহিত্য নয়; এটি এক জীবন্ত সময়ের দলিল, যেখানে মানুষ, প্রেম, ক্ষয় ও পুনর্জন্ম সব একাকার হয়ে যায়।
শক্তি চট্টোপাধ্যায় ছিলেন সময়ের দার্শনিক। তিনি বুঝেছিলেন সময়কে থামানো যায় না, কিন্তু সময়কে অনুভব করা যায়। তাঁর কবিতা সেই অনুভবেরই উন্মোচন, যেখানে মর্মবেদনা পরিণত হয় এক গভীর মানবিক সঙ্গীতে। এই সঙ্গীত আজও প্রতিধ্বনিত হয় প্রতিটি সংবেদনশীল পাঠকের হৃদয়ে একই প্রশ্ন রেখে, “সময় কাকে বলে?” এবং তার উত্তর খুঁজতে গিয়ে আমরা আবিষ্কার করি শক্তি চট্টোপাধ্যায়কেই সময় ও মর্মবেদনার কবি।