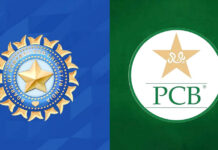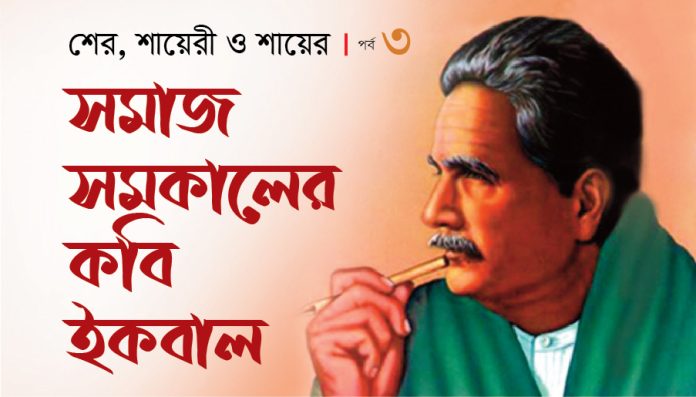ভাষা মানে একেক জাতি। যেমন, বাংলার সাথে বাঙালি, ফরাসির সাথে ফরাসি জাতি, জার্মানদের সাথে জার্মান জাতি। কিন্তু উর্দু এমন একটি ভাষা যার সাথে নির্দিষ্ট কোন জাতির সম্পর্ক নেই।
ঔপনিবেশিক ইতিহাসের চক্করে সুকৌশলে একই ভাষাকে হিন্দু ও মুসলমান বিভাজনে কাজে লাগানো হয়। একদিকে আরবি লিপির উর্দু আর অন্য দিকে নাগরি লিপির হিন্দি। অথচ দুটো ভাষাই এক। মুসলিমদের বিপরীতে হিন্দুদের জন্য একটা নিজস্ব ভাষা তৈরির অভিপ্রায়ে বহাল ভাষা হতে আরবি ফারসি বাদ দিয়ে সংস্কৃত ঢোকানোর কাজটা ইংরেজরা করিয়েছিল হিন্দু পণ্ডিতদের দিয়ে। এখানে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য স্পষ্ট। এই বিভাজনের সুদূরপ্রসারী ফল ছিল ভারতভাগ।
উপমহাদেশের নবীনতম ভাষা আর সাহিত্য উর্দু। একটা দীর্ঘ সময় উপমহাদেশের বহু ভাষা আর সংস্কৃতির মাঝে ভাব বিনিময়ের মাধ্যম হয়ে টিকে ছিল উর্দু। ইংরেজরা আসার পর উপনিবেশ কালের রাজনীতিতে এই ভাষাই হয়ে ওঠে সম্প্রদায় বিভাজনের রাজনীতির হাতিয়ার।
কবি মুহাম্মদ ইকবাল, আল্লামা ইকবাল হিসেবেই বেশি পরিচিত। আল্লামা শব্দের অর্থ হচ্ছে শিক্ষাবিদ।
১৯০৪ সালে ইকবালের লেখা বিখ্যাত দেশাত্মবোধক গানের প্রথম দু’কলি—
সারে জাঁহা সে আচ্ছা হিন্দোস্তাঁ হামারা
হাম বুলবুলে হায় ইস কি ইয়ে গুলিস্তাঁ হামারা
সারা জগত থেকে ভালো আমাদের হিন্দুস্তান
আমরা তার গানের পাখি, সে আমাদের ফুলবাগিচা
কবি ও গীতিকার হিসেবে আল্লামা ইকবালকে এই গান তুমুল জনপ্রিয়তা দেয়- আজকের ভারতেও গানটি ভীষণভাবে সমাদৃত।
শুরুতে না হলেও পরে কবি ইকবাল দ্বিজাতি তত্ত্বের একজন প্রবল সমর্থক হয়ে ওঠেন, ভারত ভাগ করে আলাদা পাকিস্তান তৈরির পক্ষেও জোরালো দাবী জানাতে শুরু করেন।
সাতচল্লিশে পাকিস্তান সৃষ্টির বছরদশেক আগেই লাহোরে তিনি মৃত্যুবরণ করেন, পরে তিনি স্বাধীন পাকিস্তানের জাতীয় কবিরও সম্মান পেয়েছিলেন।
উর্দু পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা, যদিও পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার দশ শতাংশের কম উর্দুভাষী। পাকিস্তানের চেয়ে ভারতে উর্দু ভাষাভাষীর সংখ্যা পাঁচ গুণেরও বেশি। যাঁরা পাকিস্তানে উর্দু ভাষায় কথা বলেন তাঁদের মধ্যেও অধিকাংশই মোহাজির বা উদ্বাস্তু যারা দেশভাগের পর ভারত থেকে গেছেন।
উর্দু শুধু মুসলমানের ভাষা না। এই ভাষাতে সাহিত্য রচনা করেছেন এমন অমুসলমানের সংখ্যাও অজস্র। উর্দু ভাষায় ছোটগল্পের সূচনা প্রেমচন্দের (১৮৮০-১৯৩৬) হাতে, যিনি উর্দু ও হিন্দি দুই ভাষাতেই সমান দক্ষ ছিলেন। প্রথম উর্দু সংবাদপত্র বের করার কৃতিত্ব হরিহর দত্ত নামে একজন বাঙালির।
মীর তকি মীর, মির্জা গালিব ও আল্লামা ইকবাল – এই তিনজন তিন আলাদা আলাদা শতাব্দীর কবি। শৈলী আর ভাবের বিচারে মীর এমন এক কাব্যস্রোত যেখানে সকল নদীর স্রোত এসে মিশেছে। মির্জা গালিবের কবিতার রং মীরের কবিতারই ফসিল। গালিবের কবিতার হাত ধরেই আধুনিক উর্দু কবিতার জন্ম। আর সমাজ সমকালের কবি হিসেবে ইকবালের কবিতায় যে গাম্ভীর্য আর চিন্তার দার্শনিকতা, মীরের কবিতায় এর আঁচ পাওয়া যায় প্রথম।
উর্দু সাহিত্যে গালিবের পরেই স্থান ইকবালের (১৮৭৭-১৯৩৮)। ইকবাল ছিলেন চিন্তাশীল ও সমাজ সচেতন কবি। তাই গজলের সীমাবদ্ধ পরিসর ছেড়ে নজম (কবিতা) লেখা বেশি পছন্দ করতেন। তাঁর কবিতা নজরুলের কবিতার মতোই গতিময়। ইকবালের রচনা বহুমাত্রিক। তাতে যেমন দেশপ্রেমের কথা আছে, তেমনই আছে মুসলিম বিশ্বভ্রাতৃত্বের বাণী, আবার শ্রীরামের প্রশংসাও। ইকবাল উর্দু সাহিত্যের এক বিশাল স্তম্ভ। তাঁর আগমনে উর্দু সাহিত্যে নবযুগের সূচনা হয়।
মুহাম্মদ ইকবাল
জন্ম: ৯ নভেম্বর, ১৮৭৭ শিয়ালকোট
মৃত্যু: ২১ এপ্রিল, ১৯৩৮ লাহোর
ব্রিটিশ ভারতের পাঞ্জাব প্রদেশে (বর্তমানে পাকিস্তান) জাতিগতভাবে কাশ্মীরি একটি পরিবারে ইকবাল জন্মগ্রহণ করেন। তাঁদের আদি পরিবার মূলত কাশ্মীরি ব্রাহ্মণ এবং সাপ্রু সম্প্রদায়ের মানুষ। পরবর্তীকালে তাঁর দাদার পরিবার ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। উনিশ শতকে শিখ সাম্রাজ্য যখন কাশ্মীর জয় করে, তখন তাঁর দাদার পরিবার শিয়ালকেটে গিয়ে বসবাস শুরু করেন।
ইকবালের দাদা শেখ রফিক কাশ্মীরি শাল তৈরি ও ব্যবসার সঙ্গে জড়িত ছিলেন। তাঁর দাদার দুই পুত্র— শেখ গোলাম কাদির এবং শেখ নূর মুহাম্মদ। ইকবালের বাবা ছিলেন দর্জি, কোন আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ছিল না। তবে তিনি ছিলেন নিবেদিত প্রাণ মুসলমান এবং সুফি সঙ্গীতের অনুরক্ত। ইকবালের মা ইমাম বিবিও ছিলেন অত্যন্ত ধার্মিক মহিলা।
১৮৯৫ সালে ইকবাল লাহোর সরকারি কলেজে ভর্তি হন। দর্শন, ইংরেজি ও আরবি সাহিত্য নিয়ে পড়াশোনা করেন। এখান থেকেই তিনি বিএ ও এমএ ডিগ্রি লাভ করেন।
মাস্টার্স ডিগ্রিতে পড়বার সময় ইকবাল স্যার টমাস আর্নল্ডের সংস্পর্শে আসেন। তিনি ছিলেন ইকবালের কাছে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সেতুবন্ধন। স্যার টমাস আর্নল্ড তাঁকে ইংল্যান্ডে যেতে উৎসাহ দেন। ইকবাল ক্যামব্রিজে আইন আর নিও-হেগেলীয় দর্শন অধ্যয়ন করেন। মিউনিখ থেকে তিনি দর্শনে ডক্টরেট করেন। লিঙ্কনস ইন থেকে ব্যারিস্টার হিসেবে সনদ লাভ করেন।
ইকবাল তিন মাসে জার্মান ভাষা আয়ত্ব করেছিলেন। ইউরোপে অধ্যয়নকালে ইকবাল ফারসি ভাষায় কবিতা লিখতে শুরু করেন। ইকবাল তাঁর বন্ধু স্বামী রাম তীর্থকে মসনভি শেখাতেন, যার বিনিময়ে রাম তাকে সংস্কৃত শেখাতেন।
ইকবালের প্রথম কাব্যগ্রন্থ ‘আসরার-ই-খুদি’ ১৯১৫ সালে প্রকাশিত হয়। ১৯২২ সালে ‘আসরার-ই-খুদি’ কাব্যগ্রন্থের জন্য ব্রিটিশ সরকার মুহাম্মদ ইকবালকে ‘নাইট’ উপাধি দেয়।
হেগেল হতে নিৎশ, পূর্ণ মানুষের খোঁজে ইকবাল। এই পথে তাঁর পথপ্রদর্শক মাওলানা রুমি। ১৯১৭ সালে সংঘটিত রুশ বিপ্লব ইকবালের কাছে গুরুত্ববহ ছিল। সাম্রাজ্যবাদ আর শোষণ হতে মুক্তির এই ঘটনা তাঁকে আন্দেলিত করে।
পরবর্তী কালে ইকবালের লেখনিতে যে ইসলামী পুনর্জাগরণের আওয়াজ উঠেছিল তা সমসাময়িক অনেক ব্যক্তি ও আন্দোলনকে বহুলভাবে প্রভাবিত করেছে। বিশেষ করে ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলমানদের রাজনৈতিক ও আধ্যাত্মিক পুনরুজ্জীবনের তিনি ছিলেন একজন প্রবল সমর্থক, ইকবাল এই বিষয়ে যে বক্তৃতাসমূহ দিয়েছিলেন তার সিরিজটি ১৯৩০ সালে ‘ইসলামে ধর্মীয় চিন্তার পুনর্গঠন’ নামে প্রকাশিত হয়।
আসরার-ই-খুদি, শিকওয়া ও জবাবে শিকওয়া, দ্যা রিকনস্ট্রাকশন অফ রিলিজিয়াস থট ইন ইসলাম, জাভেদ নামা ইত্যাদি ইকবালের অত্যন্ত গভীর দার্শনিক ভাবসমৃদ্ধ রচনা।
আতিয়া ফয়েজি নামে ইকবালের একজন প্রেমিকা ছিলেন। আধুনিক ও শিক্ষিতা, দুজনের আলাপ বিদেশে। দেশে ফিরে ইকবাল তাঁর স্ত্রীর থেকে আলাদা বাস করতে শুরু করেন কিন্তু পরিবারের সম্মতি না পাওয়ায় আতিয়াকে বিয়ে করেননি। আতিয়া পরবর্তীতে তাদের চিঠিপত্র প্রকাশ করে। বিদেশে যাবার আগেই তাঁর বিয়ে হয়ে গিয়েছিল। পরে অবশ্য প্রথম স্ত্রীকে ছেড়ে আরও দু’বার বিয়ে করেন।
কর্মজীবনে কিছুকাল অধ্যাপনা এবং পরে আইনব্যবসা ও রাজনীতিতে যুক্ত ছিলেন আল্লামা ইকবাল। জীবনের শেষ বছরগুলিতে তিনি নিয়মিতভাবে লাহোরে বিখ্যাত সুফি আলী হুজভিরির দরগায় যেতেন। কয়েক মাস অসুস্থ থাকার পর, ইকবাল ২১ এপ্রিল ১৯৩৮ সালে লাহোরে মারা যান।
ঢুন্ডতা ফিরতা হুঁ ম্যায় ইকবাল আপনে আপকো
আপ হি গোয়া মুসাফির আপ হি মনযিল হুঁ ম্যায়
[ ঢুন্ডতা— খোঁজা; মুসাফির—পথিক; মনযিল—গন্তব্য ]
নিজেই নিজেকে খুঁজে ফিরি আমি ‘ইকবাল’
যেন নিজেই পথিক, আবার নিজেই নিজের গন্তব্য আমি
মুদ্দায়ি লাখ্ বুরা চাহে তো কেয়া হোতা হ্যায়
ওহি হোতা হ্যায় জো মঞ্জুরে খুদা হোতা হ্যায়
[ মুদ্দায়ি—প্রতিপক্ষ; বুরা—খারাপ; ওহি—তা-ই; মঞ্জুর—ইচ্ছা,অনুমতি ]
প্রতিপক্ষ যতই খারাপ চায় তো কি হবে
খোদার যা মঞ্জুর তা-ই হবে
কিউঁ খালিক ও মখলুক মেঁ হায়িল রহেঁ পর্দে
পিরানে কলিসা কো কলিসা সে উঠা দো
[ খালিক— স্রষ্টা; মখলুক—সৃষ্টি; হায়িল—বাধা;
পিরানে কলিসা— ধর্মগৃহের পুরোহিত ]
স্রষ্টা আর সৃষ্টির মধ্যে পর্দা থাকবে কেন!
ধর্মগৃহের যত পুরোহিত তাড়িয়ে দাও
ম্যায় নাখুশ ও বেযার হুঁ মরমর কি সিলোঁ সে
মেরে লিয়ে মিট্টি কা হারম অওর বানা দো
[ নাখুশ—অখুশি; বেযার—নারাজ; সিলোঁ—পাথর;
মিট্টি—মাটি; হারম—প্রার্থনাঘর ]
মর্মর পাথরের ফলকে আমি নারাজ, অখুশি
আমার জন্য মাটির কোন প্রার্থনাঘর বানিয়ে দাও
আচ্ছা হ্যায় দিল কা সাথ রহে পাসবানে আকল
লেকিন কাভি কাভি উসে তনহা ভি ছোড়িয়ে
[ পাসবানে—পাহারাদার; আকল—বুদ্ধি; তানহা— একা ]
হৃদয়ের সঙ্গে বুদ্ধির পাহারাদার থাকা ভালো
তবে কখনো কখনো তাকে একাও ছেড়ে দিও
হ্যায় দিল কে লিয়ে মওত মাশিনোঁ কি হুকুমত
এহসাসে মুহাব্বাত কো কুচাল দেতে হ্যাঁয় আলাত
[ মাশিনোঁ—যন্ত্র; হুকুমত—শাসন; এহসাস—অনুভূতি;
কুচাল—বিশৃঙ্খল বা নোংরা; আলাত—ভুল
যন্ত্রের শাসন হৃদয়ের মৃত্যু ডেকে আনে
মানুষের কোমল অনুভূতির সেখানে সমাধি
ইলমে ভি সুরূর হ্যায় লেকিন
ইয়ে ও জান্নাত হ্যায় জিস মেঁ হুর নেহি
[ ইলম— বিদ্যা, সুরূর—গভীর আনন্দ ]
বিদ্যায়ও আছে গভীর আনন্দ, কিন্তু
এ সেই বেহেশত যেখানে হুর নেই
তেরি আযাদ বন্দোঁ কি ন ইয়ে দুনিয়া ন ও দুনিয়া
ইয়াহাঁ মরনে কি পাবন্দি ওয়াহাঁ জিনে কা পাবন্দি
[ আযাদ—স্বাধীন; পাবন্দি—বাধ্যবাধকতা ]
তোমার মতো স্বাধীন বান্দার না এই দুনিয়া না ওই দুনিয়া
এখানে মরবার বাধ্যতা ওখানে বেঁচে থাকার বাধ্যতা
ওয়াতান কি ফিকর কর নাদান মুসিবত আনে ওয়ালি হ্যায়
তেরি বরবাদিয়োঁ কে মাশওয়ারা হ্যাঁয় আসমানোঁ মে
[ মুসিবত—দৃর্যোগ/বিপদ; মাশওয়ারা—আলোচনা/পরামর্শ ]
দেশের চিন্তা কর নাদান, দুর্যোগ আসছে
তোমার সর্বনাশের আলোচনা আকাশে আকাশে
ভরি বযমে মেঁ রায কি বাত কেহ্ দি
বড়া বে-আদব হুঁ সযা চাহতা হুঁ
[ ভরি—ভরা; বযমে—আসরে; রায—গোপন; সযা—শাস্তি ]
ভরা আসরে গোপন কথা বলে দিয়েছি
বড় বেয়াদব আমি, শাস্তি প্রার্থনা করছি
আকল্ আয়্যার হ্যায় সৌ ভেশ বদল লেতি হ্যায়
ইশক বেচারা ন যাহিদ হ্যায় ন মুল্লা ন হকিম
[ আকল—বুদ্ধি; আয়্যার—চতুর; সৌ—শত;
যাহিদ—তপস্বী; হকিম—হেকিম ]
বুদ্ধি চতুর, শত বেশ বদলে ফেলে
প্রেম বেচারা না তপস্বী না মোল্লা না হেকিম
চয়ন ও উপস্থাপন • রুশো মাহমুদ