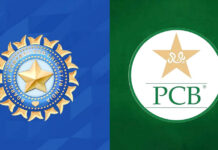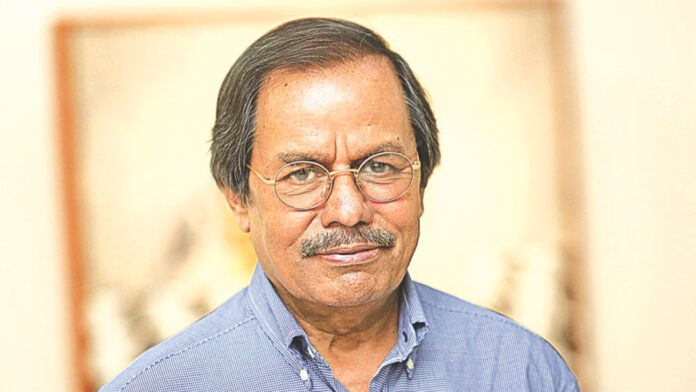ইলিয়াস বাবর »
সাহিত্যের মননশীল মাধ্যম প্রবন্ধ নিয়ে নানা আলাপ চলে। আলাপের নানা হেতুও আছে। বর্তমানে কিংবা নিকট অতীতে সাহিত্যের অপরাপর মাধ্যমগুলোয় বলার মতো উল্লেখযোগ্য নাম আমাদের সমুখে ভেসে বেড়ালেও প্রবন্ধ শাখায় এখনো ভরসা দূর-অতীত কিংবা অতীতের ঋদ্ধ আলোয় প্রবীণ কয়েকটি নাম। পরম্পরা রক্ষার বিষয়টি হয়তো অনেকানেক কাজে লক্ষ করার মতো ব্যাপার কিন্তু সাহিত্যে প্রবন্ধচর্চায় যে হিম্মত কি জানাশোনা দরকার তা অনেকেরই নেই সেটা স্বীকার করেও বলতে হয়, প্রবন্ধ শাখা বরাবরেই একটা মার্গ রক্ষা করে চলে। আলোচনার মতো অনেক জিনিসকে প্রবন্ধ বিবেচনায় আমরা হয়তো গণ্য করি, সেই দোষ উহ্য রেখে আমাদের পাঠ করা উচিত ‘আমাদের সাহিত্যে মুক্তিযুদ্ধ ও অন্যান্য প্রবন্ধ’গ্রন্থটি। এই গ্রন্থে প্রথাগত প্রবন্ধের চেয়ে বিষয়গত, প্রকরণগত ভিন্নতার দিকে হেঁটেছেন প্রবন্ধকার। বিষয়ের আলোকে গ্রন্থস্থিত প্রবন্ধগুলোকে কয়েকটা ধাপে রাখা যায় আলোচনার সুবিধাহেতু। ‘কবিতা কী ও কেন”, ‘মাইকেল মধুসূদন ও আধুনিকতা”, ‘নজরুল ইসলামের বৈশ্বিক চিন্তা’, ‘হুমায়ুন আহমেদের ছোটগল্প’, ‘আমাদের সাহিত্যে মুক্তিযুদ্ধ’ এসব প্রবন্ধে সৈয়দ মঞ্জরুল ইসলামের সাহিত্যভাবনার বিস্ময়কর বিভূতির পরিচয় পাওয়া যায়। কবিতার নানা সংজ্ঞা, নানা মতকে সঙ্গে নিয়ে নানা উদ্ধৃতিসহ এগিয়ে যায় ‘কবিতা কী ও কেন’ প্রবন্ধটি। উল্লেখ করার বিষয়, সৈয়দ মঞ্জুরুল ইসলাম যে বিষয় নিয়েই লেখেন, তার আদিঅন্ত পাঠককে জানাতে ভালোবাসেন, ইতিহাসের সাথে তার সম্পর্ক, বর্তমানের সাথে তার ঘরকন্যা ইত্যাদি জানাতে গিয়ে মূলত পাঠক ঐ প্রেক্ষিতের দৈশিক তো বটেই, বৈশ্বিক একটা ধারণাও পেয়ে যান উপরি হিসেবে। আর আছে চমৎকার কমিউনিকেটিভ ভাষা। কবিতার নানা বিষয়াশয়, লক্ষণ ও শ্রেণিভেদ নিয়ে প্রাগুক্ত প্রবন্ধটির সম্ভবত লেখককৃত কবিতা নিয়ে শ্রেষ্ঠ মন্তব্য এই, ‘শ্রেষ্ঠ কবিতার লক্ষণ হলো, সেখানে কবির সচেতন প্রয়াসলব্ধ আবেগ অনুভূতিগুলো একটি সহজ ও অ-সচেতন রূপ লাভ করে, মনে হবে যেন কবির চেতনার দূরপ্রান্তে কোন জ্যোতির্ময় লোক থেকে তার উৎসার। তেমন কবিতা কবির ও তার সমাজের অভিজ্ঞতার আলোকে উদ্ভাসিত হবে, সমাজ ও কালের সত্যসমূহ ধারণ করবে…’ কবিতা নিয়ে এরচে মোক্ষম কথা আর হতে পারে না। মাইকেল মধুসূদন দত্ত ও কাজী নজরুল ইসলামের সময়, তাদের চিন্তাবিশ্বের স্বরূপ, কবিতায় তাদের ধরণ-ধারণ ইত্যাদি নিয়েই ‘মাইকেল মধুসূদন ও আধুনিকতা’ এবং ‘নজরুল ইসলামের বৈশ্বিক চিন্তা’। প্রবন্ধ দুটোতে বাংলাসাহিত্যের দুই মহিরূহ নিয়ে ভিন্নমাত্রিক আলাপ আছে, বক্তব্য আছে, আছে বিশ্লেষণের গভীরতা। ‘হুমায়ুন আহমেদের ছোটগল্প’ প্রবন্ধটি নানা কারণেই গুরুত্ববাহী। গত কয়েক দশকে হুমায়ুন আহমেদই ছিল আমাদের শ্রেষ্ঠ পাঠকপ্রিয় লেখক। তার ছোটগল্প নিয়ে নানা বিশ্লেষণের ভেতর দিয়ে এগিয়ে যাওয়া প্রবন্ধটির সারকথা হিসেবে একেবারে শেষ প্যারাটাই আমরা সৈয়দ মঞ্জুরুল ইসলামের সুরে পড়ে দেখতে পারি, ‘হুমায়ূন আহমেদের ছোটগল্পের দিকে আমাদের দৃষ্টি ফেরাতে হবে, তাঁর উপন্যাসের ভিড়ে যেন ছোটগল্পগুলো হারিয়ে না যায়। এসব গল্প বাংলা সাহিত্যের সম্পদ—এগুলোর তুল্য তেমন বেশি গল্প লেখা হয়নি আমাদের সময়ে। তাঁর ছোটগল্পের ওপর গবেষকদেরও অনুসন্ধানী দৃষ্টি পড়া উচিত, যাতে তার উৎকর্ষের রসায়নটি চিহ্নিত করা যায়, তাঁর গল্পপ্রতিভাকে উদযাপন করা যায়।’ ‘আমাদেরসাহিত্যে মুক্তিযুদ্ধ’ প্রবন্ধটিতে কোন দেশের সাহিত্যে মুক্তিযুদ্ধের প্রভাব, প্রেক্ষিত ইত্যাদি নিয়ে বিস্তৃত সুখপাঠ্য আলোচনা করে প্রবন্ধকার। মুক্তিযুদ্ধ যেকোন সমাজে, যেকোন দেশে প্রভাব ফেলে সবরকম কার্যক্রমে। সাহিত্যে মুক্তিযুদ্ধের প্রভাব সর্বাধিক, হোক তা প্রত্যক্ষভাবে কিংবা পরোক্ষভাবে। অভূতপূর্ব এই ঘটনা বাংলাসাহিত্যে অপূর্ব রচনায় যেমন সহযোগিতা করেছে, তেমনি লেখকের মানসপঠে, প্রজন্মের সৃজনশীলতায় এমন নির্ণায়ক হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, এর ফলে নিশ্চয়ই অসাধারণ লেখায় ভাস্বর হবে আমাদের ভাবিকাল। সৈয়দ মঞ্জুরুল ইসলাম আশাবাদ ব্যক্ত করেন, ‘নতুন উপায়ে’ সাহিত্যে মুক্তিযুদ্ধের প্রভাব আমরা প্রত্যক্ষ করবো সাহিত্যের বুকে।
‘বাঙালিয়ানার পুনর্জন্ম’, ‘বাঙালি সমাজ’, ‘বাঙালি’ প্রবন্ধগুলোয় প্রবন্ধকারের বাঙালিমানস, বাঙালি জাতিসত্ত্বা, বাঙালির পরিবর্তনমান সমাজ ও মননের স্বরূপ উন্মোচনের প্রয়াস লক্ষ করার মতোন। নানাজনের শাসন, অপশাসন আর বিবর্তনের ভেতর দিয়ে বাঙালিকে বাঙালিত্বের পরীক্ষায় বারবার মুখোমুখি হতে হয়েছে। এর ভেতর দিয়েই কার্যত বাঙালির পুনর্জন্ম হয়েছে। প্রবন্ধকারের ভাষায়, ‘… সময় প্রতিকূল হলে বাঙালিয়ানার একটা বলিষ্ঠ প্রকাশ ঘটে। বলা যায়, দ্বান্দ্বিকতার শক্তিতেই তা বলিয়ান হয়। গত কুড়ি বছরে বাঙালি সংস্কৃতি বিপদের মুখে আছে— আগেও ছিল, কিন্তু এখন প্রতিপক্ষ মূলধারাতেই একটা পা যেন রেখেছে।… বাঙালিয়ানার পুনর্জাগরণ ঘটেছে নিজের ঘরে প্রত্যাবর্তনের মধ্য দিয়ে। বাঙালিয়ানা পরমুখাপেক্ষি নয়, সে নিজেতে নিজেই পূর্ণ।’ ‘বাঙালি সমাজ’ প্রবন্ধটি শুরু হয় ‘বাঙালির সবচে বড় সমালোচক বাঙালি নিজেই। বাঙালির মতো এত আত্মসমালোচনামুখর জাতি আর আছে কিনা সন্দেহ!’ বাক্যদ্বয় দিয়েই। বাঙালির এগিয়ে যাওয়ার পেছনে বাঙালির অবদান অনস্বীকার্য এবং পিছিয়ে যাবার পথেও আছে বাঙালির নিবেদন! প্রবন্ধজুড়ে আমাদের নেতিবাচকসত্ত্বার নানা বিশ্লেষণ প্রবন্ধকার হাজির করেন। রাজনীতি থেকে সমাজব্যবস্থা, অর্থনীতি থেকে ক্রিকেটীয় রাজনীতি— সবটা জুড়ে বাঙালির এই পলায়ন-পরাভব এবং আত্মবিধ্বংসী মানসের নানা রূপ বিধৃত করেন সৈয়দ মঞ্জুরুল ইসলাম। প্রবল আত্মসমালোচনায় মুখর আরেকটি প্রবন্ধ ‘বাঙালি’। আত্মসমালোচনায় দগ্ধ হলে আমাদের দুর্বলতর অনেক দিকই গোছানো যায় অনায়াসে। কিন্তু বাঙালি কি আর তা করে? ‘বাঙালি’ প্রবন্ধের শেষ কয়েকটা লাইন দিয়েই বরং প্রবন্ধকারের ভাষায় বলা যাক, ‘তাই বলে বাঙালির মধ্যে মনুষ্যত্বের কোনো উপাদান কি আর কিছু নেই। আছে। প্রচুর আছে। কিন্তু সেগুলো যে প্রকাশিত হবে, তার পথ রুদ্ধ। পথ রুদ্ধ করে রেখেছে কে আর বাঙালি নিজে।’ ‘আমাদের সাহিত্যে মুক্তিযুদ্ধ ও অন্যান্য প্রবন্ধ’ গ্রন্থে আরেক বিস্তৃত বিষয় রবীন্দ্রনাথ। বাঙালির যাপনে, জীবনে, প্রেমে, দ্রোহে রবীন্দ্রনাথ খুব নিকটেই থাকে। সৈয়দ মঞ্জুরুল ইসলাম রবীন্দ্র আত্মীয়তাকে এত বছর পরে এসে ভিন্নতর ব্যঞ্জনায় উপস্থাপন করেন পাঠকের দরবারে। ‘রবীন্দ্রনাথের চিত্রভাবনা’, ‘রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলা: ক্লেদজ কুসুম’, ‘আকারের মহাযাত্রা: রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলা’, ‘তুমি কি কেবলই ছবি’, ‘রবীন্দ্রনাথের নন্দনচিন্তা’, মহামানবের সাগরতীরে: রবীন্দ্রনাথের সমাজ, রাষ্ট্র/জাতি ও জাতীয়তাবাদ ভাবনা’, রবীন্দ্রনাথের ছিন্নপত্র: গৃহী ও সন্ন্যাসীর বিবাদ’ প্রবন্ধসমূহের শিরোনাম পাঠেই পাঠকের মনে আসবে প্রবন্ধকারের রবীন্দ্রপ্রীতি কিংবা চর্চার ক্ষেত্র কতটুকু প্রসারিত। শেষের দুটো প্রবন্ধ বাদে আর সবগুলো প্রবন্ধেই রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলা, নন্দনচিন্তা, রঙযাপন নিয়ে নানা ধরণের প্রাজ্ঞ মন্তব্য পাওয়া যায়। গান-কবিতা-গল্প-উপন্যাস-প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথে বহুবিস্তৃত জগৎ নিয়ে আমাদের পাঠ আর আগ্রহ প্রকাশ্য, সেই তুলনায় চিত্রকর রবীন্দ্রনাথ পড়ে থাকে পেছনের বেঞ্চে। অথচ সৈয়দ মঞ্জুরুল ইসলাম চরম এক মন্তব্য করেন রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলার মৌলিক দিক নিয়ে, ‘ রবীন্দ্রনাথ নিজে তাঁর চিত্রকলায় এক আধুনিক, বিশ্বজনীন মনন ও মানসের প্রতিফলন ঘটিয়েছেন। তিনি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন, বাস্তব ও পরাবস্তবের চিত্রকল্প নির্মাণ করেছেন, কিন্তু কখনো এই মূল্য বিচারে যাননি যে কোনটা আমাদের, কোনটা অন্যের। তাঁর চিত্রকলার গুণগত উৎকর্ষের বিচারটি ভিন্ন, কিন্তু এর প্রস্তাবনাটি বিশ্বজনীন।’
বাংলাদেশ হয়ে ওঠার পেছনে অনেকানেক মনীষা ও ব্যক্তির উজ্জ্বল অংশগ্রণ সুবিদিত। কিন্তু আমাদের হুজুগের দরুণ আয়োজনে-অন্বেষণে এসব আলোকিত মনীষারা খুব কমই উপস্থিত থাকেন শরীরে-মানসে। অথচ তাদের নিবেদনের শোধ দেয়ার তুল্যমূল্য কোন কালেই হয় না। এই না হওয়ার ফলে, আমরা হয়ে পড়ছি দুর্বল, জ্ঞানের পথে ক্ষীণতম জীব। সৈয়দ মঞ্জুরুল ইসলামের আলোচ্য গ্রন্থের আরেকটি অসাধারণ দিক, তিনি বাংলাদেশ ভূগোলের কতিপয় অসামন্য মানুষের কাজ নিয়েও আলোকপাত করেছেন। ‘শাহ আব্দুল করিম: গণমানুষের বাউল’, ‘কিবরিয়া স্মরণে’, ‘কাইয়ূম চৌধুরী: ফিরে দেখা’, ‘পাঁচ পথিকৃৎ শিল্পী এবং একটি লুপ্ত ঐতিহ্য’, ‘সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর চিন্তা ও সৃষ্টির জগৎ’, ‘দর্শনের মানুষ, সক্রিয়তার মানুষ: চিন্তাবিদ সরদার ফজলুল করিম’ এসব প্রবন্ধগুলোর শরীরে আমরা প্রত্যক্ষ করি অগ্রজের প্রতি অনুজের দায়, দৃশ্যমান হয় তাদের নানাবিধ কাজ ও শ্রমের ইশারা। ‘শাহ আব্দুল করিম: গণমানুষের বাউল’ প্রবন্ধে এরকম বক্তব্য আমাদের প্রেরণা যোগায়— ‘শাহ আবদুল করিম ছিলেন গণমানুষের বাউল, তাদের দুঃখের দিনের কাণ্ডারি শ্রেষ্ঠ বাঙালিদের একজন। তিনি বেঁচে রইলেন অনেকগুলো পরিচয়ে, কিন্তু একই সঙ্গে তিনি যে একজন বাঙালি এবং বিশ্বমানব ছিলেন, সে পরিচয়টি আমাদের অনন্ত অনুপ্রেরণা দেবে, যেমন দেবে তাঁর বাউল সাধনার গানগুলো।’ এরকম কথা উপর্যুক্ত প্রত্যেক মনীষার ক্ষেত্রেই বলা যায় কিন্তু স্বরটা যত বৃহৎ ও আন্তরিক হওয়া দরকার তা যদি অন্তত স্বাধীন বাংলাদেশে হতো তবে জ্ঞানী জন্মানোর পথটা এত ক্ষীণ হতো না। কিবরিয়া-কাইয়ূম চৌধুরীর চিত্রকলা আমাদের সাহস যোগায় সত্য কিন্তু এসব নিয়ে কারো সাধনা কি তেমন চোখে পড়ে? সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী দীর্ঘকাল ধরে তার মননশীল চর্চার মাধ্যমে জাতিকে সেবা দিয়ে যা’েছন, সরদার ফজলুল করিম দর্শনের ভেতর দিয়ে মুক্তির নিশানা খুঁজে গেছেন আজন্ম— তাদের জ্ঞানসেবা নিয়ে আমাদের আলোচনার অনেকান্ত অবকাশ থাকলেও তা হয়নি যথেষ্ট পরিমাণে। সৈয়দ মঞ্জুরুল ইসলাম মূলত এ দিকটাতেই নজর দিয়েছেন, যা প্রাবন্ধিক হিসেবে তার বিচক্ষণতা ও যুগের প্রতি দায়বদ্ধতা প্রকাশ করে। আলোচ্য গ্রন্থের আরেক গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ ‘বাংলাদেশের প্রচ্ছদশিল্প’। প্রকাশনা শিল্পের সাথে, এমনকি প্রকাশিত মহামূল্যবান গ্রন্থটির ক্ষেত্রেও প্রচ্ছদ গুরুত্ববহ এক বিষয়। প্রাগুক্ত প্রবন্ধে প্রবন্ধকার বিস্তারিতভাবে দেশীয় প্রচ্ছদশিল্পের অবস্থার সাথে বৈদেশকেও জুড়ে দেন। এবং নিজস্ব ভাবনার সাথে পরম্পরা মিলিয়ে বলেন, ‘… প্রকাশনা শিল্প থেকে শুরু করে পাঠক পর্যন্ত, সকলের কাছেই প্র’ছদটি বইয়ের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে দেখার প্রবণতার জন্য। এখনও বইয়ের সমালোচনায় প্রচ্ছদশিল্পীর নাম এসে যায়, প্রচ্ছদশিল্পীদের জন্য সর্বদেশীয় পর্যায়ে প্রতিযোগিতা এবং পুরস্কারের ব্যবস্থাও রয়েছে।… তবে প্রচ্ছদশিল্পের টিকে থাকার মূল কারণটি হয়তো সহজেই চোখে পড়ে না, অথচ যার অবদান অনস্বীকার্য: সে হচ্ছে শিল্পীদের নিষ্ঠা এবং আন্তরিকতা।’এই আন্তরিকতার বলেই দিনকে দিন রূপময়, গুণময় হয়ে ওঠছে আমাদের প্রচ্ছদশিল্প। প্রায় অনালোকিত এই বিষয় নিয়ে সৈয়দ মঞ্জুরুল ইসলামের গবেষণা চূড়ান্তরূপে আশাবাদের জন্ম দেয়, নতুন কাজের এষণা দেয়।”আমাদের সাহিত্যে মুক্তিযুদ্ধ ও অন্যান্য প্রবন্ধ’গ্রন্থটি আমাদের চিরায়ত প্রবন্ধচর্চার ধরণে যোগ করেছে ব্যতিক্রমি আলো। গ্রন্থস্থিত প্রতিটি প্রবন্ধই প্রসাদগুণে অনন্য, গতানুগতিক ধারার বাইরে এর প্রক্ষেপন। নতুনতর বিভায় ঔজ্জ্বল্য ছড়িয়ে ক্রমশ প্রবন্ধগুলো ছড়িয়ে পড়ুক নতুন প্রাণে, তারুণ্যে ভরপুর বাংলাদেশে।