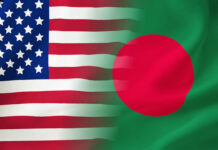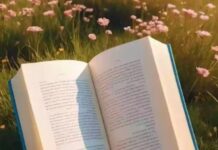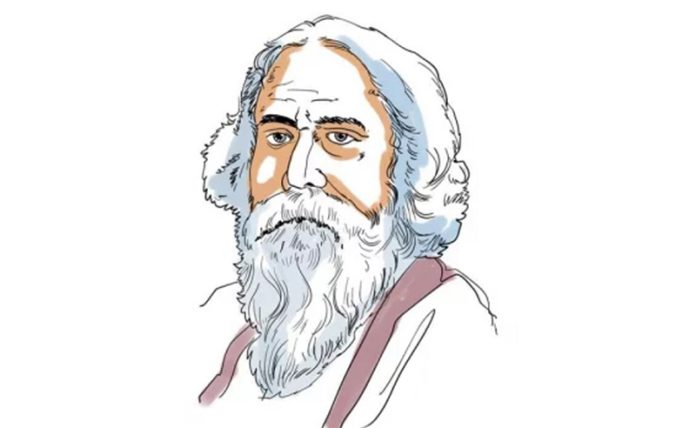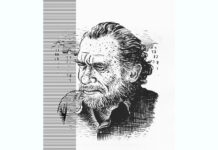মোহীত উল আলম »
সহকর্মী সৈয়দ জসীম উদ্দিন আমাদেরকে চমকে দিলেন। তিনি অনার্সের ছাত্র থাকাকালে নীরদ সি. চৌধুরীকে একটি চিঠি লিখেছিলেন। সেখানে তিনি প্রশ্ন করেছিলেন, নীরদ চৌধুরী কেন সাধু ভাষায় লিখেন। অক্সফোর্ড থেকে ২৬ সেপ্টেম্বর ১৯৯০ সালে নীরদ চৌধুরী জসীম উদ্দিনকে স্বহস্তে লিখে একটি চিঠি পাঠান। সে চিঠি জসীম আমাদেরকে দেখাচ্ছেন ২৫ বছর পরে। হয়তো আগেও দেখিয়েছিলেন, হয়তো মনে পড়ছে না।
জসীমের চিঠির উত্তরে নীরদ চৌধুরী জানাচ্ছেন যে “আপনি যাকে ‘সাধুভাষা’ বলছেন, অথবা যাকে এখন সবাই সাধুভাষা বলে, তাই বাংলা ভাষায় সাহিত্য সৃষ্টির একমাত্র ভাষা। যাকে চলিত বাংলা বলে, তাতে বাঙালী মনের শুধু ঘরোয়া দিকের প্রকাশ হয়, কোনো গভীর বা পূর্ণতালব্ধ ভাব প্রকাশ হয় না। আপনি ধরে নিতে পারেন যে, বাংলা সাহিত্যে ‘মৌখিক ভাষায় যা লেখা হয়েছে তার মধ্যে এক রবীন্দ্রনাথের কিছু রচনা ছাড়া কিছুই টিকবে না।”
তারপর লিখছেন, “‘চলিত’ ভাষায় লেখা আর ‘সাধু’ ভাষায় লেখার মধ্যে কি প্রভেদ তা প্রচলিত বাংলার প্রবর্তক প্রমথ চৌধুরী বুঝেন নাই, এমন কি রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত বুঝেন নাই।”
নীরদ চৌধুরীর শেষোক্ত বাক্যটা থেকে রবীন্দ্রনাথের মহাপ্রয়ানের ৮৪তম বার্ষিকীতে একটি বক্তব্য রাখতে চাই। নীরদ চৌধুরী এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন তাঁর “আত্মঘাতী বাঙালী”তে। সে বইটি আমার পড়া নেই। কিন্তু যে কারণে নীরদ চৌধুরীর বক্তব্যটি দিয়ে আমি আলোচনায় নামতে চাই, সেটি সাধুভাষা ও চলিত ভাষার ওপর কোন তাত্ত্বিক আলোচনা নয়, কিন্তু আমার নিজেরই একটি ধারণা যে, রবীন্দ্রনাথের রচনা সাধুভাষায় যতোটা গভীর আর প্রাঞ্জল, চলিত ভাষায় রচিত রচনাগুলির মধ্যে সে স্বাদ পাওয়া যায় না।
আমার এই মনে হওয়াকে আমি কোনভাবেই বৈকারণিক বা ভাষাগত শৈলী দিযে প্রমাণ করতে পারব না, কিন্তু আমার অনুভূতি এই যে, রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প, উপন্যাস, জীবনস্মৃতি, প্রবন্ধ ও অন্যান্য রচনা যেগুলি তিনি সাধুভাষায় লিখেছিলেন সেগুলি তুলনামূলকভাবে অধিকতর সুখপাঠ্য। ছোটগল্পে সে “ঘাটের কথা” থেকে শুরু করে “ত্যাগ,” “একরাত্রি,” “জীবিত ও মৃত,” “স্বর্ণমৃগ,” “জয়পরাজয়,” “কাবুলিওয়ালা,” “ছুটি” হয়ে যতই এগোতে থাকি, তখন বাক্যবিন্যাসে সাধুভাষার যে মাহাত্ম্যের ছোঁয়া পাই, সেটি নীরদ চৌধুরীকে আকৃষ্ট করেছিলো কিনা জানি না, কিন্তু আমার মনে হয় সাধুভাষার বিস্তারিত গঠণপ্রণালী রবীন্দ্রনাথকে মানবমনের গভীরের সীমানাবিহীন রহস্য উদ্ঘাটিত করতে সাহায্য করেছিল। চলতি ভাষার চাঁছাছোলা সংক্ষিপ্ত পরিসরে গভীর কথা ব্যক্ত করার যেন সুযোগ ছিল না, কিন্তু সাধুভাষার প্রশস্ত সড়কে, শব্দগত ব্যাপ্তির মধ্যে রবীন্দ্রনাথ লিখতে পেরেছিলেন এমন একটি পংক্তি: “পূর্বপ্রথানুসারে ঝি সকালবেলায় তামাক সাজিয়া তাঁহাকে খুঁজিল, কোথাও দেখিতে পাইল না। বেলা হইলে প্রতিবেশিগণ গৃহপ্রত্যাগত বান্ধবের খোঁজ লইতে আসিল, কিন্তু বৈদ্যনাথের সহিত সাক্ষাৎ হইল না।” (স্বর্ণমৃগ”)
বৈদ্যনাথের নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়ার আবিস্কারটা গভীরভাবে রেখাপাত করে আমাদের মনে যেমনটি “অতিথি” গল্পের তারাপদের নিরুদ্দেশ হওয়া, “কিন্তু পরদিন তারাপদকে দেখা গেল না,” বা “নষ্টনীড়” গল্পের চারুর শেষ কথা, “না, থাক্” গভীর মনোবেদনার সঞ্চার করে যেটি আমি তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস শেষের কবিতা পাঠ করে কখনও পাইনি।
আমি মাঝে মাঝে চিন্তা করি, রবীন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতির অর্ন্তভুক্ত রচনাগুলো তিনি যদি প্রমথ চৌধুরীর প্ররোচনায় চলিত ভাষায় লিখতেন তা হলে এত আনন্দঘন বর্ণনা আমরা পেতাম কিনা। ধরুন তাঁর “নর্মাল স্কুল” শীর্ষক রচনাটির কথা। এইটির প্রথম পংক্তি এরকম: “ওরিয়েন্টাল সেমিনারিতে যখন পড়িতেছিলাম তখন কেবল ছাত্র হইয়া থাকিবার যে-হীনতা, তাহা মিটাইবার একটা উপায় বাহির করিয়াছিলাম।” এ পংক্তিটি এখন মনে মনে আপনি চলিত ভাষায় রূপ দেন দেখবেন যে “মিটাইবার” আর “মেটাবার” মধ্যে যেন আকাশপাতাল তফাৎ। এই কারণেই আমি নীরদ চৌধুরীর সঙ্গে একমত যে চলিত ভাষায় কিছু কেজো কথা হয়তো বলা যায়, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের প্রেক্ষাপটে সাধুভাষা গভীর সমুদ্রের মতো, আর চলিত ভাষা চিলের উড়ে যাওয়ার মতো ক্ষণিক।
শুধু শেষের কবিতা নয়, রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ পরিচিত উপন্যাস সাধুভাষায় নয় চলিত ভাষায় লেখা। ঘরে বাইরে যে পাঠ পরিক্রমার পর অতিশয় ক্লান্তিকর কথার কচকচিসম্পন্ন একটি উপন্যাস মনে হয় তার কারণ এর চলিত ভাষা। দেখাচ্ছি: “অপব্যয় আমি সইতে পারতুম, কিন্তু আমার কেবলই মনে হত বন্ধু হয়ে এ লোকটা আমার স্বামীকে ঠকাচ্ছে। কেননা, ভাবখানা তো তপস্বীর মতো নয়, গরীবের মতোও নয়, দিব্যি বাবুর মতো।” এটি হচ্ছে বিমলার সন্দ্বীপ সম্পর্কে অভিমত। কিন্তু চটুলতার ভাবটা ভাষার চটুলতার জন্য কেবল জলখেলা হয়ে গেল। উল্টোভাবে, তাঁর অত্যন্ত সফল উপন্যাস গোরাতে তিনি বর্ণনা রেখেছেন সাধুভাষায় কিন্তু সংলাপ চলিত ভাষায়। এই কারণে গোরা উপন্যাস হিসেবে সুখপাঠ্য।
রবীন্দ্রনাথের একটি উপন্যাস আমার কাছে সেরা মনে হয়, নৌকাডুবি। এখানে বর্ণনা এবং সংলাপ উভয়ত সাধুভাষায়। এইজন্য সাধুভাষায় রচিত ছোটগল্পগুলো যেমন রূপলালিত্যে ভরা, এই উপন্যাসটিও তেমন। শুরুর দিক থেকে একটু উদ্ধৃতি দিই: “এইরূপে রমেশ যখন নারীভক্তির উচ্ছ্বসিত উৎসাহে অন্য দিনের চেয়ে দু-পেয়ালা চা বেশি খাইয়া ফেলিয়াছে, এমন সময় বেহারা তাহার হাতে এক-টুকরা চিঠি দিল। বর্হিভাগে তাহার পিতার হস্তাক্ষরে তাহার নাম লেখা। চিঠি পড়িয়া তর্কের মাঝখানে ভঙ্গ দিয়া রমেশ শশব্যস্তে উঠিযা পড়িল। সকলে জিজ্ঞাসা করিল, ‘ব্যাপারটা কী?’ রমেশ কহিল, ‘বাবা দেশ হইতে আসিয়াছেন।’ হেমনলিনী যোগেন্দ্রকে কহিল, ‘দাদা, রমেশবাবুর বাবাকে এইখানেই ডাকিয়া আনো-না কেন, এখানে চায়ের সমস্ত প্রস্তুত আছে।’”
উপরোক্ত বর্ণনার মাঝে রসবোধের যে সাড়ম্বর উপস্থিতি, “দুই পেয়ালা চা বেশি খাইয়া ফেলিয়াছে” এই হিউমার তাঁর চলিত ভাষায় লেখা উপন্যাসগুলোতে ফুটে ওঠেনি। এমনকি শেষের কবিতার অমিট রায়ে আর লাবণ্যের মধ্যে যে ব্যাটল অব উইট চলে কলসীর জল আর পুকুরের জল নিয়ে তাও আমার কাছে ঘটনার আবেগের প্রেক্ষাপটে নিতান্তই ভাষার চাতুরি মনে হয়।
আমি জানি না, নীরদ চৌধুরী রবীন্দ্রনাথের চলিত ভাষার ব্যবহার নিয়ে এমন কথা বলতেন কিনা, কিন্তু আমার মনে হয়েছে রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে নিজের রচনাবলী চলিত ভাষায় বা কথ্য ভাষায় স্থানান্তর করার মধ্যে যুগের সঙ্গে তাল মেলানোর (”আজ সবার রঙে রঙ মেলাতে হবে”) দাবি থাকলেও তাঁর প্রাণের সঙ্গে এই ভাষার শেষ পর্যন্ত জুড়ি মেলেনি।
এটা এমনও হতে পারে যে শিশুবেলা থেকে তিনি যে ভাষায় পড়তে এবং লিখতে অভ্যস্ত ছিলেন, বহু দশক পরে সে ভাষা থেকে সরে গিয়ে কথ্য ভাষায় লিখতে গিয়ে তাঁর চমৎকারিত্বে তিনি অভিভুত ছিলেন, কিন্তু মানবচরিত্রের নিগূঢ় প্রদেশে প্রবেশ করার যে সহজাত অর্ন্তদৃষ্টি তাঁর সাধুভাষায় রচিত ছোটগল্প ও জীবনকাহিনীতে প্রদর্শিত হয়েছে, সেগুলি তাঁর চলিত ভাষায় রচিত রচনাগুলোর ক্ষেত্রে হয়নি। এবং একই কারণে রবীন্দ্রনাথের নাটকগুলোকে আমার নাটক মনে হয় না। মনে হয়, অমিত প্রতিভার একটা ব্যর্থ প্রচেষ্টা।
পরিশেষে বলি, তাঁর ছোট জামাই ড. নগেন্দ্রকে রবীন্দ্রনাথ বিস্তর চিঠি লিখেছিলেন অনেকটা অনোন্যপায় হয়ে। কারণ নগেন নিজেকে বাংলাদেশের আর দশটা স্বামীর মতো অর্থগৃধ্নু পাত্র হিসেবে প্রমাণ করছিলেন। এই চিঠিগুলি তিনি সাধুভাষায়ই লিখেছিলেন। তিনি এরকম একটি সদুপদেশ তাঁকে দিয়েছিলেন যেটি অনেকটা এরকম (স্মৃতি থেকে লিখছি): “বাবা নগেন, জীবনে যদি তুমি নিজেকে কোন বৃহৎ কাজের সঙ্গে জড়িয়ে নিতে না পারো, তাহা হইলে এই জীবন তোমার কাছে নিরর্থক হইয়া উঠিবে।”
রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে সাধুভাষার জায়গায় চলিত ভাষা যেন মাছের আঁেশ ঝামার ডলা।