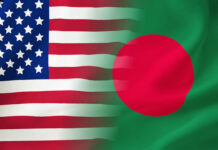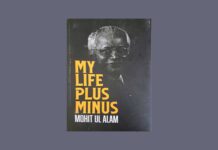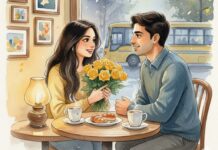হাবিবুল হক বিপ্লব »
বাংলা নামে যে দেশ নাম তার বাংলাদেশ এবং ভাষার নামে যে জাতির পরিচয় সে জাতির নাম বাঙালি। সেই ঐতিহ্যবাহী বাঙালিরই একান্ত নিজস্ব উৎসব বাংলা নববর্ষ উৎসব- এই উৎসব বিশ্বের ত্রিশ কোটি বাঙালিদের একটি সর্বজনীন নিজস্ব উৎসব। বাংলা সনের প্রথম দিন অর্থাৎ পহেলা বৈশাখ বাংলা শুভ নববর্ষ। বাংলাদেশ, ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা (আগরতলা) এবং আসামের বাঙালি অধ্যুষিত শিলচর (যেখানে বাংলা ভাষার জন্য ১১জন বাঙালি প্রাণ দিয়েছিলেন), করিমগঞ্জ ও হাইলাকান্দি এলাকা এবং বিশ্বের সকল প্রান্তের সকল বাঙালি এ দিনে নতুন বছরকে বরণ করে নেয়, ভুলে যাবার চেষ্টা করে অতীত বছরের সকল দুঃখ-গ্লানি এবং সব বাঙালিরই কামনা থাকে নতুন বছরটি যেন সমৃদ্ধ ও সুখময় হয়। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পহেলা বৈশাখ বা বাংলা নববর্ষ উপলক্ষে বলেছেন- “মুছে যাক গ্লানি, ঘুচে যাক জরা/ অগ্নিস্নানে শুচি হোক ধরা।”
পৃথিবীতে খুব কম জাতিরই নিজস্ব নববর্ষ আছে- বাঙালিরা সেই ঐতিহ্যবাহী গর্বিত জাতি যাদের নিজস্ব নববর্ষ, নিজস্ব ভাষা, নিজস্ব শক্তিশালী বর্ণমালা, নিজস্ব ষড়ঋতু, নিজস্ব উঁচুমানের সংস্কৃতি রয়েছে- এবং সারা বিশ্বে একমাত্র বাঙালিরাই তাদের নিজস্ব ষড়ঋতুকে আলাদা আলাদা করে আনুষ্ঠানিকভাবে বরণ করে নেয়। বাংলাদেশ তথা বাংলা ছাড়া পৃথিবীর আর কোথাও ছয় ঋতু নেই- এটাই বাঙালির গর্ব করার মত বিচিত্র বৈশিষ্ট্য। অসাম্প্রদায়িক সাংস্কৃতিক উৎসবে এবং অপার আনন্দের সাথে বাঙালি এর মধ্যে খুঁজে পেয়েছে তার প্রকৃত পরিচয়।
বাংলা নববর্ষের ইতিহাসঃ বাংলাদেশে বাংলা একাডেমি কর্তৃক নির্ধারিত আধুনিক পঞ্জিকা অনুসারে প্রতিবছর ১৪ এপ্রিল তথা ১ বৈশাখ বাংলা নববর্ষ ঘটা করে পালন করা হয়। বাংলা সাল প্রবর্তন নিয়ে বিভিন্ন মতবাদ রয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেঃ
১। প্রাচীন বঙ্গদেশের (গৌড়) রাজা শশাঙ্ক (রাজত্বকাল আনুমানিক ৫৯০-৬২৫ খ্রিস্টাব্দ) বঙ্গাব্দ চালু করেছিলেন। সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভে শশাঙ্ক বঙ্গদেশের রাজচক্রবর্তী রাজা ছিলেন। আধুনিক বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার অধিকাংশ এলাকা তাঁর সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল৷ অনুমান করা হয় যে, জুলীয় বর্ষপঞ্জীর বৃহস্পতিবার ১৮ মার্চ ৫৯৪ এবং গ্রেগরীয় বর্ষপঞ্জীর শনিবার ২০ মার্চ ৫৯৪ বঙ্গাব্দের সূচনা হয়েছিল।
২। ভারতে ইসলামী শাসনামলে হিজরী পঞ্জিকা অনুসারেই সকল কাজকর্ম পরিচালিত হত। মূল হিজরি পঞ্জিকা চান্দ্র মাসের ওপর নির্ভরশীল। চান্দ্র বৎসর সৌর বৎসরের চেয়ে ১১/১২ দিন কম হয়। কারণ সৌর বৎসর ৩৬৫ দিন, আর চান্দ্র বৎসর ৩৫৪ দিন। একারণে চান্দ্র বৎসরে ঋতুগুলি ঠিক থাকে না। আর চাষাবাদ ও এ জাতীয় অনেক কাজ ঋতুনির্ভর। এজন্য ভারতের মোগল সম্রাট আকবরের সময়ে প্রচলিত হিজরী চান্দ্র পঞ্জিকাকে সৌর পঞ্জিকায় রূপান্তরিত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সম্রাট আকবর ইরান থেকে আগত বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ও জ্যোতির্বিদ আমির ফতুল্লাহ শিরাজীকে হিজরী চান্দ্র বর্ষপঞ্জীকে সৌর বর্ষপঞ্জীতে রূপান্তরিত করার দায়িত্ব প্রদান করেন। ফতুল্লাহ শিরাজীর সুপারিশে পারস্যে প্রচলিত সৌর বর্ষপঞ্জীর অনুকরণে ৯৯২ হিজরি মোতাবেক ১৫৮৪ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট আকবর হিজরি সৌর বর্ষপঞ্জীর প্রচলন করেন। তবে তিনি ঊনত্রিশ বছর পূর্বে তার সিংহাসন আরোহনের বছর থেকে এ পঞ্জিকা প্রচলনের নির্দেশ দেন। এজন্য ৯৬৩ হিজরী সাল থেকে বঙ্গাব্দ গণনা শুরু হয়। ৯৬৩ হিজরি সালের মুহররম মাস ছিল বাংলা বৈশাখ মাস, এজন্য বৈশাখ মাসকেই বঙ্গাব্দ বা বাংলা বর্ষপঞ্জির প্রথম মাস এবং ১লা বৈশাখকে নববর্ষ ধরা হয়। প্রথমে এই সনের নাম ছিল ফসলি সন এবং পরে বঙ্গাব্দ বা বাংলা বর্ষ নামে পরিচিত হয়। [সুত্রঃ উইকিপিডিয়া ও ইন্টারনেট]
৩। পুঁথি গবেষক ও বিশিষ্ট পণ্ডিত যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য বাংলা ও এর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের সন-তারিখ সম্পর্কে নানা অনুসন্ধান করেছিলেন। সে জন্য তাকে এ অঞ্চলের সন-তারিখ সম্পর্কে একজন বিশেষজ্ঞ বলে অভিহিত করা হয়। তিনি তাঁর বিশিষ্ট গবেষণাকর্ম ‘বাংলা পুঁথির তালিকা সমন্বয়’ (প্রথম খণ্ড পৃ. ৩৭৮)-এ বলেছেন : ‘‘সুলতান হোসেন শাহের সময়ে বঙ্গাব্দ বা বাংলা সন চালু হয়। বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও বাঙালিত্বের বিকাশেও শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ ও সুলতান হোসেন শাহের অবদান বিরাট। সুলতান হোসেন শাহ নিজেকে বাঙালি বলে পরিচয় দিতে গর্ব অনুভব করতেন। ‘শাহ-এ-বাঙালিয়ান’ বলে নিজের পরিচয় লিপিবদ্ধ করেছেন তিনি। তাদের একজন, অর্থাৎ হোসেন শাহের পক্ষে বাংলা সন চালু করা অসম্ভব নয়।’’
তবে সুলতানি আমল বিশেষজ্ঞ শ্রী সুখময় মুখোপাধ্যায় এ মত মেনে নিতে পারেননি। তিনি লিখেছেন : ‘‘কোন বিষয় থেকে যতীন্দ্রবাবু এ সিদ্ধান্তে উপনীত হযেছেন তা তিনি উল্লেখ করেননি। সেজন্য একে গ্রহণ করতে আমাদের অসুবিধা আছে।’’ এটা ঠিক যে, কোনো কোনো পুঁথিতে ‘যবন নৃপতে শকাব্দ’ বলা হয়েছে, রামগোপাল দাসের রসকল্পাবলীর পুঁথিতেও বঙ্গাব্দকে ‘যাবনী বৎসর’ বলা হযেছে। কিন্তু এ থেকেই এটা অনুমান করা ঠিক নয় যে, কোনো মুসলমান রাজা বঙ্গাব্দ প্রবর্তন করেছিলেন, এবং তিনি হোসেন শাহ।
হোসেন শাহ (রাজত্বকাল ১৪৯৩-১৫১৯) বঙ্গাব্দ চালু করেছিলেন এ মতের বিপক্ষে একটি যুক্তি দেখানো হয়। হোসেন শাহের পুত্র নসরৎ শাহ একটি সংবৎ প্রবর্তন করেছিলেন যা ‘নসরৎশাহী সন’ নামে পরিচিত। বঙ্গাব্দের সঙ্গে এর তফাত দু’বছরের। ১০৮৩ নসরৎশাহ সন এবং ১০৮১ বঙ্গাব্দে লেখা একটি পুঁথি পাওয়া গেছে (যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য, বাংলা পুঁথির তালিকা সমন্বয়, পৃ. ৩৭৭)। বঙ্গাব্দ যদি হোসেন শাহের দ্বারা প্রবর্তিত হত, তাহলে তাহলে তার পুত্র একটি নতুন সংবৎ প্রবর্তন করতেন কি? (সুধাময় মুখোপাধ্যায়, ১৪০০ সাল, শারদীয় সংখ্যা এক্ষণ, কোলকাতা)। [সুত্রঃ ড.সামসুজ্জামান খানের একটি কলাম থেকে।]
বাংলা মাসের নামকরণঃ বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে, বাংলা মাসের নামগুলো বিভিন্ন নক্ষত্র বা তারকারাজির নাম থেকে নেয়া হয়েছে। এই নাম সমূহ গৃহীত হয়েছে জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক প্রাচীন গ্রন্থ “সূর্যসিদ্ধান্ত” থেকে।
আগেকার দিনে অগ্রহায়ণ মাসে ধান কাটা শুরু হত বলে এই মাসকে বছরের প্রথম মাস ধরা হত। তাই এ মাসের নামই রাখা হয় অগ্রহায়ণ। অগ্র অর্থ প্রথম আর হায়ন অর্থ বর্ষ বা ধান। সম্রাট আকবরের সময়ে একটি বিষয় ছিল অত্যন্ত কষ্ট সাধ্য, তা হল মাসের প্রত্যেকটি দিনের জন্য আলাদা আলাদা নাম ছিল। যা কিনা প্রজা সাধারণের মনে রাখা খুবই কষ্ট হত। তাই সম্রাট শাহজাহান ৭ দিনে সপ্তাহ ভিত্তিক বাংলায় দিনের নামকরণের কাজ শুরু করেন। ইংরেজী বিশেষজ্ঞদের সহায়তায় ইংরেজি ৭ দিনের নামের কিছুটা আদলে বাংলায় ৭ দিনের নামকরণ করা হয়।
বাংলা সনে দিনের শুরু ও শেষ হয় সূর্যোদয়ে। ইংরেজি বা গ্রেগরীয় বর্ষপঞ্জীর শুরু হয় যেমন মধ্যরাত হতে। এভাবে বর্ষ গণনার রীতিকে বাংলায় প্রবর্তনের সংস্কার শুরু হয় মোঘল আমলে।
বর্ষ বরণের প্রবর্তিত রুপঃ বাংলা দিনপঞ্জীর সাথে হিজরি ও খ্রিস্টীয় সনের মৌলিক পার্থক্য হলো হিজরী সন চাঁদের হিসাবে এবং খ্রিস্টীয় সন ঘড়ির হিসাবে চলে। তাই হিজরি সনে নতুন তারিখ শুরু হয় সন্ধ্যায় নতুন চাঁদের আগমনে এবং ইংরেজি দিন শুরু হয় মধ্যরাতে আর বাংলা সনের দিন শুরু হয় ভোরে সূর্যোদয়ের সাথে সাথে- অর্থাৎ সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় বাঙালি নববর্ষ অর্থাৎ পহেলা বৈশাখের উৎসব- যা পৃথিবীর অন্যান্য জাতি থেকে সম্পূর্ণ আলাদা- এটাই বাঙালির একান্ত গর্ব করার মতো নিজস্ব বৈশিষ্ট্য- যার জন্য সারা পৃথিবী অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে।
নতুন বছর বরণে বাঙালি আয়োজনঃ বাংলাদেশে বর্ষবরণের মূল আয়োজন মূলত ঢাকার রমনা পার্কের বটমূলকে (অনেকে বলেন অশ্মথ মূল) ঘিরেই। সেই আনন্দ আয়োজন আর পান্তা ইলিশের বাঙালিয়ানায় পুরো জাতি নিজেকে খুঁজে ফেরে ফেলে আসা গত দিনগুলোর স্মৃতি রোমন্থন আর নতুন অনাগত সময়কে বরণের ব্যস্ততায়। পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি জাতিই নিজেদের ইতিহাস সংস্কৃতিকে বরণের জন্য বিশেষ বিশেষ দিনকে স্মরণীয় করে রাখে।
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের “এসো হে বৈশাখ……এসো , এসো….”গানের মাধ্যমে তারা স্বাগত জানাতে শুরু করে নতুন বছরকে। বর্ষবরন এগিয়ে যায় আরো এক ধাপ। বিস্তৃত হতে শুরু করে ছায়ানট নামের সংগঠনটির। যা এখন বাংলাদেশের সংস্কৃতির ক্ষেত্রে একটি মহিরূহে পরিণত হয়েছে।
১৯৭২ সালের পর থেকে রমনা বটমূলে বর্ষবরণ জাতীয় উৎসবের স্বীকৃতি পায়। ১৯৮৯ সালে বৈশাখী মঙ্গল শোভাযাত্রার মাধ্যমে এক ধাপ বাড়তি ছোঁয়া পায় বাংলা নববর্ষ বরণের অনুষ্ঠান। ছড়িয়ে পড়ে সবার অন্তরে অন্তরে। প্রতি বছরই তাই কোটি বাঙালির অপেক্ষা থাকে কবে আসবে বাংলা নববর্ষ।
আধুনিকতার ছোয়ায় বর্ষবরনের অনুষ্ঠান মালা : বেসরকারি স্যাটেলাইট টেলিভিশন চ্যানেলগুলোর কল্যাণে এখন ভোরে রমনা বটমূলে শুরু হওয়া বর্ষ বরণের অনুষ্ঠান উপভোগ করে কয়েক কোটি বাঙ্গালি। ছায়ানটের শিল্পীদের পরিবেশনায় বৈশাখকে বরণের সব প্রস্তুতি করা হয় আগেভাগে। পহেলা বৈশাখের দিন ভোরেই শুরু হয় বিভিন্ন স্থানে উম্মুক্ত কনসার্ট, বাউল, লালন, জারী-সারি, মুর্শেদী গানের আসর । আর শহুরে এ্যামিউজমেন্ট পার্কের স্বাদ থাকলেও পহেলা বৈশাখের দিন অন্তত নাগর দোলায় চড়তে চায় অনেক শিশুই।
বাংলা বর্ষবরণে যে কয়টি আনুষ্ঠানিকতা পালন না করলেই নয় তন্মদ্ধ্যে, মঙ্গল শোভাযাত্রা, বৈশাখী মেলা, হালখাতা অন্যতম।
মঙ্গলশোভা যাত্রাঃ বর্ষবরণের অনুষ্ঠান মালায় ভিন্ন মাত্রা যোগ করেছে মঙ্গল শোভাযাত্রা। ১৯৮৯ সালে এই শোভাযাত্রার প্রচলন শুরু করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইন্সটিটিউটের শিক্ষার্থীরা। পহেলা বৈশাখের দিন সকাল গড়িয়ে যখন রমনা টি.এস.সি শাহবাগে মানুষের উপচে পরা ভিড় থাকে, তখন শুরু হয় মঙ্গলশোভা যাত্রা। ঢাকাবিশ্ববিদ্যালয় চারুকলা থেকে শোভাযাত্রা বের হয়ে রাজধানীর বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে। এখানে পশু পাখির মুখাকৃতির ছবিসহ গ্রামীণ ঐতিহ্যের নানা অনুসঙ্গকে ফুটিয়ে তোলা হয় নানা রং বেরং-এর মুখোশ ও আলপনার মাধ্যমে। ছেলে বুড়ো সবাই তখন মেতে ওঠে বর্ষবরণের মঙ্গলশোভা যাত্রার আনন্দে।
বৈশাখী মেলাঃ বৈশাখ মাস বলতে তো মেলার মাসকেই বোঝায়। একসময় শুধু গ্রাম গঞ্জে মেলা হলেও এখন এর পরিধি বিছিয়েছে শহরের বড়সর এপার্টমেন্ট ও হাই-সোসাইটিতেও। তবে পার্থক্য থাকে গ্রামের আর শহুরে মেলার। বাঁশের বেতের তৈজষ আর নানা জাতের খেলার সামগ্রী, নারকেল মুড়কিসহ আরো কত কি থাকে এসব মেলায়- তার ইয়ত্তা নেই। মেলার সময়ে নৌকাবাইচ, লাঠি খেলা, কুস্তির আসর বসে এখনও।
চট্টগ্রামে লালদীঘীর ময়দানে অনুষ্ঠিত হয় জব্বারের বলি খেলা। আর বর্ষবরণের এই মেলা প্রবাসীদের জন্য হয় মিলন মেলা। দীর্ঘ ব্যস্ততার অবসরে বৈশাখী মেলা প্রবাসী বাঙালিদের দেয় অফুরন্ত আনন্দ।
জাপানে প্রতি বছরই অনেক ঘটা করে বিশাল পরিসরে আয়োজন করা হয় বৈশাখী মেলা। জাপান প্রবাসীদের এ মিলন মেলার রেশটা থাকে সারা বছর জুড়ে। এছাড়া নিউইয়র্ক, লন্ডনসহ বিশ্বের অন্যান্য বড় বড় শহরগুলোতে বসে বৈশাখী মেলার আয়োজন।
হালখাতাঃ প্রাচীন বর্ষবরণের রীতির সাথে অঙ্গাঅঙ্গি ভাবেই জড়িত একটি বিষয় হল হালখাতা। তখন প্রত্যেকে চাষাবাদ বাবদ চৈত্র মাসের শেষ দিনের মধ্যে সকল খাজনা, মাশুল ও শুল্ক পরিশোধ করে দিত। এরপর দিন অর্থাৎ পহেলা বৈশাখ ভূমির মালিকরা তাদের প্রজা সাধারণের জন্য মিষ্টান্ন দিয়ে আপ্যায়নের ব্যবস্থা রাখতেন। যা পরবর্তিতে ব্যবসায়িক পরিমন্ডলে ছড়িয়ে পড়ে। দোকানীরা সারা বছরের বাকীর খাতা সমাপ্ত করার জন্য পহেলা বৈশাখের দিনে নতুন সাজে বসে দোকানে। গ্রাহকদের মিষ্টিমুখ করিয়ে শুরু করেন নতুন বছরের ব্যবসার সূচনা। এ উৎসব গুলো সামাজিক রীতির অংশ হিসেবে পরিণত হয়েছে প্রতিটি বাঙালির ঘরে। এখনো গ্রাম গঞ্জে নববর্ষে হালখাতার হিড়িক পড়ে বাজার, বন্দর ও গঞ্জে।
শেষ কথাঃ খুব দুঃখজনক হলেও সত্যি যে বাঙালি সংস্কৃতির সবচেয়ে বড় উৎসব বাংলা নববর্ষের তারিখ নিয়ে দুই বাংলার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে- বাংলাদেশের বাঙালিরা পহেলা বৈশাখ অর্থাৎ বাংলা নববর্ষ পালন করে গ্রেগরিয়ান ক্যালেণ্ডার অনুযায়ী ১৪ এপ্রিল; আর পশ্চিম বাংলার বাঙালিরা কখনো ১৫ এপ্রিল আবার কখনো ১৪ এপ্রিল বাংলা নববর্ষ পালন করে। আমাদের প্রশ্ন দুই বাংলায় একই দিনে বর্ষবরণ করতে অসুবিধা কোথায়? বাঙালি সংস্কৃতির একটি প্রধান উৎসব দুই পৃথক দিনে পালন না করলে কি নয়? এতে করে বিশ্বের কাছে ঐতিহ্যবাহী বাঙালি সম্প্রদায়কে অনেক প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হচ্ছে। নতুন বছরটি হোক শান্তি, সম্প্রীতি, সম্ভাবনার এবং বাংলা শুভ নববর্ষে আমরাও আশা করবো বাংলাদেশের তথা বিশ্বের ত্রিশ কোটি বাঙালির ঐতিহ্যের বন্ধন পরিচয় যেন চির অটুট থাকে। বাংলার জয় হোক, বাঙালির জয় হোক।