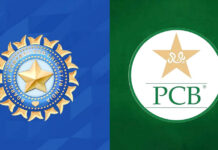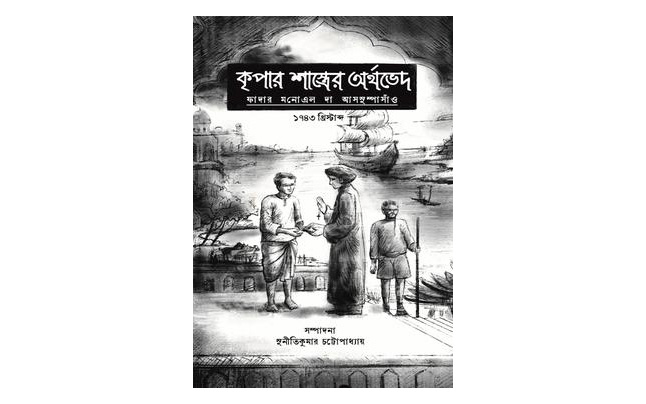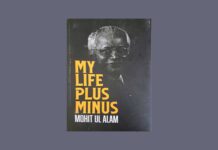শওকত এয়াকুব »
মানুষের প্রথম ভাবানুভূতির আবেগ কম্পিত প্রকাশও সকল কালে সর্বত্র পদ্যময়। কিন্তু সাহিত্যে তখনই গদ্যের জন্ম হয়, যখন মানুষের মধ্যে যুক্তি আর চিন্তার উন্মেষ ঘটে। ঠিক তেমনি বাংলা কবিতা জন্মের হাজার বছর পর বাংলা গদ্যের উদ্ভব ঘটে। ষোড়শ শতক থেকে রাজনৈতিক ও ধর্মীয় বিষয়ের বাইরেও বাংলা গদ্যের বৈচিত্র্যময় ব্যবহার লক্ষ করা যায়। তবে এসব বিষয়ের মধ্যে গদ্যচর্চা সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং আইন গ্রন্থের অনুবাদ এবং ভাষা শেখার বই রচনার মধ্য দিয়ে গদ্যের প্রসার ঘটে। বাংলা সাহিত্যের যখন নবযুগের সূচনা হয় তখন খৃষ্টান মিশনারির বিশেষ উদ্দেশ্যে বাংলা গদ্যসাহিত্য ত্বরান্বিত হয়। তাই বলা যায় বাংলা গদ্যসাহিত্য নবযুগের প্রথম অবদান। এর আগে ষোড়শ শতাব্দী হতে বাংলা গদ্যের প্রাচীন গদ্য উল্লেখযোগ্য।
পর্তুগিজ পাদ্রি দোমিঙ্গো দে সোসাই প্রথম গদ্য লেখেন ফার্নান্দেজ নামে এক সরকারি কর্মকর্তার তত্তাবধানে। পাদ্রি সোস একটি ধর্মগ্রন্থ অনুবাদ করেন এবং ১৫৯৮ খৃষ্টাব্দের শেষ অর্ধে তা অনুদিত হয়। এর পাশাপাশি পর্তুগিজরা কিছু কিছু ব্যাকরণ ও অভিধান গ্রন্থ রচনা করে বিদেশিদের বাংলা শিক্ষার পথ সুগম করেন। তার পরবর্তী সময়ে রোমান ক্যাথলিক পর্তুগিজ পাদ্রি মনোএল দা আসসুম্পসাঁও কর্তৃক ১৭৩৪ খ্রিস্টাব্দে রচিত এবং ১৭৪৩ খ্রিস্টাব্দে লিসবনে রোমান হরফে মুদ্রিত কৃপার শাস্ত্রের অর্থ ভেদ গ্রন্থটি বাংলা গদ্যের প্রাথমিক প্রচেষ্টার নিদর্শন হিসেবে উল্লেখযোগ্য। পর্তুগিজ ধর্মপ্রচারক রচিত যেসব গ্রন্থে গদ্যরীতি অনুসৃতি হয়েছে তা পরবর্তী সময়ে বাংলা গদ্যসাহিত্যে তেমন প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। কারণ পর্তুগিজ পাদ্রিদের সাথে পরবর্তী সময়ের ইংরেজ পাদ্রিদের কোনো যোগাযোগ ছিল না এবং ধর্মীয় আদর্শের দিক দিয়েও যথেষ্ট পার্থক্য ছিল। ইংরেজ পাদ্রিদের মাধ্যমে যে গদ্যচর্চা শুরু হয়েছিল তা ছিল স্বতন্ত্র।
১৮০০ খৃষ্টাব্দে ফোর্ড উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠার পূর্বে, খৃষ্টান পাদ্রিরা বিশেষ আগ্রহের সাথে গদ্য রচনায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। খৃষ্টধর্ম প্রচারের স্বার্থেই তাদের এই আত্মনিয়োগ। এর ফলে বাংলা গদ্যসাহিত্য বিশেষ প্রেরণা লাভ করেছিল। বাংলা গদ্যের ইংরেজ আমল থেকে ব্যাপক চর্চা শুরু হলেও তার আগ থেকে বাংলা ভাষায় কবিতা চর্চার মাধ্যমে বহু আরবি-ফারসি শব্দ বাংলা ভাষায় স্থান করে নিলেও যখন বাংলা গদ্য চর্চা শুরু হয় তখন আইনের বই অনুবাদ করতে গিয়ে বাংলা গদ্যে দুই রকম পরিবর্তন সাধিত হয়।
লর্ড ওয়েলেসলি ভারতের গভর্নর জেনারেল হয়ে এসে লক্ষ্য করলেন, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারিরা ব্রিটেন থেকে আসতেন ভারতবর্ষে শাসনকার্য চালানোর জন্য। বয়সে তারা ছিলেন অতি নবীন, প্রায় যুবক বলা যেতে পারে। তারা ব্রিটেন থেকে যখন ভারতবর্ষে আসতেন তখন নিজেদের ভাষাও ভালো করে জানতেন না, যে দেশ শাসনের জন্য তাদের পাঠানো হতো, সে দেশ সম্বন্ধেও তারা ছিলেন সম্পূর্ণ অজ্ঞ। তাই শাসনের জন্য ওয়েলেসলি মনে করলেন, এ দেশে এমন একটি কলেজ প্রতিষ্ঠিত হওয়া দরকার, যেখানে তরুণ কর্মচারীরা পড়াশুনা করে এ দেশের ভাষা, সাহিত্য, ভূগোল, ইতিহাস, আইন-কানুন প্রভৃতি শিখবেন। এজন্য ১৮০০ সালে কলকাতা লালবাজারের কাছে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠা করলেন। অবশ্য এর সঙ্গে বাঙালির যোগ ছিল না, কিন্তু বাংলাসাহিত্য, বিশেষত গদ্যসাহিত্যের যোগ ছিল অনেক।
১৮০০ সালে ফোর্ড উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠা হলেও ৪ মে কলেজের প্রতিষ্ঠা দিবস এবং ২৪শে নভেম্বর থেকে কলেজের কার্যক্রম শুরু হয়। এর একবছর পর ১৮০১ সালে প্রবর্তিত হয় বাংলা-সংস্কৃত-মারাঠি বিভাগ। এই
বাংলা-সংস্কৃত-মারাঠি বিভাগের ভার বাইবেলের অনুবাদে হস্তক্ষেপ করে শাসক মহলে পরিচিত পাওয়া ফোর্ট উইলিয়ামের ওপর অর্পিত হলো। তখন তিনি ওই তিন ভাষার বিভাগীয় প্রধান হয়ে দেশীয় অধ্যাপক নিযুক্ত করতে লাগলেন ফোর্ট উইলিয়াম বাংলা পড়াতে গিয়ে বিদেশিদের সহজে বাংলা ভাষা শিখবার জন্য খুব উদগ্রীব হয়ে পড়েন। তিনি দেখলেন, সহজ বাংলায় লেখা গদ্যগ্রন্থ প্রকাশিত না হলে বিদেশিদেরকে বাংলা শেখানো অত্যন্ত কষ্টকর হবে। তখনো কোনো গদ্যগ্রন্থ তার হাতে আসেনি। তাই তিনি নিজে বাংলা গদ্যে বই লিখলেন এবং বাঙালি অধ্যাপক ও অন্যান্য পণ্ডিতদের দিয়ে লিখিয়েও নিলেন। পণ্ডিত ও লেখকদের উৎসাহ দেওয়ার জন্য তিনি কলেজ কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে পণ্ডিত-মুন্সিদের জন্য অনেক পুরস্কার ও অন্যান্য নানাধরনের সহায়তা চেয়ে নিতেন। তার অধীন অধ্যাপকমণ্ডলী এবং বাইরের কেউ কেউ তার নির্দেশে অনেকগুলো বাংলা গদ্যগ্রন্থ লিখেছিলেন-অবশ্য প্রায় সবগুলো সংস্কৃত, ইংরেজি ও ফার্সি থেকে অনুদিত এবং অধিকাংশ বই গল্পকাহিনিমূলক। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের জন্য রচিত ও প্রকাশিত বইগুলোর সাথে সে যুগের বাঙালিদের অল্প পরিচয় থাকতে পারে। কিন্তু এসব গ্রন্থকে খ্রিস্টানি ব্যাপার বলে অনেকেই এর থেকে দূরে থাকতেন। গদ্য রচনার দিক দিয়ে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার প্রশংসার যোগ্য। অন্য লেখকদের বইগুলোর ভাষা ছিল জড়তাপূর্ণ, সাধারণ পাঠক সমাজে এসব বইয়ের চল ছিল না। কেরির উদ্যোগে নিম্নলিখিত পণ্ডিত ও মুন্সিদের সাহায্যে অনেক গদ্যগ্রন্থ রচনা করিয়ে নিয়েছিলেন- (১) গোলকনাথ শর্মা (হিতোপদেশ- ১৮০২ সালে প্রকাশিত),(২) তারিণীচরণ মিত্র (ওরিয়েন্টাল ফেবুলিস্ট, ঈশপ্স ফেবসের অনুবাদ- ১৮০৩),(৩) রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায় (মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়সা চরিত্রং ১৮০৫), (৪) চন্ডীচরণ মুন্সি (তোতা ইতিহাস- তুতিনামা নামক ফরাসি গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ ১৮০৫),(৫) রামকিশোর তর্কচূড়ামণির ‘হিতোপদেশ’ (১৮০৮ সালে রচিত, কিন্তু পাওয়া যায়নি ৬) হরপ্রসাদ রায় (পুরুষ পরীক্ষা, বিদ্যাপতির ওই নামের সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ- ১৮১৫), (৭) কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন (পদার্থতত্ত্ব- কৌমুদী- ১৮২১, আত্মতত্ত্ব কৌমুদী- ১৮২২), (৮) রামরাম বসু, (রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র-১৮০১),(৯) মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার এবং (বত্রিশ সিংহাসন, রাজাবলি -১৮০৮) (প্রবোধন্দ্রিকা-১৮৩৩),(রচনাকাল আনুমানিক ১৮১৩, মুদ্রিত ১৮৩৩) এই কটি গদ্যগ্রন্থ গুলো রচনা করেন।
১৮১২ সালে প্রকাশিত কেরির ‘ইতিহাসমালা’ এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা কর্তব্য। এরকম সহজ-সরল গদ্যরীতি মৃত্যুঞ্জয় ভিন্ন ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের আর কোনো পণ্ডিত রচনা করতে পারেননি। নামে ইতিহাসমালা হলেও এতে বেশিরভাগ কাহিনি অনৈতিহাসিক গালগল্প । এমনকী এতে চণ্ডীমঙ্গলের লহনা-খুল্লনার গল্পও আছে। কেরি এতে যেমন ভারতীয় পুরাকথা ও গল্পকাহিনি সম্বন্ধে সরস উপাখ্যান সংগ্রহ করেছিলেন, তেমনি অতি পরিচ্ছন্ন ভাষায় ব্যক্ত করেছিলেন। বাংলা-সংস্কৃত বিভাগের অধ্যক্ষ হিসেবে ভাষার বিশুদ্ধতার প্রতি কেরি বিশেষ দৃষ্টি রাখতেন। ফারসি মিশ্রণের প্রতি তিনি বিরূপ ছিলেন। তাঁর রচনা প্রাথমিক পর্যায়ে সহজ সরল থাকলেও পরবর্তীতে বাংলা গদ্যের ব্যাপক সূচনাতে হিন্দু লেখকগোষ্ঠী বাংলা গদ্যকে সংস্কৃতঘেঁষা করে তোলেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন সংস্কৃত পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয়। এর ফলে তদ্ভব, আরবি-ফারসি ও দেশজ শব্দের যে প্রচলন ছিল তা বেহাত হয়ে গদ্যরীতির মধ্যে কৃত্রিম গাম্ভীর্য আনীত হয়।