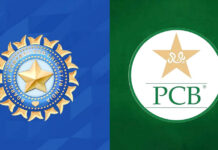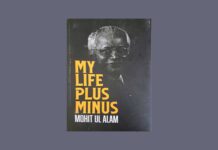রতন কুমার তুরী »
দেশে দেশে, কালে কালে কিছু সাহিত্যিক তাদের মেধা,আর মননশীলতা দিয়ে কিছু অমর সাহিত্য রচনা করে যান, যে সাহিত্য ওই সমাজে চিরকাল মানুষের মনে ভাবনার উদ্রেক ঘটায় এবং মানুষকে তাদের জীবনের সুখ দুঃখগুলো বুঝতে শেখায়। সেরকম একটা সাহিত্য হচ্ছে বিভূতিভূষণ বন্দোপাদ্যয়ের ‘পথের পাঁচালী’ এবং উপন্যাসটির মূল চরিত্র দুর্গার যাপিত জীবনের সহজ সরল দুঃখভরা ঘটনাবলী। পথের পাঁচালীর দুর্গা চিরকালই দুঃখী এবং জীবনচলাও অত্যন্ত সীমিত।
কাশবনে হারিয়ে ফেলা বোন, অপুর দুর্গা বিসর্জন
শরৎ এলে পথের পাঁচালী সিনেমায় দেখা অপু-দুর্গার কাশবনে ঘুরেফিরে রেলগাড়ি দেখতে যাওয়ার সেই কালজয়ী ছবিটি কখনো কখনো উঁকি দেয় আমাদের মনে। আমরাও ঘুরতে যাই কাশবনে। কেন এমন ঘটে? শরতের কোনো বেদনাতুর মুহূর্তে আমাদের কেন মনে পড়ে দুর্গা চরিত্রটির কথা?
শরৎ এসে পড়েছে। কেউ জানে না কী হবে। অপু-দুর্গা সেবার তিনটি নতুন জিনিস দেখে লাজবাব হয়ে গিয়েছিল। নিশ্চিন্দিপুর গ্রামের বাইরে সেটাই তাদের প্রথম যাওয়া। কৈশোরের আনন্দ-বিষাদমাখা মন নিয়ে তারা দেখেছিলো বিদ্যুতের বড়বড় খুঁটি, টেলিগ্রাফ তারের রিন রিন শব্দ আর কাশবনঘেঁষা রেললাইন দিয়ে ছুটে চলা রেলগাড়ির মোহময় ঝিকমিক শব্দ । কালো ধোঁয়া ওড়ানো রেলগাড়ি। সেই রেলগাড়ি চলে যাওয়ার পর অনেক্ষণ আকাশটা কালো ধোঁয়ায় ঢাকা পড়েছিলো। যেনো জানিয়ে দিতে চাইছিলো আসন্ন বিপর্যয়ের কথা। এটা সিনেমার ভাষা। সিনেমায় পরিচালক চলচ্চিত্রের পরিণতির আভাস শুরুর দৃশ্যে অথবা মূল যে ঘটনা কাহিনিকে গড়ন দেবেন, কোনো না কোনো দৃশ্যের সংকেতে তার আভাস রেখে দেন। তেমনি আমরা সত্যজিৎ রায়ের পথের পাঁচালী সিনেমায় দেখি, কাশবনে বসে আখ চিবোতে চিবোতে দুর্গাই প্রথম কিসের যেনো আওয়াজ টের পায়। সে-ই অপুকে নিয়ে ছুট দেয় রেললাইনের দিকে। কিন্তু যখন রেলগাড়িটা আসে, দেখা যায়, অপু একাই সেটা দেখছে। দৃশ্যে কোথাও দুর্গা নেই। অপুর দেখাটাও ইশারাময়। ক্যামেরা বসেছে রেলের ওপারে, অপু আরেক পারে। চাকার ফাঁক দিয়ে তার মুখ একবার দেখা যায়, একবার হারায়। অপু যে এই রেলপথ ধরেই একদিন নিশ্চিন্দিপুর গ্রাম ছেড়ে চলে যাবে, দুর্গা যে তার সঙ্গী হতে পারবে না, সেই বিয়োগের চিহ্ন হয়ে থাকে দৃশ্যটা।
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পথের পাঁচালী উপন্যাস যারা পড়েছেন আর যারা সত্যজিৎ রায়ের বানানো পথের পাঁচালী সিনেমা দেখেছেন, দুই তরফের আস্বাদন হুবহু এক নয়। তবে দুটিকে এক করে নিলে মনের ভেতর স্মৃতিগুলো ছবি হয়ে যায়। সার্থক কোনো উপন্যাসের এমন দ্বিতীয় জন্ম ঘটানোর মতো চলচ্চিত্র খুবই বিরল। উপন্যাসে দুর্গা কখনো রেলগাড়ি দেখেনি। কিন্তু সিনেমায় ভাই-বোন অপু–দুর্গা একসঙ্গে সেই অভিযানে বেরোয়। কিন্তু তারা সেই রেলপথ আর খুঁজে পায় না।
উপন্যাসের দুর্গা ম্যালেরিয়া জ্বরে ঝিরঝিরে নিমপাতার মতো কাবু হয়ে শুয়ে ভাইকে ফিসফিসিয়ে বলেছিলো, ‘আমায় একদিন তুই রেলগাড়ি দেখাবি?’ আর সিনেমায় বলে, ‘এবার জ্বর ছাড়লে একদিন রেলগাড়ি দেখতে যাবো, হ্যাঁ ?’ দুই উক্তির মধ্যে পার্থক্য অনেক। যে ভাই-বোন একসঙ্গে প্রকৃতির শিশু হয়ে ঘুরে বেড়িয়েছে, বোনের সাথে হয়ে তার চুরি করা ফলফলাদি খেয়েছে, সুখ-দুঃখের সেই শৈশবসাথী যে আর কখনোই অপুকে পায়ে পায়ে নিয়ে ঘুরবে না, সেই বেদনা বড় হয়ে বাজে পরের দৃশ্যগুলো দেখার সময়; যখন দুর্গার মৃত্যু হয়।
অপুর সঙ্গে বিভূতিভূষণের দুর্গা রেলগাড়ি দেখতে যেতে না পারলেও সত্যজিতের অপু-দুর্গাকে আমরা সাদা সাদা কাশবনের ভেতর দিয়ে দৌড়ে দৌড়ে ধোঁয়ামেঘে কালো করে ফেলা আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে রেলগাড়ি দেখতে দেখি। তারপর একসময় টের পাই, দৃশ্যটা চিরকালের মতো মনে গেঁথে গেছে। জীবনের রেলপথে আমরা যতো দূরেই যাই না কেন, কিশোরবেলার প্রথম দেখাগুলো, পয়লা বেদনাগুলো ভুলি না। অপুও ভোলে না সেই অন্য রকম শরতের কথা। ওই কাশবনেই সে তার বোনকে হারিয়ে ফেলে ডেকে উঠেছিল, ‘দিদিইই!’ এমনকি ছুটন্ত রেলগাড়ির কাছাকাছি তাকেই একা দাঁড়িয়ে থাকতে দেখি। সেখান থেকে ফিরে আশ্বিনের বৃষ্টিতে ভিজে জ্বরে পড়ে ম্যালেরিয়া বাঁধিয়ে বসে দুর্গা। আশ্বিনী ঝড়বৃষ্টির রাত পেরিয়েই তার মৃত্যু হয় নিঃশব্দে।
ম্যাক্সিম গোর্কির মা, পৃথিবীর পাঠশালা ও পৃথিবীর পথে ট্রিলজির পাশে বিভূতিভূষণের পথের পাঁচালী, অপরাজিত, অপুর সংসার মিলিয়ে নিলে বুঝতে পারি, কেনো বাংলা মুলুকে সমাজ রূপান্তর হয়নি, কেনো বিপ্লব সাধিত হয়নি, কেনো বাস্তবতার কাছে হার না মানা নায়কের জন্ম হয়নি। আমাদের নায়ক দুঃখের আঘাতে ফণা তোলে না, বিষণ্ন হয়ে যায় বা ঘর ছেড়ে উদাসীনতার পথ নেয়। যেমন রবীন্দ্রনাথের গোরা উপন্যাসের গোরা। কিন্তু দুটি ট্রিলজিতেই কেন্দ্রীয় বালক চরিত্র স্বজনের মৃত্যুর ধাক্কাতেই বড় হয়ে ওঠে। দুর্গা-হারা হওয়া ছাড়া বালক অপু পরের উপন্যাস অপরাজিতর অপু হতে পারতো না। সেদিক থেকে অপুর নিশ্চিন্দিপুরের নিস্তরঙ্গ জগতের বাইরে চলে যাওয়ার প্রধান সংকেত ওই শরতে দুর্গার মৃত্যুর ঘটনা। সেই থেকেই বালক অপু যেনো জগতের অলৌকিক আনন্দের ভাগ পাওয়া সত্ত্বেও চির বিষণ্ন হয়ে পড়ে। ‘সকল দুঃখের প্রদীপ জ্বেলে’ও এই বিসর্জনের ব্যথার পূজা আর তার আর হয় না সমাপণ। বিষণ্নতা দুঃখের চেয়ে বড় কিছু। ফ্রয়েড বলছেন, যে শোকের উদ্যাপন হয়নি, যে হারানোর ক্ষতি কখনো নিরূপণ করা হয়নি, মনের আড়ালে তা বিষাদের সুর হয়ে বাজে। বিভূতিভূষণের প্রাকৃত বিষণ্নতা যেন জীবনানন্দীয় বিষণ্নতারই গদ্যরূপ। এক শারদ ঋতুতে তা চিরতরে মিশে যায় অপুর সত্তায়। অপরাজিতের অপুর মনে হয়, ‘শুধু তাহার দিদি শুইয়া আছে। সে দিদির বয়স আর বাড়ে নাই, মুখের তারুণ্য বিলুপ্ত হয় নাই, তার কাচের চুড়ি, নাটা ফুলের পুঁটুলি অক্ষয় হইয়া আছে।’ এই মায়াবাস্তব কেমন জীবনানন্দীয় নয়?
‘মনে পড়ে কবেকার পাড়াগাঁর অরুণিমা স্যানালের মুখ;
উড়ুক উড়ুক তারা পউষের জ্যোৎস্নায় নীরবে উড়ুক
কল্পনার হাঁস সব পৃথিবীর সব ধ্বনি সব রং
মুছে গেলে পর
উড়ুক উড়ুক তারা হৃদয়ের শব্দহীন জ্যোৎস্নার ভিতর।’
(‘বুনো হাঁস’, জীবনানন্দ দাশ)
কিন্তু এই দুর্গাকে কোথায় পেলেন বিভূতিভূষণ? এর তদন্ত করেছেন বিভূতি বিশারদ রুশতী সেন (বিভূতিভূষণ: দ্বন্দ্বের বিন্যাসে, ১৯৯৮, প্যাপিরাস, কলকাতা)। পরিমল গোস্বামীর সাক্ষ্যে তিনি জানাচ্ছেন: ‘বিভূতিবাবু আমাকে বললেন, “পথের পাঁচালী যখন প্রথম লিখি, তাতে দুর্গা ছিল না। শুধু অপু ছিল। একদিন হঠাৎ ভাগলপুরের রঘুনন্দন হলে একটি মেয়েকে দেখি। চুলগুলো তার হাওয়ায় উড়ছে। সে আমার দৃষ্টি এবং মন দুই-ই আকর্ষণ করল, তার ছাপ মনের মধ্যে আঁকা হয়ে গেল, মনে হলো, উপন্যাসে এ মেয়েকে না আনলে চলবে না। পথের পাঁচালী আবার নতুন করে লিখতে হলো এবং রিকাস্ট করায় একটি বছর লাগলো।”
এরপর বিভূতিভূষণকে উদ্ধৃত করে যোগেন্দ্র সিনহার বয়ানে পাচ্ছি ওই একই বালিকার কথা: ‘ওর চোখে আমি পেলাম এক অবর্ণনীয় সন্দেশ, এক অপূর্ব আহ্বান আর মধুর বেদনার এক অদেখা জগৎ। আমি ওর দিকে তাকিয়ে রইলাম। আমার মনে হলো যে এই বালিকা আমার পুস্তকে যতক্ষণ পর্যন্ত স্থান না পায়, ততোক্ষণ পর্যন্ত আমার লেখা ব্যর্থ ও নির্জীব।’
এক গ্রাম্য মেয়েকে দেখে বিভূতির মনে যে আশ্চর্য মায়া জন্মে যায়, তার কি কোনো ব্যক্তিগত কারণ থাকতে পারে?
সাহিত্যের ইতিহাসকার সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ওই সাহিত্য ও জীবনের ওই অকাল্পনিক সুতা ধরিয়ে দেন। তিনি জানান, ‘ৃআরও একটি মেয়ে এই চরিত্রের মূলে বর্তমান। বিভূতিভূষণের সবচেয়ে ছোট বোন. তাঁকে বিভূতিভূষণ আদর করে “দুর্গা” বলে ডাকতেন।’ উপন্যাসের দুর্গার মতো সেই বোনও অল্প বয়সে মারা যায়। বয়সে বড় হলেও শিশুর মতো স্বভাবের জন্য বিভূতিভূষণ তাঁর বোন এবং বোনের মতো সঙ্গিনীদের কাছে শৈশব জীবনে স্নেহ, ভালোবাসা ও আশ্রয় পেয়েছিলেন। ব্যক্তিগত জীবনে বোন দুর্গার স্মৃতি যদি এত মধুর ও মর্মান্তিক না হতো, তাহলে পথের পাঁচালীর দুর্গার মৃত্যু ঘটতো কি? এ কারণেই কি বিভূতিসাহিত্যে চলে চিরশোকসভা ? পথের পাঁচালীর দুর্গা, বল্লালী-বালাইও আম আঁটির ভেঁপু অধ্যায় পেরোনোর আগেই মরে যায়। অপরাজিতার অপর্ণা মরে গিয়ে অপুকে বিবাগী করে ফেলে। দুর্গা যদি না-ও মরতো, তার পরিণতি হতো বিভূতির অন্য সব গল্প-উপন্যাসের মেয়েদের মতো লাবণ্যহারা ও আশাহীন। ঠিক যেমন জীবনানন্দের সরোজিনী, মৃণালিনী, অরুণিমারা।
সেটাও ছিল শরৎকাল। শরতে কাশ ফোটে, শরতে বাঙালি হিন্দুর বড় উৎসব দুর্গাপূজা হয়, শরতেই আবার সেই মহাদেবীর বিসর্জন। দুর্গার অবিস্মরণীয় মৃত্যুও হয় শরৎকালে। ‘নেবু পাতায় করমচা’ বলতে বলতে দুর্গা নিজেই যেন বৃষ্টি হয়ে ঝরে পড়েছিল। নিশ্চিন্দিপুরে দেবী দুর্গার কথা বা তাঁর পূজার কথা তেমন আসে না। আসে এক নিম্নবর্গীয় দেবী বিশালাক্ষীর কথা। আর আছে হরেক রকম ব্রতের সংবাদ। তাহলে সেই শরতের দুর্গা কে? কার বিসর্জন হলো অপুর জীবন থেকে?
পথের পাঁচালীতে দুর্গা নামে দেবীর কথা তেমন নেই, আছে এক গরিবস্য গরিব সর্বজয়ার অশান্ত, চঞ্চল প্রকৃতিকন্যা দুর্গার কথা। এই উপন্যাসে খুবই সম্ভব ছিল ঘটা করে দুর্গাপূজার উৎসব দেখানো। কিন্তু ইন্দির ঠাকরুনের করুণ জীবন ও মৃত্যু দিয়ে বিভূতি যে বিষাদের সুরে পথের পাঁচালী গাওয়া শুরু করলেন, অভাবের যে মর্সিয়া চলে হরিহর-সর্বজয়ার সংসারে, সেখানে তো উৎসবের আলোবাদ্যি বেমানান। তাই স্বর্গের দেবীকে আড়ালে রেখে এক দুঃখিনী বালিকাকে সেই আসনে বসালেন লেখক। অভাগিনী এই মনুষ্যকন্যাই তো নিশ্চিন্দিপুরের স্মৃতির বেদিতে চির অধিষ্ঠিতা। পথের পাঁচালীর প্রধান বিসর্জনের ব্যথা তার প্রয়াণেই সৃষ্ট। ছোট ভাই অপুকে যে প্রকৃতি ও বনাঞ্চল চিনিয়েছিল, আস্বাদন দিয়েছিল গ্রাম্য প্রকৃতির মধ্যকার তুচ্ছতার সৌন্দর্যের, পৃথিবীর পথে যে কিছুদূর এগিয়ে দিয়ে গিয়েছিল বালক অপুকে, অপু যাকে কখনো ভুলতে পারেনি, অথচ যার মুখ আবছায়া হয়ে গিয়েছিল পরে; সেই দুর্গার স্মৃতির টানেই অপুর সংসারের অপু তার ছেলে কাজলকে রেখে গিয়েছিল নিশ্চিন্দিপুরের রাণুদির কাছে।
এতকাল পর এসে মনে হয়, শরতের কাশবনের ভেতর দিয়ে যে কিশোরী দৌড়ে যায়, সেই দুর্গাই তো পথের পাঁচালীর দুঃখের পূজার প্রধান দেবী। সেই-ই এই আখ্যানের শরৎদুহিতা, অকালবোধনের পর অকালমৃত্যুতে যার বিসর্জন। সেই তো আমাদের ‘গডেস অব স্মল থিংস’! বিভূতিভূষণ তাঁর শৈশবে হারানো বোনকে তাহলে এভাবেই অমর করে রেখে গেলেন! আর কী আশ্চর্য, এমনই এক শরতে নিজেও চলে গেলেন বিভূতিভূষণ!
প্রকৃতপক্ষে বাংলা সাহিত্যে বিভূতিভূষণ সাহিত্য আমাদের দুঃখ বেদনার রঙ শেখায়। বিভূতিভূষণ মানুষের জীবনের দুঃখ কষ্টগুলো যেভাবে স্বার্থক এবং
বাস্তবভাবে বিদৃত করেছেন তা আর কোনো,সাহিত্যিক পারেননি। আর তাই তার পথের পাঁচালী উপন্যাসটি পাঠক যতবার পড়েছেন কিংবা সিনেমার পর্দায় দেখেছেন ততবারই ছোট্ট দূর্গার জন্য কেঁদেছেন। এখানেই বিভূতি সাহিত্যের সফলতা।