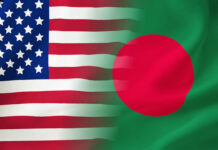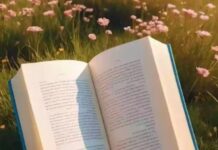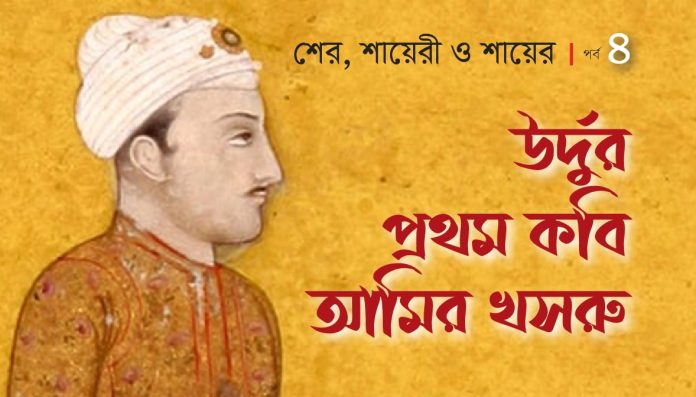উর্দুর প্রথম নিদর্শন পাওয়া যায় নবম শতাব্দীতে। যে কোন ভাষার মতো এই ভাষাও গড়ে উঠেছিল সাধারণ মানুষের মুখে মুখে। ফলে তার কোন লিখিত রূপ একেবারে প্রথমদিকে পাওয়টা সুলভ ছিল না।
মধ্য এশিয়া থেকে আসা তুর্কি, পাঠান, মোগল এইসব নানা জনগোষ্ঠীর সঙ্গে স্থানীয় মানুষদের সংযোগ থেকে জন্ম হয়েছিল উর্দু ভাষার। সাহিত্যের ভাষা হয়ে উঠতে তার বেশ সময় লেগেছে।
পশ্চিমা এক গবেষকের মতে প্রথম উর্দু লেখক হলেন মাসুদ, যাকে তিনি মুসলিম ভারতের দান্তে বলেছেন। মাসুদের পুরো নাম শেখ ফরিদউদ্দিন মাসুদ (১১৭৩-১২৬৫)। তবে তিনি পরিচিত ছিলেন বাবা শেখ ফরিদ বা ফরিদ শকরগঞ্জ নামে। তিনি মূলত একজন সুফি সাধক। শুধু মুসলমান নন, শিখরাও তাঁকে সম্মান করেন। তাঁর কিছু বাণী গুরু নানকজি পবিত্র গ্রন্থসাহেবে স্থান দিয়েছিলেন। আসলে তিনি লিখতেন মুলতানি পাঞ্জাবিতে। প্রাচীন পাঞ্জাবি সাহিত্যের তিনিই অবিসংবাদিত প্রথম লেখক। জন্ম পাঞ্জাবে হলেও অনেকটা সময় তিনি দিল্লিতে কাটিয়েছেন। ফলে আদিম উর্দুতে তিনি কিছু লিখে থাকলে অবাক হওয়ার কিছু নেই।
শেখ ফরিদের শিষ্য শেখ নিজামউদ্দিন (১২৪২-১৩২৫)। তিনি নিজামউদ্দিন আউলিয়া নামেই সমাধিক পরিচিত। নিজামউদ্দিন আউলিয়ার শিষ্য হলেন আমির খসরু, প্রাথমিক উর্দু সাহিত্যে যাঁর অবদান কেউই অস্বীকার করতে পারেন না। খসরু লিখতেন মূলত ফারসি ভাষাতেই। তখনও উর্দু পূর্ণাঙ্গ ভাষা হয়ে ওঠেনি।
ভাষা হিসেবে উর্দুকে প্রথম সনাক্ত করতে পেরেছিলেন আমির খসরু। উর্দু হলো সেই মুখের ভাষা, যা পরবর্তীকালে আমির খসরু ও আরো কয়েকজনের হাত ধরে সাহিত্যের ভাষা হয়ে ওঠে। উর্দু ভাষার প্রথম কবিদের একজন আমির খসরু।
ভাষা হিসেবে উর্দুর বয়স খুব বেশি নয়। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে আমির খসরু সাহিত্যকর্মে সর্বপ্রথম ভাষাটি ব্যবহার করেন। তখন এর নাম ছিল ‘হিন্দভী’, মানে হিন্দুস্থানের ভাষা। আজ যাকে আমরা উর্দু নামে চিনি। বহুকাল আগে এটি হিন্দভী, দেহলভী, লস্করী, গুজরি, দকনি এবং রেখতা নামে পরিচিত ছিলো।
আমির খসরুর আসল নাম আবুল হাসান ইয়ামিনউদ্দিন। জন্ম ১২৫৩ সালে ভারতের উত্তর প্রদেশের মমিনাবাদ জেলার পাতিয়ালায়। আমির খসরুর বাবা আমির সাইফুদ্দিন মাহমুদ ছিলেন তুর্কি বংশোদ্ভূত। আর মা বিবি দৌলত নাজ ছিলেন ভারতীয়। তিনি সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবনের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজপুত রাওয়াত আরজের কন্যা।
মঙ্গোলদের আক্রমণের সময় খসরুর বাবা ভারতে চলে আসেন এবং মামলুক রাজবংশের সুলতান শামসুদ্দিন ইলতুতমিশের অধীনে পাতিয়ালা রাজ্যে জায়গিরদারি লাভ করেন।
আমির খসরুর বয়স যখন মাত্র ৭ বছর, তখন তিনি বাবাকে হারান। এরপর নানা ইমাদুল মুলকের নিকট লালিত পালিত হন। মাত্র ৮ বছর বয়সে তিনি কাব্যচর্চা শুরু করেন। ১৬ বছর বয়সে তার প্রথম কাব্যগ্রন্থ ‘তুহফাতুস সিগার’ প্রকাশিত হয়। এমন এক পরিবেশে তিনি বেড়ে উঠেছিলেন, যাতে শৈশব থেকেই তাঁর মধ্যে দুটি সংস্কৃতির সংযোগ ঘটেছিলো।
যে সময়কালে আমির খসরুর বেড়ে ওঠা তখন দিল্লি সালতানাতের বয়স পঁচাত্তরে পৌঁছে গেছে। শান-শওকত ও বিশালতা এমন পর্যায়ে যে, একে দ্বিতীয় বাগদাদ বলে গন্য করা হতো।
মঙ্গোলীয়দের ধ্বংসজ্ঞের কারণে বহুসংখ্যক কবি, আমির, পণ্ডিত, আলেম, রাজনীতিক মধ্য এশিয়া ছেড়ে ভারতবর্ষের দিল্লিতে এসে আশ্রয় নেয়। দিল্লির সব রঙই অবলোকন করেছেন খসরু।
আমির খসরু তাঁর কালে দিল্লির শাসক হিসেবে এগারো জনকে পেয়েছেন। দিল্লি সালতানাতের সাত শাসকের রাজদরবারের সাথে যুক্ত ছিলেন সংগীতজ্ঞ ও কবি হিসেবে। দিল্লির অন্যতম পরাক্রমশালী সুলতান আলাউদ্দিন খিলজির সভা কবি এবং দরবারের প্রধান সংগীতজ্ঞ হিসেবে কাজ করেছেন আমির খসরু।
আমির খসরু একাধারে একজন ফারসি কবি, সঙ্গীতজ্ঞ, ইতিহাসবিদ, লোক-সংস্কৃতি উপাদান সংগ্রাহক। ভারতের আদি অনথ্রোপলজিস্ট বা নৃতাত্বিকদের একজন তিনি। ভারতীয় জাতীয়তাবাদের অন্যতম উদগাতা ভাবা হয় তাঁকে।
ফারসি কাব্যে আমির খসরুকে হাফিজ সিরাজির সমান হিসেবে গণ্য করা হয়। মসনবী, কাসিদা, গজল, রূবাই প্রত্যেক ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। সবমিলিয়ে প্রায় তিন লক্ষ পঙক্তি লিখে গেছেন। লিখেছেন পাহালিস (ধাঁ ধাঁ, হেয়ালি) ও দোহা, যা আধুনিক কালেও এসে পৌঁছেছে।
পারস্য সংগীতের ‘পরদা’ এবং ভারতীয় ‘রাগ’ সম্পর্কে আমির খসরুর গভীর জ্ঞান ছিল। ভারতীয় এবং পারস্য সংগীতের মিলনে সংগীতে একটি নতুন ধারার সৃষ্টি করেন তিনি।
ভারতে পরিচিত সঙ্গীত ধারা ধ্রুপদ, যা একেবারেই শাস্রবদ্ধ। প্রচলিত এই ধারার বাইরে গিয়ে কিছু করা তৎকালীন পণ্ডিতরা মোটেও পছন্দ করতেন না। উত্তর ভারতের জনমানুষের লোকগীতির সাথে ধ্রুপদ মিলিয়ে সঙ্গীতের একটি নতুন ধারার জন্ম দেন আমির খসরু, যার নাম খেয়াল।
কাওয়ালি, আমির খসরু উদ্ভাবিত একটি সংগীত ধারা। শব্দটি এসেছে আরবি ‘কাওল’ বা ‘কাওলুন’ শব্দ থেকে। যার অর্থ কথা, বাক্য। বহুবচনে শব্দটি ‘কাওয়ালি’। হযরত নিজামউদ্দিন আওলিয়ার দরবারে আমির খসরু কাওয়ালি গাইতেন। এটি সহজ, বোধগম্য ও জনপ্রিয়।
‘তারানা’ সংগীত ধারা আমির খসরুর নিজস্ব আবিস্কার। এটি হলো একপ্রকার শ্রুতিমধুর এবং দ্রুতগতির উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত। এছাড়া সেতার ও তবলা বাদ্যযন্ত্রের আবিষ্কারক খসরু। অসাধারণ গান ও কবিতার জন্য তাঁকে ‘ভারতের কণ্ঠস্বর’ বা ‘ভারতের তোতা’ (তুতি-ই-হিন্দ) বলা হয়।
নিজামউদ্দিন আওলিয়া ও আমির খসরু উভয় উভয়ের আধ্যাত্মিক প্রেমে পড়ে গিয়েছিলেন। এক্ষেত্রে তাদেরকে মাওলানা জালালউদ্দিন রুমি ও শামস তাবরিজির মধ্যকার প্রেমের সাথে তুলনা করা যায়। ১৩২৫ সালের শুরুতে নিজামউদ্দিন আওলিয়া মৃত্যুবরণ করেন। গুরুর মৃত্যুর ছয় মাস পরে একই সালে আমির খসরু গত হন। অসিয়ত অনুসারে, গুরু-শিষ্য দিল্লিতে একই স্থানে শায়িত আছেন।
১.
খসরু দরিয়া প্রেম কা উল্টি ওয়া কি ধার
জো উতরা সো ডুব গ্যায়া জো ডুবা সো পার
[ দরিয়া-নদী; উল্টি-উল্টো; ধার-ধারা বা প্রবাহ; জো-যে; সো-সে ]
খসরু প্রেমের নদী, এর ধারাই উল্টো রকম
যে পার হলো সে ডুবলো, যে ডুবলো সেই হলো পার
২.
খসরু বাজি প্রেম কি ম্যায়ঁ খেলুঁ পি কে সংগ
জিত গ্যায়ি তো পিয়া মোরে হারি পি কে সংগ
[ খেলুঁ-খেলবো; পিÑপ্রিয়া; সংগ-সাথে; গ্যায়ি-গেলে ]
খসরু প্রেমের বাজি খেলবো প্রিয়র সাথে
জিতে গেলে প্রিয় আমার, হারলে প্রিয় আমার
৩.
আপনি ছবি বানাই কে ম্যায়ঁ তো পি কে পাস গ্যায়ি
জাব ছবি দেখি পিহু কি সো আপনি ভুল গ্যায়ি
[ আপনি-নিজের; বানাই-বানানো (একেঁ); জাব-যখন ]
নিজের ছবি একেঁ, গেলাম আমি প্রিয়র কাছে
যখন দেখি প্রিয়র ছবি, গেছি নিজের কথা ভুলে
৪.
শাবানে হিজরা দারায চুঁ যুলফ
ওয়া রোযে ওয়াসালাত চু উম্রো কোতাহ্
সখি পিয়া কো জো ম্যায় না দেখুঁ
তো ক্যায়সে কাটুঁ আন্ধেরি রাতিয়া
বিরহ রাত তোমার কেশের মতো দীর্ঘ
মিলন দিন জীবনের মতো ছোট
সখি, যদি প্রিয়কে না দেখি
কী করে কাটাই এই অন্ধকার রাত
চয়ন ও উপস্থাপন ♦ রুশো মাহমুদ