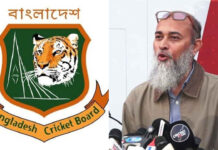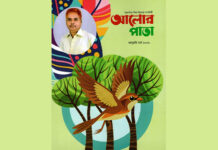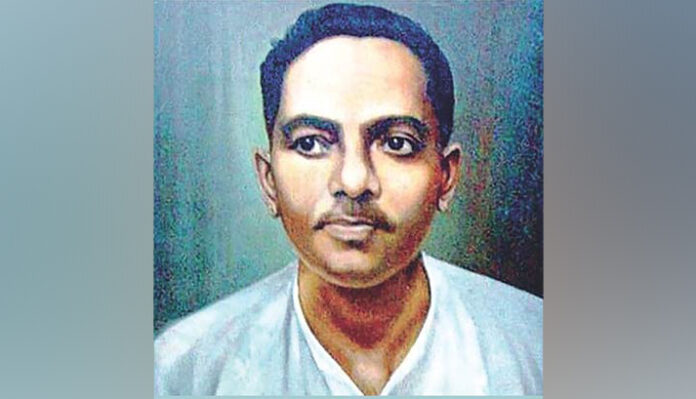হাবিবুল হক বিপ্লব »
ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক জীবনানন্দ দাশের কবিতায় শুধু নয়, তাঁর কবিমনস্কতাতেও পাশ্চাত্য কবিদের প্রভাব নানাভাবে বিকশিত হয়েছে। রবীন্দ্রোত্তর আধুনিক কবিতায় অভিমুখই যেখানে পাশ্চাত্যমুখী, সেখানে তাঁর কবিসত্তায় স্বাভাবিক ভাবেই পাশ্চাত্যের ছায়া কায়া বিস্তারের সম্ভাবনা ছিল। অথচ সেই ছায়ার মায়া অচিরেই তিনি কাটিয়ে উঠেছিলেন। সেদিক থেকে রবীন্দ্রবৃত্ত থেকেই নয়, পাশ্চাত্যের ভাবাদর্শ থেকেও তাঁর প্রভাবমুক্তি ছিল সময়ের অপেক্ষামাত্র। আধুনিক কবি হিসাবে তাঁর মৌলিক কবিসত্তার স্বতন্ত্র আভিজাত্যের মূলেই ছিল মুক্তির স্বকীয় আকাশ। সেখানে গ্রহণের ফের আছে, আছে মুক্তির অন্তর্লীন আলোও। এজন্য পাশ্চাত্য সমকালীন কবিদের প্রভাব এড়িয়েও জীবনানন্দ দাশের অভিযাত্রা এগিয়ে চলেছিল। পাশ্চাত্য প্রভাব এলেও তা তাঁর অগ্রে সক্রিয় হয়ে হাঁটেনি, বরং পশ্চাতে সরে পড়েছে। টি এস এলিয়টের ইতিহাসচেতনা তাঁর কবিসত্তায় নিবিড়তা লাভ করেছে। সেখানে অসীম অতীতচারিতার সঙ্গে সমকালীনতার সমন্বয়ে গড়ে তোলা ঐতিহ্য নিবিড়তা লাভ করে।
এলিয়ট তাঁর ‘Tradition and Individual Talent’ (1919) প্রবন্ধে জানিয়েছেন : ‘The historical sense which is a sense of timeless as well as the temporal and of the timeless and of the temporal together, is what makes a writer a writer tradition.’ অন্যদিকে জীবনানন্দ তাঁর ‘কবিতার কথা’য় বলেছেন, ‘কবির পক্ষে সমাজককে বোঝা দরকার, কবিতার অস্থির ভিতরে থাকবে ইতিহাসচেতনা ও মর্মে থাকবে পরিচ্ছন্ন কালজ্ঞান।’ সেই চেতনা ও জ্ঞানে বর্তমান জগতের মূল্যবোধের মধ্যেই সমগ্র বিশ্ব ও তার কালপ্রবাহ বর্তমান। এজন্য জীবনানন্দের কবিসত্তায় বর্তমানের অস্তিত্বে অতীতের ঐতিহ্য ও আভিজাত্যবোধ বারেবারে ফিরে এসেছে। অস্তিত্বের সোপানে কবিমানসের ইতিহাসযাপন স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। উর, ব্যাবিলন, নিনেভে, মিশর, পেগান গ্রীস, কনফুসিয়াসের চীন থেকে বিদিশা, উজ্জয়িনী বা ধর্মাশোকের ভারতবর্ষ প্রভৃতি স্থানে তাঁর অবাধ বিচরণ। অবশ্য জীবনানন্দ দাশের ইতিহাস ও ঐতিহ্যচেতনায় মধ্যে সত্তার শূন্যতাবোধে স্মৃতির আশ্রয় নয়, বরং স্মৃতির মধ্যে সত্তাকে খুঁজে পাওয়ার চেতনা বিস্তার লাভ করে। তাঁর কবিসত্তায় ‘exile, anguish, ignominy & misery’ অর্থাৎ নির্বাসন, যন্ত্রণা, অপমান ও দারিদ্রের আধুনিক বস্তুবিশ্ব থেকে মুক্তির দিশায় স্বকীয় মানসের সেই ইতিহাস ও ঐতিহ্যের আকাশ গড়ে স্বাভাবিক হয়ে এসেছে। সেখানে ‘বনলতা সেন’-এর ‘হাজার বছর ধরে আমি হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে’ র বিস্তার থেকে ‘রূপসী বাংলা’র ‘আবার আসিব ফিরে ধানসিড়িটির তীরে এই বাংলায়’-এর প্রত্যাশা সবই আবেদনক্ষম হয়ে ওঠে।
অন্যদিকে এজরা পাউন্ড ও এলিয়টের চিত্রকল্প (যেমন, বিষন্নতার চিত্রকল্পে ‘হেমন্তের হিম ঘাস, প্রেতচাঁদ, মরা নদী, শীতের কুয়াশা, শূন্য মাঠ প্রভৃতি) ও ডব্লিউ বি ইয়েটসের স্বপ্নচিত্রের (যেমন, মুখোশপরা ভাঁড়, ক্লাউনের মেলা বা লুপ্ত বিড়ালের শূন্য হাসি প্রভৃতি) ব্যবহারও জীবনানন্দের কবিতায় মধ্যে প্রতীয়মান। অবশ্য ইয়েটসের বার্ধক্যের বিকারে দুঃস্বপ্নের মতো জীবনবিমুখ চেতনা জীবনানন্দে ছিল না। হতাশার মধ্যেও তাঁর জীবনের আরতি বন্ধ হয়ে যায়নি। এজন্য ‘আট বছর আগের একদিন কবিতা’য় শেষে সেই জীবনাসক্তি জেগে ওঠে : ‘হে প্রগাঢ় পিতামহী, আজো চমৎকার?/ আমিও তোমার মতো বুড়ো হব চাঁদটারে আমি ক’রে দেবো/ কালিদহে বেনোজলে পার;/ আমরা দু-জনে মিলে শূন্য ক’রে চ’লে যাবো জীবনের প্রচুর ভাঁড়ার।’ আসলে জীবনানন্দের কবিতায় পাশ্চাত্য প্রভাব কিছুমাত্র ছায়া পড়লেও তার কায়া কবি জীবনানন্দের স্বকীয়। ‘বনলতা সেন’ কবিতায় এডগার এলান পো’র ‘হেলেনের প্রতি’ কবিতাটির চিত্রকল্পের আদলটি উঠে এসেছে। জীবনানন্দের ‘চুল তার অন্ধকার বিদিশার নিশা, মুখ তার শ্রাবস্তীর কারুকার্য’ই পো’র কবিতাটিতে পাওয়া যায়, ‘The hyacinth hair, the classic face’রূপে। ‘শ্রাবন্তী’-‘বিদিশা’ও গ্রীস ও রোমের স্মৃতিতে প্রতিরূপ লাভ করেছে, ‘To the glory that was Greece ! And the grandeur that was Rome!’। অথচ সে-সব চিত্রকল্পের প্রতিরূপ লক্ষ করা গেলেও, তা যে তার অনুরূপ নয়, জীবনানন্দের চিত্রকল্পেই প্রতীয়মান। অনুকরণ বা অনুসরণ নয়, বরং স্বকীয় কবিসত্তাতেই তাঁর স্বতন্ত্র আভিজাত্য। সনেটের ক্ষেত্রেও তাঁর নিজস্ব কবিসত্তা প্রবহমান। শেকসপিয়রীয়(স্তবক ৮+৬=১৪, অন্তমিল কখখককখখক+চছজচছজ) , পেত্রাকীয়(৪+৪+৪+২, কখকখ+গঘগঘ+পফপফ+চচ) বা ফরাসীয় (৮+২+৪) সনেটের কোনো নির্দিষ্ট ছক জীবনানন্দে নেই। তাঁর জীবিতকালে প্রকাশিত গ্রন্থে সনেটে ‘শকুন’(‘ধূসর পাণ্ডুলিপি’) ও ‘পথহাঁটা’(‘বনলতা সেন’) দুটিই তিন চরণের স্তবক (৩+৩+৩+২)। দুটিরই মাত্রা সংখ্যা ২৬ (৮+৮+১০)। আবার ‘রূপসী বাংলা’র সনেটগুলোয় ২২ থেকে ২৬ মাত্রা লক্ষ করা যায়। অন্যদিকে তাঁর সনেটগুলোর শিল্পরূপ প্রচ্ছন্ন থেকে কবিতার কাব্যগুণকেই পরিস্ফুট করেছে। সেদিক থেকে বলা যায়, পাশ্চাত্যের ছায়াতেও কবি জীবনানন্দের আলো স্বমহিমায় ভাস্বর।
অন্যদিকে রবীন্দ্রোত্তর আধুনিক কবিকণ্ঠ হিসাবে জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে মতানৈক্য নেই। তাঁর কাব্য-কবিতার বিষয় ও আঙ্গিক, ভাষা-শৈলি বা প্রকাশের অভিজাত স্বাত্নত্র্যেই তা প্রতীয়মান। কবি জীবনানন্দ দাশ ও তাঁর কবিতা বোঝার জন্য কতকগুলি মতবাদ সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা প্রয়োজন। সেগুলি হল, ‘ইম্প্রেশনিজম’ (Impressionism), ‘ফবিজম’ (Fauvism), ফিউচারিজম’ (Futurism), ‘কিউবিজম’ (Cubism), ‘এক্সপ্রেসিজম’ (Expressionism), ‘সুরিয়ালিজম’ (Surrealism) প্রভৃতি মতবাদ প্রথমে শিল্পে এবং পরে সাহিত্যে প্রভাব বিস্তার করেছে। অধিকাংশ মতবাদই ফ্রান্সে গড়ে উঠেছে। কোনোটি রঙের, কোনোটি আকার-আকৃতির। আবার কোনোটি প্রকাশের প্রকৃতিতে স্বতন্ত্র। ‘ইম্প্রেশনিজম’ আলো-ছায়ার মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। কোনো দৃশ্য দেখার পর মনের আয়নায় যে ছাপ পড়ে শিল্প-সাহিত্যে আলো-ছায়ায় সজীবতা লাভ করে, তাই ইম্প্রেশনিজম-এর প্রভাব। জীবনানন্দ দাশের কবিতায় নানাভাবে তার প্রকাশ ঘটেছে। অন্যদিকে ইম্প্রেশনিজমের বিরুদ্ধে মূলত চারটি মতবাদ গড়ে ওঠে। ফবিজমের ফব মানে বন্যজন্তু। ১৯০৫-এ এই মতবাদটি গড়ে ওঠে ফ্রান্সে। লুই ভক্সেলেস কথাটি প্রথম চালু করেন। ১৯০৬-এ নিউ ইম্প্রেশনিস্টিক আর্টের বিরুদ্ধে একদল শিল্পী বিদ্রোহ করে চড়া রঙে ও রেখায় প্রাকৃতিক পটভূমিকে নতুন করে তুলে ধরার আন্দোলনে ফবিজম মূর্ত হয়ে ওঠে। চিত্রশিল্পী মাতিসের ছবিতে তার পরিচয় পরিস্ফুট হয়। গাড় টকটকে রঙের ব্যবহারই সেখানে প্রাধান্য পায়। রঙই তার প্রাণ-গতি ও নাটকীয়তার প্রকাশ। চিত্রধর্মিতাই তার বিশেষত্ব। জীবনানন্দ দাশের কবিতাতেও তা লক্ষ করা যায়। অন্যদিকে ১৯০৯-এ ইতালিতে গড়ে ওঠা ফিউচারিজমে গতি, ১৯০৭-১৪-তে রাশিয়ায় গড়ে ওঠা কিউবিজমে গঠনে (চিত্রশিল্পী সেজানের স্থাপত্যসুলভ ঘনত্ব প্রকাশে আঁকা ছবিতে তার পরিচয় প্রথম।) এবং ১৯১২-১৩তে গড়ে ওঠা এক্সপ্রেসিনিজমে বিকার প্রাধান্য লাভ করে। জীবনানন্দ দাশের কবিতায় কিউজিজম বাদে অন্যগুলি অল্পবিস্তর প্রাধান্য লাভ করে। অন্যদিকে তাঁকে কবিতায় ইম্প্রেশনিস্ট কবির পরিচয় সমধিক। জীবনানন্দ দাশের তার পরিচয় নানাভাবে উঠে এসেছে। তাঁর অসংলগ্ন এবং ছিন্নবিচ্ছিন্ন ভাবে প্রকাশিত বিভ্রান্তিকর কবিতায় ইম্প্রেশনিজমের প্রভাব বর্তমান। এছাড়া তাঁর কবিতায় সুদূর প্রসারিত কবিদৃষ্টির বিস্তার, রঙে রূপান্তরিত চিত্রে সময়ের চলমানতা থেকে দেশজ ও গদ্যগন্ধী শব্দের নিরঙ্কুশ ব্যবহার, আলো-অন্ধকারের রূঢ় বৈপরীত্য, আঙ্গিকের ধ্রুপদী শিল্পীদের সুস্পষ্ট ও সুশৃঙ্খল শৈলীর অনুকরণহীনতা প্রভৃতির মাধ্যমে তার পরিচয় লক্ষণীয়।
পাশ্চাত্য মতবাদগুলি নানাভাবে জীবনানন্দের কবিপ্রকৃতির মধ্যে সবুজ হয়ে উঠেছে। ফবিজম তাঁর কবিতায় নানা রঙে প্রস্ফুটিত। চিল হয়ে ওঠে ‘সোনালি ডানার চিল’, রৌদ্র হয় ‘রক্তাভ রৌদ্র’। এসবই ফবিজমের রঙের বহুমাত্রিক খেলা। বর্ণবাহারি প্রকৃতি তার মজ্জায়, তার সজ্জায়। জীবনানন্দের কবিতাতেও তা সুলভ। যেমন, ‘বনলতা সেন’ কাব্যের ‘নগ্ন নির্জন হাত’ কবিতায় উঠে এসে সেই বর্ণাঢ্য : ‘ রামধনু রঙের কাচের জানালা,/ ময়ূরের পেখমের মতো রঙিন পর্দায় পর্দায়/ৃ ৃ ৃ/ পর্দায় গালিচায় রক্তাভ রৌদ্রের বিচ্ছুরিত স্বেদ/ রক্তিম গেলাসে তরমুজ মদ।’ এরকম ফবিজমের নিদর্শন জীবনানন্দের কবিতায় নানাভাবে উঠে এসেছে। ‘বনলতা সেন’ কাব্যের ‘বনলতা সেন’ কবিতায়, ‘চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা’, ‘অন্ধকার’-এ ‘নীল কস্তুরী আভার চাঁদ’, ‘মহাপৃথিবী’ কাব্যের ‘বিড়াল’ কবিতায় ‘জাফরান-রঙের সূর্য’, ‘শিকার’ কবিতায় ‘টিয়ার পালকের মতো সবুজ’, ‘মোরগফুলের মতো লাল’ বা ‘নদীর জল মচকাফুলের পাপড়ির মতো লাল’, ‘হাওয়ার রাত’-এ ‘চিতার উজ্জ্বল’, ‘আমি যদি হতাম’-এ ‘সোনার ডিমের মতো/ ফাল্গুনের চাঁদ’, ‘সিন্ধুসারস’ কবিতায় ‘হেলিওট্রোপের মত দুপুর’ প্রভৃতিতে তার পরিচয় সমুজ্বল। অন্যদিকে একই রঙকে জীবনানন্দ ফবিস্টদের মতো নানাভাবে ব্যক্ত করেছেন। যেমন, শাদা রঙের প্রতি কবির তীব্র প্রকাশ নানা ভাবে উঠে এসেছে। ‘বনলতা সেন’-এর ‘সবিতা’ কবিতায়, ‘দুধের মতন শাদা নারী’, ‘মহাপৃথিবী’ কাব্যের ‘হাওয়ার রাত’-এ ‘স্বাতী তারার কোল ঘেঁষে নীল হাওয়ার সমুদ্রে শাদা বকের মতো/ উড়ছে সে’, ‘সিন্ধুসারস’ কবিতায়, ‘জানি পাখি, শাদা পাখি, মালাবার ফেনার সন্তান’, ‘পরিচায়ক’ কবিতায়, ‘বরফের মতো শাদা ঘোড়াদের তরে’ প্রভৃতি। অন্যদিকে ফিউচারিজমের সঙ্গেও ফবিজমের অপূর্ব মেলবন্ধনও জীবনানন্দ দাশের কবিতায় মেলে। ‘সিন্ধুসারস’ কবিতাই তার পরিচয়। আসলে ফিউচারিস্টদের চেতনাতেই রঙের বহুরূপী বিস্তার বর্তমান। স্বাভাবিক ভাবেই সেখানে ফবিজমও এসে পড়ে। রঙের তারতম্যে সময়ের প্রতিফলন ঘটে। চলমান দৃশ্যে রঙের রূপান্তর ঘটে। ভোরে উদিত সূর্য থেকে বিকেলে অস্তগামী সূর্যের রঙেই তা সহজবোধ্য হয়ে ওঠে। সেখানে রঙের তারতম্যে গতির পরিচয় নিবিড়তা লাভ করে। আসলে ফিউচারিস্টদের গতির প্রাধান্যে গড়ঃরড়হ, ঝঢ়ববফ আপনাতেই সক্রিয় হওয়ায় তাতে রঙের রূপান্তর স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময়ান্তরে রঙের রূপও বদলে যায়। ইম্পেশনিজমেও তা লক্ষণীয়। সেখানে ভাবের প্রকাশে আলোআঁধারি রূপবৈচিত্র উঠে আসে। সকাল দুপুরে গড়িয়ে যায়, দুপুর বিকেল হয়ে ওঠে। সেখানে অবশ্য স্মৃতি-সত্তার বিষয়টি প্রাধান্য লাভ করে। অন্যদিকে ফিউচারিস্টদের সময়ের নানামাত্রিক রঙের দীপ্তি নানাভাবে প্রকট হয়ে ওঠে। সেখানে অমব ড়ভ ংঢ়ববফ কে প্রকাশই লক্ষ্য। ফিউচারিস্টদের দার্শনিক ভিত্তি বের্গসঁ’র গতিবাদ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও তার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। চলমান জীবনের প্রতিচ্ছবি সেখানে মূর্ত হয়ে ওঠে। জীবনানন্দ দাশেও তা লক্ষণীয়।