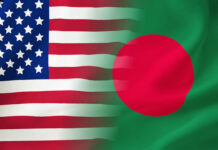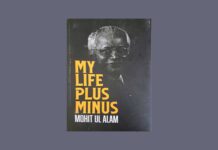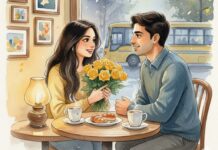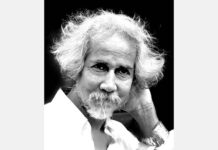হাফিজ রশিদ খান »
নতুন বাংলা নববর্ষে এখন আমরা শ্বাস-প্রশ্বাস নিচ্ছি। এর আগের বছরটিতে আমাদের বহু আশা-প্রত্যাশা যেমন সঠিক পরিপ্রেক্ষিত, সাচ্চা পরিচর্যার অনুপস্থিতিতে অনেকটাই তামাদি হয়ে গেছে, তেমনি নতুন বছরটিকে ঘিরে দুর্বলের মন না-মানা প্রত্যাশার মতো আবারও পল্লবিত হয়ে উঠতে চাইবে অনেক-অনেক চাওয়া-পাওয়ার নতুন মনোবৃক্ষটি। মনে পড়ছে প্রবাদবাক্যসম কোনো এক জ্ঞানীজনের একটি বচন : ‘মানুষ তার আশার সমান বয়সী’। কথাটিতে একটি বেগানা আভিজাত্যের মতো দূরবর্তী সান্ত¡নার প্রলেপ থাকলেও ওতে মন না-মজিয়ে উপায়ও-বা কী! দেশটাকে যে আমরা সকলেই ভালোবাসি, তাতে বিন্দুমাত্র আঁচড় না-দিয়েও বলা যায়, এ ভালোবাসা প্রকাশে আমাদের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের মধ্যে যেন সঠিক ও সাবলীল ধরনের প্রকাশভঙ্গিগত বিপুল ঘাটতি মনে এত্তেলা দিয়ে যায়। ফলে মন বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়। মন বুঝ পায় না, বছরে-বছরে কেন আমরা তামাদি দলিল-দস্তাবেজ ঘেঁটে কাইজা-ফ্যসাদে লিপ্ত হই প্রায়শ? দেশের চলমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির দিকে তাকালে, এমন ভাবনা ছাড়া আর কীই-বা উদিত হয় মনে? স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক মানসিকতাকে আমরা একই চেতনার অংশ হিশেবে নির্মাণ করে নিতে সক্ষম হইনি আজও। আমরা দুটোতেই আমরা রয়েছি যেন বারঘরের ক্ষণিকের অতিথি হয়েই। আমাদের স্বাধীনতা ভূখ-গত জনমানুষের বৈষয়িক বা ইহজাগতিক সমৃদ্ধির গ্যারান্টি দিতে বহু বেশি সময় নষ্ট করে চলেছে। কে জানি একটা প্রকা-, নির্লিপ্ত, বিমূর্ত ধারণার ভেতরেই আমাদের স্বাধীনতা নিস্তেজ হয়ে আছে। আর গণতন্ত্র বিভিন্ন সময়ে, বর্ষে-বর্ষে, নতুন নতুন পোশাক পরে আবির্ভূত হয়ে আমাদের নাগরিক সমাজের বনেদি রুচি-সংস্কৃতির গায়ে কেবলই ঘা দিয়ে যাচ্ছে সজোরে, ‘এই, আমাকে চেন না বুঝি?’ এ থেকে আমাদের সত্যসন্ধ, সহজ, মানবিক মুক্তি কবে কে জানে। তার ভেতরেই এলো কোভিডকালের দ্বিতীয় স্ট্রেইন বা ভেরিয়েন্ট। সবকিছু ভেঙে পড়ার দশা যেন। এ শুধু আমাদের দেশ নয়, এটি বৈশ্বিক বিপর্যয়। দেশে এটি আহার-বিহার ও স্বাভাবিক জীবনযাপনে একধরনের যবনিকা টেনে দিয়েছে। সার্বক্ষণিক শঙ্কা ও আতংকের অনুভূতি নিয়েই চলছে জীবনকে বয়ে নেওয়ার দুর্মর প্রয়াস। এ অবস্থায় নৈসর্গিক নিয়মের কোনো ব্যতিক্রম না-ঘটিয়ে, প্রকৃতিকে সাজিয়ে চলে এসেছে বাংলা, বাঙালি ও আদিবাসী জীবনের নববর্ষ। এদেশে বাঙালি জাতিভুক্ত ধর্মবর্ণ নির্বিশেষে সকলের বাইরে পাহাড়ি ও সমতলী মানুষের মধ্যেও এই নববর্ষটি বরণের একটি সচেতন ও সমাজবদ্ধ স্বতঃস্ফূর্ত উন্মাদনা রয়েছে, এ আমরা ছোটবেলা থেকেই দেখে আসছি।
এসব নিয়ে বহুদিন ধরে তক্কে-তক্কে ভাবছি, পহেলা বৈশাখ ও তার এদেশীয় পরিম-ল বিষয়ে আমার বেশ জানা-বোঝা হয়ে গেল বুঝি! যেহেতু বিগত বিশ শতকের সত্তর দশকের শেষাংশ ও আশি’র দশকের প্রায় পুরোটা জুড়ে আপনযৌবন বাউলের একরোখা আবেশের বশবর্তী হয়ে জনপদচারী আর সেসবের ভেতর-বাহির নিয়ে বহু কথাচারী প্রগল্ভ ছিলাম বেশ। সেই সময়গুলোতে একধরনের স্বপ্নচারিতার মায়াজাল আমাকে পরিপূর্ণ গ্রাস করে ফেলেছিল অজান্তেই। আনন্দের বিষয় হলো, ওই মায়াজালে আমার তৃপ্তিমালাও তৈরি হলো কোনো প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির খেদ বা বৈরাগ্যবোধ ছাড়াই। ওই বৃহতের ভেতরে আমার এ-ক্ষুদ্রকে বিসর্জন দিয়ে বেশ অনায়াস-সাবলীল ভঙ্গিতে ভাসতে পারি বলেই হয়তো তা সম্ভব হয়েছে। যে-কারণে ‘জনতার জঘন্য মিতালি’ ভরা ঢাকা-চট্টগ্রামের যত বৈশাখী মেলা আর সারি-সারি পসরা সাজানো ওই বিকিকিনিতে আগ্রহ কমিয়ে ফেলি প্রায় শূন্যের কোটায়। মাঝখানে পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের বিজু, সাংগ্রাইং-সাংগ্রেন-চাংক্রেন কিংবা বিষু অথবা বৈসুকের রঙদার, উল্লাসকর, সঞ্জীবক, জীবনদীপ্ত জনকল্লোলের ঘূর্ণিতে ডুবতে-ডুবতে, ভাসতে-ভাসতে এখন বাকি থাকা ওসবের গলি-ঘুপচির পাদপূরণে যেন ধ্যানমগ্ন থাকি অষ্টপ্রহর। অনেকটা জাবরকাটা বা ক্যাথারসিস-এর ধরনে।
দুই
কিন্তু ওই স্বাপ্নিকতা আর ধ্যানমগ্নতার চেতনাঝড় তো এক অর্থে ঢের আগেকার সঞ্চয় নিয়ে। প্রায় তিন দশকের অতীতের কথা যা। সেই সময়ের পহেলা বৈশাখ আর উল্লিখিত অঞ্চলের আদিবাসী বিজু, সাংগ্রাইং-সাংগ্রেন-চাংক্রেন কিংবা বিষু অথবা বৈসুকের যাপনা আর লোকময়তার তেজ, লালিত্য, চঞ্চলতা, নৈকট্য, মগ্নতা এখন তো প্রায় সুদুর্লভ হয়ে গেছে। সে এক বিবশ বাস্তবতাই বটে। এখন তো আরোপিত বড়সড় আয়োজনে প্রাণদলন আর নিঃস্বায়নের বাজিমাত চলছে শুধু চারপাশে। বাঙালি জাতিসত্তার প্রতœ ও জায়মান প্রাণসত্তার জিজীবিষায় এখন আমি স্বকীয়তা হারানোর ভয়ালরূপই দেখি বৈশাখের ওই ধাঁধানো আনুষ্ঠানিকতায়, বিজু, সাংগ্রাইং-সাংগ্রেন-চাংক্রেন কিংবা বিষু আর বৈসুকের বেগুনি নীল আসমানি সবুজ হলুদ কমলা লালরঙের পতাকাগুলোর দোল দোলনে। আলোকসজ্জার বীভৎস উলঙ্গতার ভেতর আমার আমিকে আমি বসনহীন, উদগ্র, আগুপিছু বিবেচনাহীন নগদ নগরের এক উন্মাদরূপে, ভিক্ষুকের বাড়ানো হাতের মতো দেখতে পাই। আর দীনতার, হীনতার ভেতর বেআক্কেল হাস্যপরতার জাজিমে অনর্থক নৃত্যরত দেখি নিজেকেই যেন। আমার বৈশাখ ওই অঢেল, অফুরন্ত, অজস্র সহজতা আর সরলতার বাঙালিয়ানা ও আদিবাসিতা দাঁতের পাটিতে দেখানোপনার, লুণ্ঠিত-ভ্রষ্টিত হবার কৃত্রিম সোনালি লাস্যপনা দেখে কবি চ-ীদাসের মতো বলে ওঠে :
‘মেদনী বিদার দেওÑ পসি অঁ লুকাওঁ …’
তিন
ওপরের ওই অংশটুকু পড়ে পাঠকের নির্দোষ মনে প্রশ্ন জাগতে পারে : কেন এই উষ্মা, কিছুটা তাচ্ছিল্যম-িত এ উদ্গার কেন, বাবা? ভেবে বিস্মিত হই আমিও তো! তবে কী নগদলাভের আশায় অগ্র-পশ্চাৎ ভাবনাহীন, বদলে যাওয়া মানুষগুলোর মতোই পুরনোর কাতারে শামিল হয়ে গেলাম এই অভাজনও? মানুষ নাকি বেঁচে থাকলে বদলায়, কারণে-অকারণে বদলায়, মরে গেলে পচে যায়। জানি, তা তো হয়ই! মনুষ্যজাতির ধারাবাহিক, বিধিসম্মত পরিণতি আমার বেলায় ভিন্ন রূপাকৃতি নেবে, এ মতো ভাবনার প্রশ্রয়ে অত বড় কমবখ্ত আমিও হয়তো নই। ভেবে মরি শুধু, আমাদের এইসব বৈশাখী আয়োজনে, আদিবাসী বিজু, সাংগ্রাইং-সাংগ্রেন-চাংক্রেন, বিষু আর বৈসুক, ওয়াংগালায় আমাদের ভূমিজ প্রাণবৈচিত্র্য, জীববৈচিত্র্য চুরি হয়ে যাবার দরবারি নিলামের বিরুদ্ধে কোথাও নেই কেন টু-শব্দটি কারো? বিপুল আয়তনে, বিশাল শামিয়ানার কর্মযজ্ঞে, শুমারহীন অর্থব্যয়ে গত দুই সন বাদে (বাংলা ১৪২৬ ও ১৪২৭, করোনার প্রথম ও দ্বিতীয় ভেরিয়েন্টের দাপটে) বৈশাখের উদযাপনা, বিজু-সাংগ্রাইংয়ের অনুষ্ঠানমালা তো হয়েই চলেছে। তথাকথিত ঐতিহ্য অন্বেষণ আর সংরক্ষণের নামে হাত পেতে নেওয়া স্পন্সরের সোনালি প্ররোচনায় একধরনের ঋদ্ধিতে আহ্লাদিত-আমোদিত হচ্ছি বটে বছর-বছর। কিন্তু এর ভেতরে আমি কেন কোনো এক সর্বনাশা চৈতালি ঘূর্ণির উড্ডয়ন হেরি দুই নয়নে! এ আমাদের কোন্ খাদে, কোন্ অজানা-বেগানা মরা দহের কাছে দুমড়ে-মুচড়ে ফেলে দিচ্ছে গুমখুনের লাশের মতো?
চার
আমি ভেবে মরি : উত্তর ঔপনিবেশিক পাঠের ভেতর যে বায়োকলোনিয়ালিজমের কথা বলা হচ্ছে, এই দেশে, এই প্রাণবৈচিত্র্যে ভরপুর আমাদের এই জনপদে, ওই ‘স্পন্সরশিপ’ নামক আগ্রাসনের বিরুদ্ধে, কই কোনো সম্মেলক প্রতিবাদ তো পেলাম না জাতীয় আত্মার ক্রন্দনের মতো, চিৎকারের মতো! তাহলে কেন এবং কাদের চোখে প্রেমের আবিল চোখ রেখে বাঙালিয়ানার নামে দেশজতা, আদিবাসী প্রাণবৈচিত্র্যরক্ষার আধো-আধো আওয়াজে বাজিয়ে চলেছি ঢোলবাদ্য সবখানে? একদা যে-বিষয়টিকে ঔপনিবেশিকরণ বলতেন জ্ঞানীজনে, তাতে ছিল ভূমিদখলের ধারণাটাই প্রধান। আর এখন ইরড়পড়ষড়হরধষরংস বা প্রাণ-ঔপনিবেশিকরণের মাজেজা হচ্ছে অনুন্নত, দুর্বল জাতিগুলোর প্রাণবৈচিত্র্যের উদ্ভিদ, প্রাণী, অণুজীব, শস্যবীজসহ জিন পর্যন্ত বেদখল হয়ে যাবার বহুজাতিক আগ্রাসন। এই থাবার ভেতরে বাংলাদেশের মতো দেশগুলোর হাজার বছরের জেনেটিক সম্পদ, লোকায়ত জ্ঞান লুণ্ঠিত হচ্ছে প্রকাশ্যেই, বুদ্ধিবৃত্তিক তেলেসমাতিতে। প্রান্তিক জনগোষ্ঠী ও তাদের বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতি, জীবনযাপন এখন বাণিজ্য ও মুনাফার অবারিত ক্ষেত্র হয়ে উঠছে দিন দিন। আর এ ‘প্রকল্প’ বাস্তবায়নের সুবিধার্থে অনুন্নত রাষ্ট্রগুলোর কাছে পশ্চিমা প্রণোদনা হয়ে আসছে বিরাষ্ট্রীয়করণ, বিনিয়োগ, বিনিয়ন্ত্রণ, উদারীকরণ, কৃষিতে ভরতুকি হ্রাসকরণ, বেসরকারিকরণের বিভিন্ন বাধ্যবাধকতা। আর এসবের অবাধ বাস্তবায়নে এ ধরনের রাষ্ট্রগুলো খুলে দিচ্ছে স্থানিক কৃষিজ ব্যবস্থাপনার সদর-অন্দর। এভাবেই অনুপ্রবেশের অধিকার পেয়ে যাচ্ছে বহুজাতিকের বিবিধ কিসিমের গুপ্তচরেরা। আর ফাঁকতালে তাদের নিষ্কুণ্ঠ ব্যয়বাহুল্য আর এন্তেজামি মহলায় বেহাত হয়ে যাচ্ছে নিম্নবর্গীয় জনসমাজের খাদ্য নিরাপত্তাবলয়। কৃষিজ লোকপরম্পরা ছিন্ন হয়ে গড়ে উঠছে হাইব্রিড ও নন-হাইব্রিড ‘জেনেটিকেলি মডিফাইড’ (জিএম) শস্য উদ্ভাবন ও তার প্রচার-প্রসারের মুক্তবাজার। এই আগ্রাসনের দেবদূতগণ আমাদের মতো অনুন্নত, অথচ জীব ও প্রাণবৈচিত্র্যে ভরপুর দেশগুলোর বিবিধ শস্যবীজ সংগ্রহ করে গড়ে তুলছে বহুজাতিক শস্যবীজ ভা-ার। অতঃপর উক্ত শস্যসমূহের ‘জিনোম সিকোয়েন্স’ নির্ণয় করে যে-জিনটি শস্যটির বিশেষ বৈশিষ্ট্যের জন্য দায়ী তা শনাক্ত করে ওই জিনটিকেই তাদের মৌলিক উদ্ভাবনা বলে পেটেন্ট করে নিচ্ছে। এভাবেই বিশ্ববাণিজ্য সংস্থায় বাংলাদেশের ফজলি আম ও জামদানি শাড়ির মালিকানা কুক্ষিগত করেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। একই পদ্ধতিতে এদেশীয় বাসমতি চালের স্বত্বও এখন ভারত ও পাকিস্তানের নামে পেটেন্ট করা হয়েছে। বাংলাদেশের নকশিকাঁথাও পশ্চিমবঙ্গের ভৌগোলিক পণ্যরূপে ভারত তার নামে পেটেন্ট করতে উদ্যোগ নিয়েছে বিশ্ববাণিজ্য সংস্থায়। এদেশের নয় প্রকারের বেগুনের জাতকে ‘জিএম’ পদ্ধতিতে বদলে ফেলে এসব বীজের মালিকানা এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের।
বাংলাদেশের আদিবাসী জাতিগোষ্ঠী অধ্যুষিত পাহাড় ও সমতলী অঞ্চলগুলোর জীববৈচিত্র্য আরও প্রসারিত, আরও অনুপম সম্পদ সুষমায় বৈশিষ্ট্যম-িত। বিশেষ করে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল এক্ষেত্রে আরও একধাপ এগিয়ে। এ অঞ্চলে রাজনৈতিক বিভেদ-বিসম্বাদের সুবাদে বা তার আড়ালে বহুজাতিকের নগ্ন বিচরণ আরও সহজতর হয়ে উঠেছে। ওই আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীবহুল জনপদে উৎসব-মেলা-পার্বণে বহুজাতিক সংস্থাগুলোর মায়াজড়ানো নানা স্পন্সরশিপের ঘাটতি থাকে না তাই কোনো অবস্থাতেই।
পাঁচ
আর্নেস্ট হেমিংওয়ের ‘দি ওল্ডম্যান অ্যান্ড দি সী’র বুড়ো সান্তিয়াগোর মতো বড় ধরনের স্বস্তিদায়ী অবলম্বন পেয়েও হাঙর বা লুণ্ঠনকারী বা আক্রমণকারীর উপর্যুপরি আঘাতে-আঘাতে নিঃস্ব হয়ে যাবার মতো বেদনামথিত হৃদয় নিয়ে আমিও আজ জাতীয় ঐতিহ্যসমূহের পুরাকালীন সোনালি স্বপ্নময়তায় ভেসে চলি বিচ্ছিন্ন, একক হয়ে বিলাপ করতে-করতে। বিপুল ক্ষোভে ও ক্রোধের আহাজারিতে। এই উল্লাসপরতার বৈশাখী সুখ, আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর বিজু, সাংগ্রাইং-সাংগ্রেন-চাংক্রেন কিংবা বিষু আর বৈসুকের স্পন্সরময় আমোদ আমাকে বরং বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে পিছিয়ে দিচ্ছে বারবার ভয়ার্ত ওই আগ্রাসন থেকে বাঁচার উপায়হীন তাগিদে। অনেকটা পার্বত্য অঞ্চলের ম্রো আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর খরতর বাস্তবতা অনুধাবনের বিশুদ্ধ চেতনার মতোই যা। দেখা গেছে, ম্রো জাতিগোষ্ঠী যত নগরায়ণ, যত সাহেবানা আর যত বেশি দেখে পিচের কালো রাস্তার বিস্তার, তত বেশি তারা পশ্চাদপসারণ করে গভীর-গভীরতর অরণ্যের দিকে। নিজেদের স্বতন্ত্রতাকে বাঁচানোর জন্যে। কারণ, ওরা তো আসলে নগরায়ণ আর ইকোপার্ক কালচারের ধাক্কায় ‘ঘরপোড়া গরু’ই হতে থাকে যুগে-যুগে, বারে-বারে। সিঁদুরে মেঘ দেখলেই তাই ওরা প্রচ- ভয় পায়। তাদের কাছে এ নগর তো আসলে হায়েনার আগ্রাসনেরই নামান্তর। এক অর্থে, এ তো আসলে সুবেশী গুপ্তঘাতকদের সাজানো-গোছানো শিবিরে বেকুব-বেভোলার মতো ঢুকে পড়া। এর লগে কিসের পিরিতি গো, হে বাঙালি?
ছয়
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরই এখন আমার মতো উপদ্রুত বাঙালি সত্তা আর যাযাবর স্বভাবসম্পন্ন আদিবাসী ম্রো জাতিগোষ্ঠীর সন্তপ্ত আদি পিতৃপুরুষ। আগ্রাসী তথাকথিত সভ্যতার বিরুদ্ধে যিনি যথার্থই উচ্চারণ করেছিলেন :
‘… দাও ফিরে সে অরণ্য, লও এ নগর…’।
লেখক : কবি ও সাংবাদিক