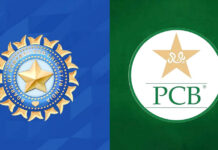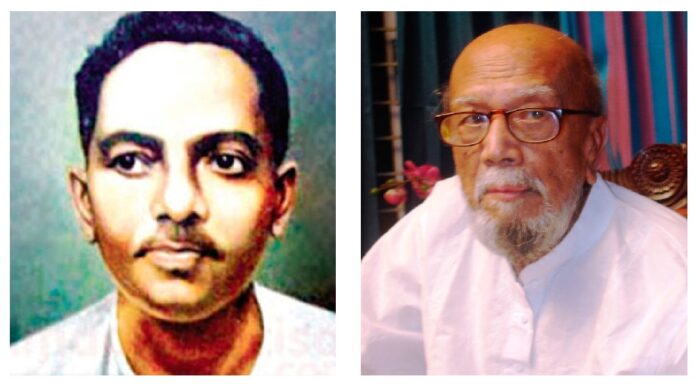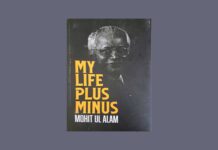পান্থজন জাহাঙ্গীর »
বাংলা কবিতায় অঘ্রাণ বা হেমন্ত ঋতু একটি বিশেষ আবহ—যেখানে প্রকৃতি পরিপক্বতার পর নীরবতায় ডোবে, আলো সোনালি হয়ে আসে, কুয়াশা নেমে পড়ে, আর গ্রামবাংলার মাঠ চুপচাপ। কিন্তু এই নীরবতার ভেতর দুই বড় কবি—জীবনানন্দ দাশ ও আল-মাহমুদ—দেখেছেন সম্পূর্ণ দুই ভুবন। একই ধানের গন্ধ, একই কুয়াশা, একই গ্রামের বাতাস—তবুও একজনের কাছে তা অস্তিত্বের নিঃশব্দ স্তবগান, অপরজনের কাছে তা প্রেম ও শরীরের নিবিড় উৎসব। এই দ্বন্দ্বই বাংলা কবিতার হেমন্ত-বোধকে বহুমাত্রিক করেছে।
প্রকৃতি: নীরব নৈঃশব্দ্য বনাম স্পন্দিত মাটি
জীবনানন্দ দাশ প্রকৃতিকে দেখেন দূর থেকে—একটি নীরব আকাশের নিচে বিচ্ছিন্ন, স্বপ্নময় দৃষ্টি। তাঁর অঘ্রাণ নিস্তরঙ্গ, ধূসর, ডুবে থাকা। ধানের খেত তাঁর কাছে শুধু কৃষির সুর নয়; তা সময়ের দুঃখ, মানুষের ক্ষয়, জীবনের অবসান। তাই তিনি লিখতে পারেন—
ধানের সোনার কাজ ফুরায়েছে—
বিবর্ণ পাখি
ঝ‘রে পড়ে অঘ্রাণের শেষ সোনালি।
এখানে কৃষিজগত নেই—আছে সময়ের পতন, আলোর অবসান। অপরদিকে আল-মাহমুদের অঘ্রাণ পূর্ণ শরীরী সজীবতায়। তাঁর দৃষ্টি যেন খড়ের গন্ধ থেকে ওঠা উষ্ণ বাষ্প—প্রকৃতি কোমল, কিন্তু জীবন্ত; মাটি, নারী ও শরীর একাকার। তিনি বলেন—
আজ এই হেমন্তের জলদ বাতাসে
মন মানবীর গন্ধে ভরে গেছে।
এই গন্ধ ব্যক্তিগত নয়; তা মাটির গন্ধ, কৃষির গন্ধ, কপালে ঘামের ফোঁটা, পুকুরের ধারে দাঁড়ানো গ্রামের মেয়ের শরীরবদ্ধ নিঃশ্বাস।
জীবনানন্দ প্রকৃতিকে মনে বহন করেন;
আল-মাহমুদ প্রকৃতিকে স্পর্শে অনুভব করেন।
প্রেম: ধূসর স্মৃতি বনাম দহনশীল ঘ্রাণ
জীবনানন্দের প্রেম অতীতমুখী; স্মৃতি ও অনুপস্থিতির আলোয় গড়া। তাঁর নারীরা স্বপ্নের মধ্যে, হারিয়ে যাওয়া সময়ের ধারে—যেন ঝাপসা আলোর মধ্যে ভাসমান। প্রেম এখানে পিরিচের ওপর রাখা নীল ফুল—ভঙ্গুর, নীরব, অচেনা বিষাদময়। নারী তাঁর কাছে—
নদীর মুখ, কুয়াশা, জোছনার ধোঁয়া, পাখির ছায়া।
স্পর্শ নেই, তাড়না নেই—
আছে দূরত্ব ও স্বপ্নের স্নিগ্ধতা।
কিন্তু আল-মাহমুদের প্রেম সরাসরি;
নারী তাঁর কাছে বাস্তব, স্পর্শযোগ্য, দেহের উষ্ণ প্রতীক।
নারীর ঘ্রাণ, ত্বকের উত্তাপ, লবণসিক্ত বাতাস—সবই প্রকৃতির চিহ্ন। তিনি প্রশ্ন করেন দেবতাদের—
তবু কেন রমণীর নুন, কাম, কুয়াশার
প্রাকৃতিক গন্ধ লেগে থাকে?
এ প্রশ্ন জীবনদর্শনের—
কেন সৃষ্টির কেন্দ্রে নারী? কেন প্রেমে প্রকৃতি? কেন কাম অপরাধ নয়—বরং জীবনের ধর্ম?
জীবনানন্দের প্রেম মেঘের কণ্ঠস্বর;
আল-মাহমুদের প্রেম ধানগাছের দেহে ঘামের শিশির।
সময় ও স্মৃতি: বিস্মরণ বনাম বাসনা
জীবনানন্দ সময়কে দেখেন ফুরিয়ে যাওয়া আলো হিসেবে। হেমন্ত তাঁর কবিতায় ক্ষয় ও রূপান্তরের ঋতু। মাঠের শূন্যতা তাঁর ভিতরের শূন্যতার সঙ্গে মিশে যায়। তিনি আত্মপরিচয়ের নদীতে দাঁড়িয়ে দেখেন—দিন যায়, মানুষ হারিয়ে যায়, তবু প্রকৃতি নীরবে বেঁচে থাকে। সেই নীরবতা কবির আত্মায় লাগে—
“মৃত্যুর মতো শান্ত”।
অন্যদিকে আল-মাহমুদের সময় উর্বর ও ক্রিয়াশীল। অঘ্রাণে তাঁর দৃষ্টি পাকে—
শরীর, বীজ, ফসল, ঘ্রাণ, পরিবার, মাটি ও মাতৃত্ব। তাই তাঁর কবিতায় হেমন্তে মৃত্যু নেই—
রয়েছে সৃষ্টি, প্রেম, উপাসনা, জৈব বিদ্যুৎ।
জীবনানন্দের স্মৃতি—পুরনো নৌকার মতো নদীতে ভাসে;
মাহমুদের স্মৃতি—মহুয়ার গন্ধে মাতাল মাঠে দৌড়ায়।
ভাষা ও সুর: কুয়াশার নীরবতা বনাম মাটির তীব্রতা জীবনানন্দের শব্দ গোধূলির পাখির মতো নিঃশব্দে উড়ে ওঠে; তার কবিতায় ধুলো, কুয়াশা, আলোর ঝাপট—সব ধীরে ধীরে। বাক্য দীর্ঘ, নিশ্বাস লম্বা, ভাব গভীর, স্বর চাপা।
আল-মাহমুদের ভাষা উচ্ছ্বাসে পূর্ণ—উজ্জ্বল, উষ্ণ, মাটির ঠাণ্ডা ঘরে রাখা ধানের মতো গন্ধময়। তিনি শব্দে বাতাস, ঘ্রাণ, দেহ, রক্ত ঢেলে দেন। তাঁর ভাষা কৃষিজীবী বাঙালির ভাষা—জীবন্ত ও মাটিস্নাত। জীবনানন্দের ভাষা স্নিগ্ধ, স্বপ্নিল, ধীর
আল-মাহমুদের ভাষা সংলগ্ন, শারীরিক, জীবন্ত।
দেশচেতনা: অদৃশ্য নদী বনাম মাটির মাঠ জীবনানন্দের দেশচেতনা মানসিক ও প্রান্তিক; আল-মাহমুদের চেতনা—মজুর, কৃষক, নদীর ঘাট। জীবনানন্দের বাংলা মানস-মানচিত্রের দেশ; আল-মাহমুদের বাংলা ধান কাটার গান, ভোরের শিস, গরুর গা থেকে নেমে আসা বাষ্প। একজন স্মরণে গড়েন দেশ; অন্যজন দেহে ও ঘামে তা বাঁচান।
শেষ কথন
দুই কবির চোখে অঘ্রাণ দুই জগত—
দু’টি আলোর ভিন্ন তাপমাত্রা। জীবনানন্দ অঘ্রাণে শোনেন । ধীর, বিষণ্ন, আত্মবিস্মৃত সময়ের সঙ্গীত।
এই সঙ্গীতের নোট নরম, ঝরা পাতার শব্দের মতো ক্ষীণ। তিনি দেখেন জীবনের ক্ষয়কে শান্তির মতো। আল-মাহমুদ অঘ্রাণে দেখেন মাটি, নারী, ঘ্রাণ, প্রেম, উর্বরতা।
তিনি দেখেন জীবনের জন্মকে ঈশ্বরের আশীর্বাদ।
জীবনানন্দে অঘ্রাণ — নীরব বিষণ্ন জ্যোতি
আল-মাহমুদে অঘ্রাণ — উষ্ণ, লবণাক্ত, শরীরী আলোকোৎসব। একজনের কবিতা—চাঁদের আলোর মতো। অন্যজনের—দুপুরের ধানের ঘ্রাণের মতো। কিন্তু দু’জনেই মিলিয়েছেন—
বাংলার শরৎশেষ শস্যভরা নিস্তব্ধ প্রান্তর,
মানুষের প্রেম, জীবন, সময়, ও স্মৃতির গোপন বার্তা। এ দুই সুর মিলেই পূর্ণ হয় বাংলা কবিতার হেমন্তভুবন—
একটি ধীর আলো, অন্যটি তীব্র উষ্ণতা।